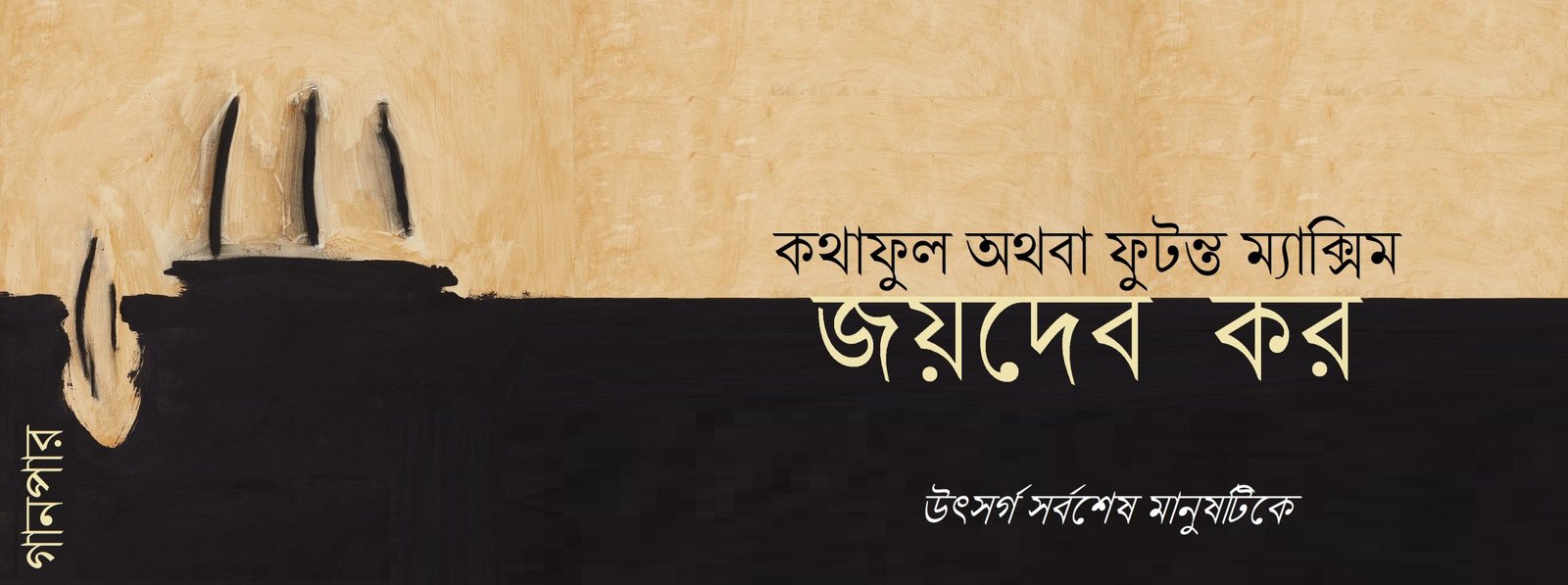
♣
নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে অন্যকে ভালোবাসা যায় কী করে? নিজের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেই তো মানুষ সুখ-দুঃখ বোধ করতে পারে। ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের মিশ্রণই তৈরি করে সমাজ নামক রসায়নের। আধুনিক সমাজের উদ্দেশ্য শুধুই ভাতকাপড়ের সাম্য নিশ্চিত করা নয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কল্যাণকর সংযোগ স্থাপনও অন্যতম লক্ষ্য। ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলনীতি এক হলেও, চিন্তার স্বাতন্ত্র্য যে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন তা অস্বীকারের কোনও পথ নাই। ব্যক্তিকে গৌণ রেখে মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে যারা সমাজ গঠনের কথা বলেন তারা মূলত তত্ত্বদাস মৌলবাদী। তাদের কাছে মানুষের চেয়ে মতবাদ বড়। আমি মূর্খ বলি, মতবাদের প্রয়োজনে মানুষ নয় মানুষের প্রয়োজনে মতবাদ। মানুষ যে কত স্বাধীন মতান্ধরা কোনওদিন হয়তো তার সন্ধানই পায় না । আর পেলেও অন্যের স্বাধীনতা দমিয়ে রাখতে চায় তাদের মতাদর্শের দেবতাদের মুখ থেকে মনুষ্যবিরোধী শ্লোক উপস্থাপন করে।
♣
ব্যক্তিমানুষকে মর্যাদা না দিয়ে শুধু সমাজ সমাজ করে চিৎকার করা মানুষটি না বোঝে মানুষ না বোঝে সমাজ। গ্রন্থান্ধ, মতান্ধ ও ধর্মান্ধ মানুষ মূলত ব্যক্তিমানুষকে বুঝতে চায় না মনের মৌলবাদমুখিতার জন্য। এদের কল্পিত সমাজ যে কত ভয়াবহ হতে পারে তা তাদের আলোচনায় বোঝা যায়।
♣
পুরুষের হাতেই মানবসমাজ বিভক্ত হয়েছে নারী-পুরুষ-বৃহণ্নলা পরিচয়ে। শারীরিক শক্তি ও শারীরিক পুরুষের হাতেই মানবসমাজ বিভক্ত হয়েছে নারী-পুরুষ-বৃহণ্নলা পরিচয়ে। শারীরিক শক্তি ও শারীরিক দুর্বলতার ভিত্তিতেই এ বিভক্তি ঘটেছে। লৈঙ্গিক পরিচয়ের ভিত্তিতে পুরুষ স্বাবলম্বী আর অন্যরা পরনির্ভরশীল এ-কথা পুরুষ নিজেরাই বলেনি, বলিয়েছে তাদের ঈশ্বরের মুখ দিয়ে, মহাপুরুষের মুখ দিয়ে, ধর্মগ্রন্থ দিয়ে, সমাজ-পরিবার দিয়ে। নারীর উত্তরণে পুরো ব্যবস্থাটাই বিরূপ, পুরো ব্যবস্থাটাই একটা বিকট পরুষ। আজকের আধুনিক পৃথিবীতে প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই পরুষের উচিত প্রভুর ভূমিকা থেকে নেমে সঙ্গীর ভূমিকায় আসা, আর নারী ও বৃহণ্নলার উচিত প্রভুত্বের মানসিকতাহীন সঙ্গী না পেলে নিজেই নিজের প্রভু ও নিজেই নিজের সঙ্গী হয়ে চলা।
♣
পরিবর্তনশীলতা নিত্য ঘটমান। সর্বশক্তিমান পরিবর্তনশীলতা থেকে শিক্ষা নিলে বহুধাবিভক্ত মানবসমাজকে অখণ্ড মানবসমাজে রূপান্তর করা কি আর অসাধ্য থাকে?
♣
ভোগ আর উপভোগের প্রভেদ বুঝতে না দিয়ে প্রেমের বিরোধিতা করা ভোগবাদী প্রথা তোমাকে আটকে রাখতে চাইবেই, আর তুমি? বন্দী থাকতে চাও? বন্দী করতে চাও? যদি মুক্তির সহজ রাস্তার সন্ধানে থাকো তবে তোমাকে প্রেমেই আত্মসমর্পণ করতে হবে। প্রেমেই বিপ্লব বা মুক্তির মোক্ষ নিহিত। নিজেকে সচেতনে ভালোবাসো, আমিকে আমরাতে রূপান্তর করার জাদুশক্তি নিশ্চই নিজের মধ্যে খুঁজে পাবে।
♣
শাসকশ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ দ্বারা সৃষ্ট ধর্মবাদগুলো কখনোই মানুষের মঙ্গলকামী হতে পারে না। ওগুলো জনতার চিন্তার জগতকে বদ্ধ জলাশয় করে ফেলতেই সিদ্ধহস্ত।
♣
সংস্কৃতি ও শিক্ষার সঠিক পৃষ্ঠপোষকতাই প্রতিক্রিয়াশীলতার বীজ ধ্বংস করে দিতে পারে। পৃষ্ঠপোষক নিজেই যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তখন শিক্ষা ও সংস্কৃতি টিকে রয় শুধু বিপ্লবী সত্তার অন্তরতম স্থানে। মৌলবাদের সাথে আঁতাত করা আর মুক্তবুদ্ধির প্রতি খড়গহস্ত হওয়া শাসনপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসার গণআকাঙ্ক্ষা তীব্রতর করতে জেগে ওঠো অমৃতের সন্তানেরা।
♣
ঈশ্বর-পরকাল-আত্মা-প্রেত-ভূতে বিশ্বাস নেই । শুভ ও সুন্দরে আস্থা রাখি। জীবন একটাই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইহলৌকিক মানুষটিই সকল শুভ-অশুভ, সুন্দর-অসুন্দরের মধ্য দিয়ে যায়। তবে কিছু বোকা মানুষই নিজের যন্ত্রণামুক্তির সহজ উপায় হিশেবে অশুভ-অসুন্দর পথ ছেড়ে শুভ ও সুন্দরের প্রতি শতভাগ মনোযোগী হয়ে থাকেন!
♣
আগামীকাল বা গতকাল নিয়ে দুশ্চিন্তায় যদি কাটালে দিন তবে তুমি বর্তমানঘাতী মূর্খ, কখনও কি ছিলে যে হারিয়ে যাবে?
♣
মুক্তচিন্তা রক্ষণশীলতার প্রাণভ্রমরায় আঘাত হানে। তাই প্রথাগত সকল প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম) মুক্তচিন্তা পদ্ধতিটিকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু পারে না। কারণ সকল মানুষের চিন্তা রোধ করা যায় না, সকল মানুষকে করা যায় না চিন্তাদাস। কিছু মানুষ থাকেন যারা যে-কোনও মূল্যে চিন্তার স্বাধীনতা বজায় রাখেন। মানুষের সকল বড় অর্জনই তার চিন্তাস্বাধীনতার ফল। চিন্তাস্বাধীনতা বিস্তৃত পরিসরে হতে পারছে না। এর কারণ প্রথার সেবাদাস প্রতিষ্ঠানসমূহ মানুষের চিন্তাধারা রোধ করার জন্য পাপ, শাস্তি, জেল, নরকের ভয় দেখায়। তারা নিজেরাও চিন্তাস্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে না । কিন্তু প্রথাগত সকল প্রতিষ্ঠানই অল্পসংখ্যক মানুষের চিন্তাস্বাধীনতার ফসল খাচ্ছে যুগযুগ ধরে! প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো যে কত গণ্ডমূর্খ এতেই বোঝা যায়। চিন্তার স্বাধীনতা একজন মানুষের মৌলিক অধিকার। যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে প্রকাশও সেই অধিকারের মধ্যে পড়ে।
♣
সব শালাশালীরা খোঁজে অনুগত দাস-দাসী। দোহাই দেয় প্রেমের!
♣
রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো হাস্যকর বিষয়টি অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে যদি রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হয় গণমুক্তি। আর গণমুক্তির মতো অতিব্যবহৃত রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়িত হতে পারে যদি সেখানে ব্যক্তির মুক্তি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি থাকে অব্যর্থ নিশানা। মানুষের ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় নানান মায়াজালে বন্দী হয়েছে মানুষ। মাঝে-মাঝে যে ক্ষণিক মুক্তির ঝলক মানুষ পায়নি তা নয়। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে মানুষের মুক্তি আজো অধরা।
আজকের পৃথিবীতে কথিত অনেক আধুনিক রাষ্ট্র রয়েছে যাদের আধুনিকতা আঞ্চলিক, বিশ্বজনীন নয়। এমনও রাষ্ট্র রয়েছে যেখানে পশুহত্যারও বিচার হয়, সেইসকল রাষ্ট্রই আবার অন্য ভূখণ্ডে নির্দ্বিধায় মানুষহত্যায় মগ্ন। এই অবস্থায় অসংখ্য কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে অখণ্ড মানবসমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মতো মানসিকতার লক্ষণ কোথায় খুঁজব আমরা? বিশ্বকে এক পরিবার ভাবলে তো ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার দিকে মনোযোগী হওয়া ছাড়া গতি নাই।
এদিকে কথিত পিছিয়ে-পড়া রাষ্ট্রগুলো নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ। বরং বলা যায় ভিতরে-বাহিরে গণমুক্তিবিরোধী শক্তি দ্বারা পরিচালিত। ব্যক্তির মুক্তির পথে যত ধরনের বাধা রয়েছে তা নিরসনে তাদের কোনও উদ্যোগ নেই। ‘মুক্তি’ শব্দটিকে ব্যবহার করে রাজনীতি-করা মানুষগুলোর অধিকাংশের উদ্দেশ্য ক্ষমতাগ্রহণ ও শক্তিমান হয়ে মানুষের বিকাশ রোধ করা। রাজনীতিকদের মানসিক অসুস্থতার প্রতিযোগিতার শিকার মানুষের মুক্তি কোথায়?
ব্যক্তির মুক্তি আপাতত একটি ভূখণ্ডের ভিতরেই যদি চিন্তা করা যায় তবে সেই ভূখণ্ড কেমন হবে? সেই ভুখণ্ড হবে পুরো মহাবিশ্বের একটি মডেল যার প্রতি ইঞ্চি জমি হবে সকল সত্তার অভয়াশ্রম। খাদ্য-বস্ত্র-চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা ব্যক্তির মুক্তির পথের প্রাথমিক পাথেয়। তারপর তার অবাধ বিচরণ, বাকস্বাধীনতা, শুভ চিন্তার অধিকার; মোদ্দা কথা, ‘নিজেই নিজের প্রভু’ করে, ‘আত্মদীপ’ হয়ে নিজেকে পরিচালনা করার অধিকার নিশ্চিত হতে হবে।
♣
সমাজের দেয়াল একেকটি রক্তবীজ। যতই ভাঙবেন ততই জন্ম নেবে। কালীর কৌশল জানলেই রক্ষা।
♣
কবিতা চিন্তাস্তরের শিল্পীত প্রতিচ্ছবি। জীবনবোধ আর শিল্পবোধের সঙ্গমে জন্ম নেন এই অপরূপ শব্দব্রহ্মকলা।
♣
সমাজব্যবস্থাটা কাঁঠালের আঠার মতো! হৃৎপিণ্ডে তেল মেখে নিতে না পারলে এর মাঝে বসবাস করে ভোগান্তির শেষ নেই!
♣
সহজের মর্যাদা দিতে জানতে হয়, আর এর জন্য দরকার এমন এক মানসিক উচ্চতা যা তোমাকে নিজের অন্যায্য কামনার গোলামী থেকে মুক্ত রাখতে পারে।
♣
সম্প্রদায়কে ধর্ম মেনেই সকল বিপত্তির উদ্ভব ঘটায় মানুষ, অথচ মহাজাগতিক ধর্মে মানুষও এক সাম্প্রদায়িক শব্দ বৈ কিছু নয়।
♣
গুরু ও শিষ্য শব্দদ্বয় অনেকের কাছে বেশ তাচ্ছিল্যের সাথেই গৃহীত হয়। আমি কোনও শব্দের বলির পাঁঠা হওয়াকে ওই শব্দের ত্রুটি মনে করি না এবং করাটা স্বাভাবিকও নয়। শব্দের বহুমুখী প্রকাশ মূলত তার প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। যা হোক, এ নিয়ে আলাপ করা এইখানে উদ্দেশ্য নয়। তাই যে সাধারণ কথার সূত্রপাত করতে চাই তা হলো গুরু-শিষ্যের সমার্থক হিসেবে ছাত্র-শিক্ষক শব্দবন্ধটি মাথায় রেখে অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে হয়। ‘আত্মদীপ ভব’ বা ‘Know thyself’-এর পথে পরিচালিত হতে হলে বা হতে গেলে ছাত্র-শিক্ষক সত্তার অধিকারী হওয়া প্রাথমিক শর্ত। এই অনিবার্য শর্তসাপেক্ষতায় পরিপূর্ণ হয়েই বুদ্ধ-সক্রেটিসের মতো আদি ও বর্তমান সকল শিক্ষকের কাছে আত্মপরিব্রাজনের পথে নিজেই নিজের প্রাজ্ঞ গুরু ও নিজেই নিজের চরম জিজ্ঞাসু ছাত্র হতে পারা মূলত চূড়ান্ত পারমার্থিক সত্য, বাকিসব ব্যবহারিক সত্য হিসেবেই বিবেচিত। সাথে কোনও নির্ধারিত কাঠামোর সংযোগ খোঁজার অর্থ আত্মপরিভ্রমণের পথে অন্ধের মতো হাতিবিচার করা।
কথাফুল অথবা ফুটন্ত ম্যাক্সিম পর্বগুলো
জয়দেব কর রচনারাশি
গানপার সদুক্তিনিচয়
- ধরিত্রীর নিকট প্রেমের চিঠি-৫ / পৃথিবীতেই স্বর্গ ।। তিক নাত হান ।। ভাষান্তর : জয়দেব কর - January 16, 2026
- ধরিত্রীর নিকট প্রেমের চিঠি-৪ / তোমার স্থিতিশীলতা, ধৈর্য ও অন্তর্ভুক্তিমুখিতা || তিক নাত হান || ভাষান্তর : জয়দেব কর - January 8, 2026
- বাইশে অক্টোবর || জয়দেব কর - October 22, 2025

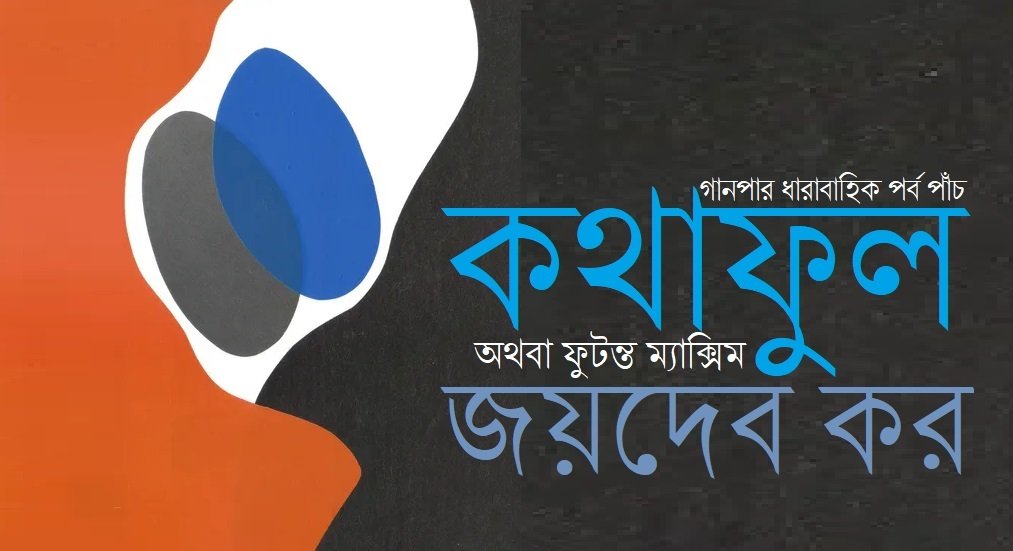
COMMENTS