পাপড়ি রহমানের উপন্যাস মানেই কোনো-এক জনপদের উপাখ্যান। ‘বয়ন’-এর মুগরাকুল, ‘পালাটিয়া’-র কইনগরের পর এবার বুড়িগঙ্গার ওপারে আগানগরের আখ্যান। বুড়িগঙ্গার দুইপাশে যে কত ঘাট আছে এই বই না পড়লে আমার জানা হতো না। সারা বাংলার কথা বাদই দিলাম, আমাদের প্রজন্মের ঢাকা শহরে যাদের জন্ম এবং বেড়ে-ওঠা আমি নিশ্চিত তারা অনেকেই এইসব ঘাটের নাম জানেন না। আমাদের নিজস্ব ভূমি এবং ইতিহাস থেকে আমরা কত যে বিচ্ছিন্ন এটা তার একটা সামান্য উদাহরণ মাত্র।
সদরঘাট, আলম টাওয়ার ঘাট, ওয়াইজ ঘাট, ইস্পাহানি ময়লার ঘাট, বাদামতলীর ঘাট, তেলঘাট এবং ঘাটপারের সাধারণ মানুষের জীবনের জলছবির এক বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ ‘নদীধারা আবাসিক এলাকা’। পাপড়ি রহমান বরাবরই উপন্যাসের চরিত্রদের নির্মাণ করার পূর্বে তাদের স্থানিক অবস্থান, সেখানকার প্রকৃতি, ঋতুবদল, ফুল-ফসলের মাঠ, নদী, মাটি এগুলোকে দুর্দান্তভাবে ফুটিয়ে তোলেন, তারপর চরিত্রনির্মাণ এবং সবশেষে মানুষ ও প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ার যৌথজীবন! হাল-আমলে সমালোচনাসাহিত্যে ইকোক্রিটিসিজমের যে ধারা তৈরি হয়েছে, পাপড়ি রহমানের উপন্যাসসমূহ সেখানে দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক। লেখক হয়তো কোনোটাই সচেতনভাবে করেন না। তবে মোটামুটি তিনটি উপন্যাস, ‘বয়ন’, ‘পালাটিয়া’এবং ‘নদীধারা আবাসিক এলাকা’-তে একই রকম প্যাটার্ন আমি লক্ষ করেছি।
“নওয়াব ইউসুফ রোড যেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফুরিয়ে গেছে, সেখান থেকেই শুরু হয়েছে বাবুবাজার ব্রিজ।” উপন্যাসের প্রারম্ভিক লাইন এটি, বস্তুত আমি উপন্যাস শেষ করে প্রথমেই বাবুবাজার ব্রিজ, ঢাকা, বাংলাদেশ লিখে গ্যুগলম্যাপে যান বোতামে চাপ দেই। মুহূর্তেই ব্রিজ এবং তার আশেপাশের সকল ঘাট, বুড়িগঙ্গা, হ্যাঁ, কালো জলের বুড়িগঙ্গা আমার মুঠোফোনের স্ক্রিনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই সেই বুড়িগঙ্গা যার বুকে গড়ে উঠেছে আমাদের নাগরিক সভ্যতা! সে এক দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত! এমনকি নদীধারা আবাসিক এলাকাও পেয়ে যাই! তিন/চারদিন ধরে যাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে বুঁদ হয়ে ছিলাম তারা সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ হয়ে আরো যেনো বেশিরকম সত্য হয়ে ধরা দিলো! লেখক পাপড়ি রহমানের সফলতা এইখানেই যে তার উপন্যাসের চরিত্ররা কাল্পনিক নয়, কোনো সুদূর অতীতের নয় বরং তারা আমাদের আজকের পৃথিবীর আমাদের চারপাশের অতি পরিচিত মানুষজন।এই বাবুবাজার ব্রিজ ধরে এগোলেই দু-পাশের অসংখ্য ঘাট এবং ব্রিজ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই আগানগরের শুরু।
‘নদীধারা আবাসিক এলাকা’ মূলত নদী ও নারীর কথকতা। নারী আর নদীকে এক করে দেখার ধারণা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়, হয়তো প্রকৃত অর্থে নারীরাই বয়ে চলে জীবনের উর্বরতার পলি। পুরুষ এক নিমিত্ত মাত্র, তবু দিনশেষে এখনো দুনিয়াব্যাপী পুরুষই নিয়ন্ত্রক, সমাজ নারীর শ্রমটুকু বিনামূল্যে অধিকারের মতো চেটেপুটে নিয়ে তাকে উচ্ছিষ্টের মতো দিনের পর দিন পায়ে দলে চলেছে।
নদীর বাকঁবদলে যেমন জন্ম হয় নতুন জনপদের, তেমনি পুরুষের হাতবদলেও বদলে যায় নারীর জীবন, জীবিকা, অস্তিত্ব। পৃথিবীর তাবৎ নারী যেমন হাজাররকম অত্যাচার সয়ে বয়ে চলে সৃষ্টির মহিমা, নদীও তেমনি… “এ নদী তবু বেঁচে থাকে। মরে যেতে যেতে ফের যেন সে জীবন ফিরে পায়।… আমাদের নদী বুড়িগঙ্গাও জানে, তার কৃষ্ণ জলের ঘূর্ণিতে যে মাতম ওঠে, সেই ধ্বনি কতটা করুণ, কতটা অসহায় সেই আর্তি!” নদী বাচঁলে নারীও বাঁচত; অধিকার যে শুধু ভোগ করা নয়, সংরক্ষণও বটে, সেই শিক্ষাটা আমরা কবে যে আর শিখব!
 বরাবরের মতোই পাপড়ি রহমানের গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য। বস্তুত এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস যার প্রধান চরিত্ররা সকলেই নারী। ইসমত আরা, রেফুল, নয়তুন্নেসা, শনতারা,দুরদানা বেগম, বিলাতন বিবি, এলেমজান — এদের সকলের জীবনই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভয়ঙ্কর নখরে ক্ষতবিক্ষত। সেই চক্র ভেঙে নতুন সমাজ বিনির্মাণের শিক্ষা এদের নেই, তবুও নিজের এবং পরিবারের দায়িত্ব নেবার মতো মনোবল এবং সক্ষমতা তারা তাদের শ্রমে-ঘামে অর্জন করে। সমাজের উঁচুতলার নারীদের সাথে শ্রমজীবী নারীদের প্রধান পার্থক্য হলো তাদের প্রতিমুহূর্তে লড়াই-সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় এবং সেটা বাপদাদার জোরে নয়, কিংবা সার্টিফিকেটের জোরে মাসকাবারি মাইনের জোরে নয়। পুরোটাই তাদের শারীরিক পরিশ্রম এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার জোরে। পাপড়ি রহমান সেইসব সহজাত সৃষ্টিশীলতাকে প্রত্যেকটি নারীচরিত্রের ভিতর আবিষ্কার করেছেন।
বরাবরের মতোই পাপড়ি রহমানের গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য। বস্তুত এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস যার প্রধান চরিত্ররা সকলেই নারী। ইসমত আরা, রেফুল, নয়তুন্নেসা, শনতারা,দুরদানা বেগম, বিলাতন বিবি, এলেমজান — এদের সকলের জীবনই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভয়ঙ্কর নখরে ক্ষতবিক্ষত। সেই চক্র ভেঙে নতুন সমাজ বিনির্মাণের শিক্ষা এদের নেই, তবুও নিজের এবং পরিবারের দায়িত্ব নেবার মতো মনোবল এবং সক্ষমতা তারা তাদের শ্রমে-ঘামে অর্জন করে। সমাজের উঁচুতলার নারীদের সাথে শ্রমজীবী নারীদের প্রধান পার্থক্য হলো তাদের প্রতিমুহূর্তে লড়াই-সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় এবং সেটা বাপদাদার জোরে নয়, কিংবা সার্টিফিকেটের জোরে মাসকাবারি মাইনের জোরে নয়। পুরোটাই তাদের শারীরিক পরিশ্রম এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার জোরে। পাপড়ি রহমান সেইসব সহজাত সৃষ্টিশীলতাকে প্রত্যেকটি নারীচরিত্রের ভিতর আবিষ্কার করেছেন।
জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, সংসারযাপন, মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব — বস্তুত সমাজের প্রতেকটি সম্পর্কই নারীর উপর পীড়নমূলক। রেফুলের মা এবং বাবা দুইজনই রেফুলকে যখন-তখন নির্বিচারে পিটিয়ে তাদের অভিভাবকত্ব প্রমাণ করে। খৈমন বিবির ভয়াবহ বাক্যবাণ আর ছোটবোনের মৃত্যুর দায় রেফুলকে রীতিমতো মানসিক ভারসাম্যহীনতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। রেফুলও জন্মাবধি সেই অপরাধবোধ বয়ে চলে। আর স্বামী মিনহাজ বেপারী লঞ্চের কেবিনেই নববিবাহিত স্ত্রী রেফুলকে ধর্ষণ করে, তার কাছে রেফুল শুধুই স্তন আর যোনী। রেফুল কোনো দোষ না করেও সারাজীবন নিজেকে দোষী জেনে এসেছে, সর্বগ্রাসী এই অপরাধবোধ রেফুলকে একধরনের মানসিক বিকারগ্রস্ততার দিকে ঠেলে দেয় এবং সম্ভবত সেজন্যেই একের পর এক মৃত সন্তান প্রসব করে চলে সে। নারীর আবার মানসিক স্বাস্থ্য! সন্তানসম্ভবা নারী যেখানে স্বামীর রোজরাতের ধর্ষণের হাত থেকে মুক্তি পায় না সেখানে তার স্বাস্থ্যসেবা কল্পনাতীত। নারীর জননাঙ্গ হয় ভোগের নয়তো প্রজননের। এর বাইরে নারীর আর পরিচয় কি?
জন্মাবধি এতসব অত্যাচার সহ্য করেও রেফুল সুরেলা গলায় গীত বান্ধে! আশ্চর্য এত ক্রন্দনেও রেফুলের কল্পনাশক্তি, জীবনবোধ, নিজেকে সুখী করার অসম্ভব ক্ষমতা হারিয়ে যায় না। দুর্দান্ত রকমের মনোজাগতিক বিশ্লেষণে সমাজের এই সকল পুরুষতান্ত্রিক নিয়মের ভেতরেও নারীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাগুলোকে উন্মোচন করেছেন লেখক পাপড়ি রহমান। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ধর্মান্ধতা এবং সামাজিক প্রবণতা নারীর অদম্য সৃষ্টিশীলতাকে লালন না করলেও একেবারে থামিয়ে দিতে পারেনি। যদিও সত্যিকারের ধর্মকথা, কোরান কিংবা হাদিস তারা পড়ে না। তাদের তালিমের আসরে তারা নিজেদের বান্ধা গীত গায়, ধর্মকাহিনি বলতে তারা পড়ে ‘বিষাদসিন্ধু’।
ইসমত আরার স্বামী হাবুল সরকার তারই প্রতিবেশী জয়নাল মিয়ার স্ত্রী জুলেখা বেগমের সাথে বলা নেই কওয়া নেই একদিন হঠাৎ রাতের আঁধারে জুলেখা-জয়নালের পুত্রসন্তান সহ পালিয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো পালানোর সময় কন্যাসন্তানকে কিন্তু তারা নেয় না, এমনকি ছোট পুত্রসন্তান বাবুল সরকারকেও রেখে যায় ইসমত আরার পেলেপুষে বড় করে তোলার জন্য। ইসমত আরা মেস খাওয়ানোর কাজ করে এবং জয়নাল মিয়ার সঙ্গে নিরানন্দ বিবাহিত জীবন যাপন করে অমানুষিক পরিশ্রমে বাবুল সরকারকে বড় করে তোলে। আর ঠিক তখনই তার পূর্বের স্বামী হাবুল সরকার পিতার অধিকারে পুত্রকে নিতে আসে কারণ এখন সে কর্মক্ষম, উপার্জন করার উপযুক্ত! ইসমত আরা আরো তাজ্জব বনে যায় যখন দেখে বাবুলেরও তাতে সম্মতি আছে। বাবুল এই সমাজ থেকে মায়ের প্রতি সহমর্মী হবার শিক্ষাটা পায়নি, বরং পিতার প্রলোভনে সম্মতি দেয়াটাকেই সত্য আর স্বাভাবিক বলে জেনেছে। এই সমাজ নারী এবং নারীর শ্রমের প্রতি কতটা মর্যাদাহীন বাবুল সরকার তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়! পক্ষান্তরে জয়নাল মিয়ার শীতলতা বাবুলের পিতৃসঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষাকে আরো উস্কে দিয়েছে। ইসমত আরা যদি মিতুকে নিজের সন্তানস্নেহে লালন করতে পারে জয়নাল মিয়া কেন বাবুলকে নিজের ছেলের মতো দেখতে পারে না? এটি কি শুধুমাত্র জয়নাল মিয়ার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নাকি একটি অমানবিক সমাজব্যবস্থা যা আমরা বছরের পর বছর প্রশ্নাতীতভাবে বয়ে চলেছি? ইসমত আরা অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করে ভেবেছিল, জীবনযুদ্ধে জয়ী সে… কিন্তু হাবুল সরকার তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মের ফাঁদ থেকে তার মুক্তি মিলল কই? সত্যিই তো কিসের জোরে সে ছেলেকে আটকাবে? জয়নাল মিয়া তো একমুহূর্তের জন্যও বাবুল সরকারকে নিজের সন্তান ভাবেনি। স্বামীপরিত্যক্তা হওয়ার শোক সামলে উঠলেও, সন্তান হাতছাড়ার কষ্ট এবং হাবুল সরকারের সামাজিক চালাকির কাছে হেরে যাবার যন্ত্রণা সে আর সইতে পারল না! “আগানগরে প্রথম পা দিয়েই ইসমত আরা জেনেছিল, বুড়িগঙ্গা তার একমাত্র ঠিকানা। স্হায়ী, বর্তমান। এই নদীই তার সর্বস্ব। কালো জলের ঘূর্ণিতুলে নদীর যে মাতম তা ইসমত আরারই অন্তর্গত মাতম। … ইসমত আরা নিজেই হয়তো মাছকুমারীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। … ইসমত আরা হয়তো ইচ্ছে করেই তুফানের বুড়িগঙ্গায় ডুব দিয়েছিল।”
নয়তুন্নেসার স্বামী মারা যাবার পর তার দ্বিতীয় বিয়ে তার সন্তানদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত করে তোলে। আশ্চর্য বিষয় তার স্বামীরও কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে এবং প্রথমপক্ষ আঙ্গুরা বিবি সাক্ষাৎ জীবিত কিন্তু তাতে রহমআলীর ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক জীবনের কোনোই ব্যাঘাত ঘটেনি। নারীর প্রতি এই যে নিপীড়নমূলক, বৈষম্যমূলক সমাজ আমরা তৈরি করেছি নয়তুন্নেসা তার এক জলজ্যান্ত প্রমাণ।এইসব সামাজিক মনোবৃত্তি শুধুমাত্র আইন পরিবর্তন করে কিংবা শিক্ষার হার বাড়িয়ে ঠিক করে ফেলা যাবে না, এর জন্য প্রয়োজন সঠিক মানবিক শিক্ষা। শুধু আগানগর কেন সমগ্র বাংলাদেশেই এর অভাব সুস্পষ্ট। “মাইয়ানুকগো আদতে কুনুখানেই শান্তি নাই; সোয়ামীর কাছে না, সন্তানের কাছেও না। মাইয়ানুক অইয়া জন্মাইলে মাটির লাহান থাকতে অইব এইডা কেমুন বিচার? এই দুনিয়ারে মাইয়ানুকরা খালি দিয়া যাইব, বেবাকেই হের থিক্যা খালি রস নিব, আহার নিব, আশ্রয় নিব … কিন্তু কেউ তাগো কিছু দিব না। এমনকি দেওনের কথা ভাববও না। সোয়ামী ভাবে মাইয়ানুকরে ফির আলাদা কইরা কি দেওন লাগে? আর সন্তান ভাবে, মায়েরে ফির আলাদা কইরা কি দেওন লাগে?”

চরিত্র চিত্রণের বাইরে পাপড়ি রহমানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো কোনো-একটি স্থানের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উপকরণ ইংরেজিতে যাকে বলে কালচারাল আর্টিফ্যাক্ট সেগুলোকে তুলে আনা। তার উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পে প্রচুর লোকজ গীত, কবিতা এসব রয়েছে — “সোনার ধান দেই রূপার কুলায়, কে মা অন্ন দিবি এত বেলায়?” গানের পাশাপাশি ‘নদীধারা আবাসিক এলাকা’-য় উঠে এসেছে মোষের শিং দিয়ে বানানো কাঙ্গাই (চিরুনী) এবং ধান আর চিকন দুর্বায় সাজানো মাগনাকুলার মতো নিত্যব্যবহার্য উপাদান। চিক্কুন চাউলের ভাত, কাঁচা আমের ফলি, বোয়ালের ছাওয়ের কষানো, মুরগার সালুন, শুকনা মরিচ, সরিষার তেলে ভেজে পেঁয়াজ ডলে মসুরডাল ভর্তা, এমন সব একান্ত নিজস্ব রান্নার পদ ও উপকরণের বর্ণনাও ‘নদীধারা আবাসিক এলাকা’-য় আমরা পেয়ে যাই। এসব সাংস্কৃতিক উপাদানের ভেতর লুকানো আছে আমাদের হাজার বছরের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস। পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়েছে লেখক হয়তো এই জায়গাটায় আরেকটু বেশি মনোযোগী হতে পারতেন। ঘাটের ইতিহাস, বুড়িগঙ্গার ইতিহাস, মোগল আমলের ঢাকার শহরতলির জীবনযাত্রার ইতিহাস এই উপন্যাসে প্রাসঙ্গিকভাবেই আরেকটু বেশি জায়গা পেতে পারত।
পাপড়ি রহমানের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো তার ভাষা ও সংলাপ, গল্প বলার ধরন এবং তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। মেদহীন, ঝরঝরে, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ তার আরাধ্য নয়, বরং তার বাক্যগুলো মানবিক আবেগে মাংসল, বৃষ্টিভারে নুয়ে-পড়া মেঘের মতো পরিপূর্ণ। একই অনুভূতির নানারূপে বিস্তার এবং পুরো দৃশ্যপট পাঠকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলবার জন্য কথাসাহিত্যে এই বর্ননার কোনো বিকল্প নেই। পাপড়ি রহমান দীর্ঘ দুই দশকে নিজস্ব ভাষাভঙ্গি নির্মানণ করেছেন। শব্দবিন্যাস বা ইংরেজিতে যাকে বলে কলোকেশন সেখানে পাপড়ি রহমানের জুড়ি মেলা ভার। ‘চিক্কুরবাক্কুর’, ‘আন্ধারকুন্ধার’, ‘সামানউমান’, ‘ছিট্টিছান’, ‘গিরগিরগির’, ‘ন্যাড়াটুন্ডা’, ‘ঝাপ্পুরঝুপ্পুর’ — এ-রকম আরো হাজারো শব্দবন্ধ তার লেখায় যোগ করে এক বাড়তি মাত্রা। লেখকের বর্ননায় সবকিছুই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। দুপুর, সন্ধ্যা, রাত, ভোর — এ-রকম নানা সময়ের বর্ণনা আমরা এ-উপন্যাসে পাই। সময়কে অক্ষরের মালায় গেঁথে রাখা এক দুরূহ কর্ম বটে। পাপড়ি রহমান আগানগরের বর্তমান সময়কে এই মানবিক আখ্যানে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আর অপেক্ষা করে আছেন এক নতুন সময়ের যখন প্রকৃত মানবিক শিক্ষা এনে দেবে আমাদের আগামীর ভোর, সূর্যালোকের সচ্ছলতা, নতুন দিন। আগামী উপন্যাসে সেই নতুন দিনের জয়ধ্বনি শোনার অপেক্ষায় থাকলাম। “নিমপাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েল পাখি শিস বাজিয়ে গেছে বহুক্ষণ। কিন্তু সোমত্ত ভোর পৃথিবীর বুকে এখনো ফুটে ওঠে নাই। চারপাশে পদ্মপাতার মতো গোল গোল অন্ধকার শুয়ে আছে। এইসব ছড়িয়েছিটিয়ে-থাকা অন্ধকার ফুরিয়ে যেতে সময় লাগবে। সূর্যের শিশুদাঁতে আলো ঝলমলিয়ে না-ওঠা পর্যন্ত ওইসব অন্ধকারেরা শুয়ে বসে থাকবে। … এইসব ছোপ ছোপ অন্ধকার দূর করতে হলে রোদ্দুরের চড়তা-ঝিলিক লাগে।”
… …
- ইকোক্রিটিসিজমের ধারায় আখ্যানপুঞ্জ || উম্মে কুলসুম রত্না - May 18, 2020

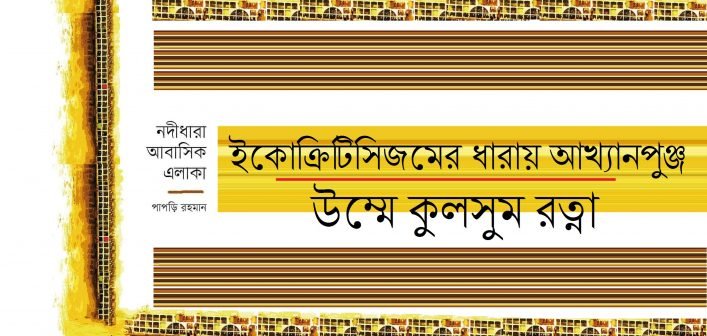
COMMENTS