বাংলাদেশের সিনেমার পথচলা প্রায় শত বছরের। শুধু যদি সিনেমা প্রদর্শনীর পয়লা আয়োজনের দিন থেকে হিসেব করা যায়, তাহলেও একশো বছর বয়স গড়িয়ে গেছে। আবার ইংরেজ ভূ-ভারতে পূর্ব-বাঙলার জমিনে প্রথম ছায়াছবি ‘সুকুমারী’ (১৯২৭/২৮) নির্বাক প্রদর্শনীর কথা আমলে রাখলে নির্মাণের ইতিহাস দাঁড়ায় ৯২/৯৩ বছরের। এরপর আবার ১৯৪৭-এ নামপরিচয় পাল্টে যাওয়ার ইতিহাস। আবার পয়লা সিনেমা বানানোর অস্থিরতা। ‘মুখ ও মুখোশ’ (১৯৫৬)-এর গল্প। এবার সবাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের, অর্জনের নয়া কাহন। সেই হিসেবে ঢাকায় সিনেমা করার ইতিহাস প্রায় ৬৩ বছরের। এখানেই ইতি নয়। শেষ দফায়, ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে “লোকে বলে সোনা / সোনা নয় তত খাঁটি / তার চেয়ে খাঁটি বাংলাদেশের মাটি”-এর নিরিখে বাংলাদেশি সিনেমার সফল চিত্রায়নের বয়স দাঁড়ায় ৪৮ বছরের। এর মাঝে বাংলাদেশের সিনেমা মুখোমুখি হয়েছে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের, যেমন মনে করা যাক — উর্দু সিনেমার বিপরীতে লোকগাথাভিত্তিক সিনেমা করার মধ্যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, ইতিহাসভিত্তিক ছবি নির্মাণের ঢল, রূপালি পর্দায় পূর্ব-বাঙলার মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের গল্পের ঠাঁই করে নেয়া ইত্যাদি।
স্বাধীনতাউত্তরকালেও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সিনেমার নির্মাতাদের মধ্যে রাজনৈতিক বাস্তবতা নির্মাণের ক্ষেত্রে, হাল আমলের ধরি মাছ না ছুঁই পানির বদলে স্পষ্ট অবস্থান লক্ষ করা গেছে। ধরা যাক, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী, রাজনৈতিকভাবে জোচ্চোর নেতা/চেয়াম্যান/মন্ত্রীর চরিত্র চিত্রায়নে কোনো ধরনের আপোস পরিলক্ষিত হয় না। বরং, সরকারি বয়ানের উল্টো দিকেই নির্মাতারা সিনেমার মুখ তুলে ধরেছেন দর্শকবৃন্দের পানে।
যা-ই হোক, বাংলাদেশি সিনেমার ইতিহাস বেশ নিদারুণ … বিশেষ করে শহুরে বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা, বিশ্বসিনেমার জ্ঞান রাখা ফিল্মমেকারদের ক্ষেত্রে তো বটেই। শুরুতেই এফডিসির সাথে মনোমালিন্য, তারপর সরকারের অসহযোগিতা, এরপর কারিগরি সীমাবদ্ধতা, আর অর্থনৈতিক সংকট এর দোহাই তো লেগেই থাকল। অতি সংক্ষেপে, এইসব নোকতা টুকে রাখার উদ্দেশ্য এইটাই যে, আলাপের গাড়িটিকে সমসাময়িক বাংলাদেশি সিনেমা করায় বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবমুখীনতা এবং উৎসবপিয়াসী এসব সিনেমার রাজনৈতিকতার গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা। একই সাথে,২০০০ সন পরবর্তী সময়ে বিএফডিসির বাইরে নির্মিত তথাকথিত স্বাধীন/মুক্ত/বিকল্প ধারার সিনেমার (বক্তব্যে রাজনৈতিকতার) নির্মাণ, বিদেশি উৎসবে প্রেরণের জরুরত এবং ‘ভালো সিনেমা’-র সংজ্ঞায়নে এর ভূমিকার তত্ত্বতালাশ করা।
সাম্প্রতিক সময়ে উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পাশাপাশি উৎপাদন ও পরিবেশনের কাজেও জড়িয়ে পড়ছে চলচ্চিত্র-উৎসবগুলো। এই প্রবৃত্তির প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, উৎসবকেন্দ্রিক বিবিধ কাঠামোর ভেতর, যেমন — ট্যালেন্ট ক্যাম্পাস, পিচিং সেশন, প্রজেক্ট ফান্ডিং, ডিস্ট্রিবিউশন লেবেল, অনলাইন স্ট্রিমিং ইত্যাদি। এই চলচ্চিত্র-উৎসবগুলো শুধু বা মাত্র দর্শকদের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের উপায় হিসেবে চরিত্র জারি রাখতে পারছে না বরং চলচ্চিত্র প্রদর্শনের প্রাথমিক শর্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে একটি চলচ্চিত্রের ধারণার বিকাশ, অর্থায়ন, উন্নয়ন/সম্প্রসারণ এবং বিপণনের প্রশ্নে যৌগিক ভূমিকা পালনে অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে, চলচ্চিত্রের উৎসবগুলো প্রদর্শনের চাইতে ক্রম-পরিবর্তনশীল সিনেমার বাজারে নিজস্ব অংশীদারী কাঠামো গড়ে তুলেছে। ফিল্মইন্ডাস্ট্রির সাথে রাজনীতি ও অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক চলকের সেতুবন্ধনরূপে চলচ্চিত্র-উৎসব গুরু ভূমিকা রাখছে। শুধু তা-ই নয়, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র-উৎসবের স্বভাবজাত বহুজাতিক চরিত্র, জাতীয়তাবাদী প্রবণতার সাথে প্রতিসাম্য যেমন রক্ষা করে থাকে, তেমনি নির্মাণ ও বিপণনের মাঝে ক্রিয়াশীল সম্পর্ক গড়ে তুলছে। বর্তমান সময়ে উদার-অর্থনৈতিক বাস্তবতায় চলচ্চিত্র-উৎসবগুলোর মাঝে ভূ-রাজনৈতিক বা দর্শককেন্দ্রিক অ্যাজেন্ডার তুলনায় ব্যাবসায়িক অ্যাজেন্ডার গুরুত্ব অধিক।
ধরা যাক, ফ্রান্সের কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের কথা। এটি আগাগোড়া একটি ‘ব্যবসায়িক’ চলচ্চিত্র-উৎসব, সাধারণ দর্শকদের অংশগ্রহণের সুযোগ এখানে ঘটে না বললেই চলে। এ-কারণে বাংলাদেশ থেকে কান ফেস্টিভ্যাল চলাকালীন এর আশেপাশের সহযোগী কর্মসূচিতে বাংলাদেশের কেউ অংশ নিলেই বেশ ঘটা করেই তার সংবাদ ছাপতে দেখা যাবে মিডিয়াতে।
এই কাতারে বার্লিন/ভেনিস/টরেন্টো/বুসান ফিল্মফেস্টিভ্যাল, ইন্টারন্যাশনাল ডকুমেন্টারি ফিল্মফেস্টিভ্যাল আমস্টারডাম এবং কারলোভি ভ্যারি, লোকার্নো, থেসালোনিকি, রটারডাম সহ আরও অনেক চলচ্চিত্রপার্বণের নাম যোগ করা যেতে পারে। এখন, এইসব নামের সাথে যদি আপনি হাল আমলে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয়া বা ভিনদেশি চলচ্চিত্রপার্বণে সমাদৃত হওয়া চলচ্চিত্রগুলোর তালিকা মিলিয়ে নেন, তাহলে সহজেই এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিপ্রাপ্ত, ভালো, বিশ্বের বুকে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করা চলচ্চিত্রগুলোর চরিত্র সমন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে।
বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের খবরে ইদানীং যেমন দক্ষিণ কোরিয়ার বুসান চলচ্চিত্র-উৎসবের নাম প্রতিনিয়ত শোনা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ১৯৯৬ সন থেকে চালু হওয়া বুসান চলচ্চিত্র উৎসব এখন এশিয়া অঞ্চলের ফিল্মবিজনেসের অন্যতম মহাজন। বুসান তার পূর্বসূরি অর্থাৎ হংকং, টোকিও ফিল্মফেস্টিভ্যালের কাছে থেকে উৎসবভিত্তিক সিনেমা বিপণন, পরিবেশনের মার্কেটটাই শুধু হস্তগত করেনি, বরং অন্তঃ-এশীয় চলচ্চিত্র উৎপাদন ব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
আদতে, এই উৎসবগুলো (বাংলাদেশের)তথাকথিত স্বাধীনধারার চলচ্চিত্রগুলোর সম্ভাব্য প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শকের মেলবন্ধন হিসেবে কাজ করে থাকে। এ-কারণেই ফিল্মবেত্তা ডিনা ইওরদানভামনে করেন, বিশ্ব চলচ্চিত্রব্যবসায় শুধু প্রযোজনা ও পরিবেশনায় নয় এই ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কর্তা, নির্মাতা, প্রযোজক এবং সমালোচকের সংযোগবিন্দুরূপে ফেস্টিভ্যাল গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখছে।
সংস্কৃতি-সমালোচক পল ওয়াইলম্যান দাবি করেন, যদিও চলচ্চিত্র-উৎসবগুলো এই প্রতীতিই জাহির করে যে তারা সিনেমার বৈশ্বিক উদ্ভাসন ও প্রচলনে গতিপথ উন্মোচন করে থাকে, কার্যকরণে, দেখা যায় যে তারা কেবলই এটি বাহানা হিসেবে ব্যবহার করে এবং নিশ্চিত করে যে অবাণিজ্যিক ছবিমালা যেন আনুষ্ঠানিক বিপণনকাঠামোর বাইরে থাকে। অর্থাৎ, চলচ্চিত্র-উৎসবগুলো সিনেমাকে দর্শকদের কাছে কোনোভাবেই নেয় না এবং কার্যকরীভাবে নিশ্চিত করে যে — ছবিগুলো যেন কোনোভাবেই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নাগালে না পৌঁছায়। পল ওয়াইলম্যানের দাবির সাথে অনেকে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন এবং ভাবতে পারেন যে, স্ববিরোধী হলেও চলচ্চিত্র-উৎসব ধারণাটি গ্লোবাল সিনেমার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।
এই ফেস্টিভ্যালগুলোতে ছবি পাঠানো এবং ফলাও করে সংবাদ ছাপানোর অন্যতম রাজনীতি হলো, আর্ট বা শিল্প হিসেবে ছবিটিকে নির্ণায়িত করার প্রচেষ্টা মাত্র। প্রাবন্ধিক, কবি, অনুবাদক, সংস্কৃতি-সমালোচক লুইস হেইডি তার প্রখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্য গিফট’-এ বলেছেন, “আর্ট বা শিল্পের মধ্যে কী আছে/থাকে, যখন এটি বাজারে বিকিকিনি করা যায়, তখন আর্ট বা শিল্প নামের ধারণাকে কিভাবে খাঁটি পণ্যের ধারণা থেকে আলাদা করা সম্ভব?” বিতর্কের খাতিরে তিনি আরও বলেন, “শৈল্পিক কর্ম যুগপৎভাবে দুই রীতির অর্থনৈতিক কাঠামোর অধীনে থাকে — বাজার-অর্থনীতি ও প্রকৃতিদত্ত গুণ অর্থনীতি। এর মধ্যে যে-কোনো একটি ক্রিয়াশীল থাকলে চলে, তদুপরি, মার্কেট ছাড়া আর্ট টিকে গেলে, প্রকৃতিপ্রদত্ত সহজাত গুণ বিনে আর্ট এর অস্তিত্ব নেই।” এই আলোচনার খাতিরে যদি ‘আর্ট’-এর স্থলে ‘সিনেমা’ পড়া হয়, তাহলে হেইডি-র বক্তব্যের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর্ট বা সিনেমাকে প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণের সাথে রূপকায়িত করার বিষয়টি ব্যক্তির সজ্ঞাকে নির্দেশ করে। হেইডি-র মতে প্রকৃতিপ্রদত্ত গুণ অর্থ প্রতিভা, মায়ের আশীর্বাদ, খোদায়ি সম্প্রদান — যা বাজার থেকে কেনা প্রায় অসম্ভব, যার আছে তার আছে, যার নাই তো নাই। তাই, সাধারণ অর্থে আমরা মনে করে থাকি — শিল্পী বা সিনেমা-করিয়েরা যখন শিল্প বা সিনেমা করেন, তখন সৃজনী প্রক্রিয়াটি অংশত অন্য কাজ থেকে নেওয়া অনুপ্রেরণা, অংশত তার কল্পনার দৌড়ের মিশ্রণ, যা হৃদয়ে দোলা দিয়ে যাবে, আত্মার তৃষ্ণার খোরাক জোগাবে, অথবা বেঁচে থাকার সাহস জোগাবে। মূল্য দিয়ে একটি শিল্পকর্ম খরিদ করলে বা টিকেট কেটে সিনেমাহলে ঢুকলেই যে এই অনুভূতিগুলো দর্শকের জন্য প্রস্তুত থাকবে তা বলা যাবে না। কেননা, ওই সিনেমা বা শিল্পকর্মের মাঝে যদি তা অন্তর্নিহিত না থাকে, এর সবটা থেকেই দর্শক বঞ্চিত হবেন। এই অকৃত্রিম সৃজনশীলতা বিনে যে-কোনো সিনেমা বা শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে ফর্মুলা, একঢালা ও বাণিজ্যিক নমুনা মাত্র। ওলন্দাজ দৃশ্যশিল্পী ও অর্থনৈতিক-সমাজতাত্ত্বিক হান্স আবিং-এর চিন্তাধারাতেও প্রায় একই সুর লক্ষ করা যায়; তার ভাবনাকে এই প্রেক্ষাপটে স্থানান্তর করে বলা যায় যে, প্রচলিত খাতের বাইরে থেকে লগ্নি নিয়ে বা বিকল্প লগ্নিতে সিনেমা করলেই একটি সিনেমার শিল্পমান স্বয়ংক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে যায় না।
এদিকে, ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, দার্শনিক, জনবুদ্ধিজীবী পিঁয়েরে বোরদিঁও হেইডি-র মতো আর্টের বিশুদ্ধতা নিয়ে ভাবালু হওয়ার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তার প্রস্তাব অনুসারে, শিল্পের অর্থনীতি দুইটি যুক্তির লেন্স দিয়ে বিচার করা করা যায় : বিশুদ্ধ শিল্পের জন্য অ্যান্টি-ইকোনোমি এবং বাজারি শিল্পের জন্য কমার্শিয়াল ইকোনমি। কিন্তু, তিনি এও নির্দেশ করেছেন যে, শিল্পের সৃজন মূলত ঘটে থাকে এই দুই প্রান্তিক সীমার মধ্যবর্তী অবস্থানে। এখানে, ‘শিল্পের খাতিরে শিল্প’-কে ফেলেছেন ‘অটোনোমাস’ বর্গে এবং বিপরীতে রেখেছেন ‘হেটারোনোমাস’ বর্গ যেথায় বাজারের নিরিখে শিল্পবস্তু উৎপাদোন করা হয়। যদিও, সমাজে এবং বাজারে দিব্যি আমরা দেখতে পাই যে সংস্কৃতি এবং পণ্য একই থালায় মাপা হতে। তারপরেও, বোরদিঁও-র ভাষ্যমতে হেটারোনোমাস প্রেক্ষিত থেকে যে-শিল্প পয়দা করা হয় তা ‘প্রকৃত’ শিল্প অর্থে উত্তীর্ণ হয় না। বিদ্যায়তনিক পরিসরে বোরদিঁও-র চিন্তা-কাজকে ফিল্মফেস্টিভ্যাল অধ্যয়ন-বীক্ষণের প্রতিষ্ঠাতা জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার কাজের বরাতে নির্ণয় করা সম্ভব হয় যে, ফিল্মফেস্টিভ্যালগুলো কীভাবে সাংস্কৃতিক বৈধকরণের জমিন হিসেবে কাজ করে থাকে।
বোরদিঁও-র চিন্তাপ্রকৃতি আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে বৈশ্বিক চলচ্চিত্রের বাজারে কো-প্রোডাকশন বা সহ-প্রযোজনার ব্যবসা রমরমা কেন। ইদানীং, প্রায়ই শোনা যায় কোনো না কোনো নির্মাতা ফিল্মবাজারের অংশ কো-প্রোডাকশন মার্কেটে সম্ভাবনাময় প্রকল্পের পুরস্কার জিতেছে; কিন্তু কেন এই পুরস্কার বা অর্থ প্রদান? শিল্পের খাতিরে শিল্পের উন্নয়ন হেতু নাকি অন্য কোনো কারণে? গ্লোবাল ফিল্মমার্কেটে কো-প্রোডাকশনের বাজার মূলত মিডিয়ার কর্পোরেটাইজেশনের ফলশ্রুতি বলে মনে করেন লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া, মিউজিক ও কালচার স্টাডিজের অধ্যাপক ডেভিড হেস্মনঢালঘ। ১৯৯০-র দশক থেকেই স্বাধীন ধারার এবং নির্মাতা-নেতৃত্বাধীন সিনেমা প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রশ্নে কো-প্রোডাকশন একটি গ্রহণযোগ্য মান হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীকালে ইউরোপের দেশগুলোতে ট্রান্সকালচারাল ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগের বিধিবিধান শিথিল হয়ে গেলে, এই ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর ফিল্মফেস্টিভ্যালগুলো হয়ে ওঠে এর কেন্দ্রবিন্দু। এতে, নির্মাতা এবং প্রযোজক প্রতিষ্ঠান উভয়ের লাভ। কো-প্রোডাকশনের এই ফন্দি শুধু নির্মাতাকেই নয়, সহ-প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানকেও বড় প্রযোজকের সুনজরের দিকে এগিয়ে দেয়। অধ্যাপক ডেভিড মনে করেন, ছোট মাছকে বড় মাছ গিলে ফেলার এই খেলায় শিল্পের দুনিয়ায় টাকার জোর, জবরদস্ত আকারে বেড়েই চলছে। শিল্প উদ্ধারের নামে এ এক আরেক কর্পোরেট পুঁজির খেলা।
তো, এখন আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন ফেস্টিভ্যালকে ঘিরে গড়ে-ওঠা বাংলাদেশি এই স্বাদহীন ধারার সিনেমাগুলোর সম্যসাটা কোথায়? ছায়াছবি হিসেবে এইগুলো গ্লোবাল দুনিয়ায় বেশ নাম কুড়াচ্ছে, মিডিয়া-সমাজ ভালো বলে বাহবা দিচ্ছে, দর্শক একটু হলেও সিনেপ্লেক্সে গিয়ে সময় কাটাতে পারছে … কিন্তু, প্রশ্নের শুরুটা ঘটছে এখান থেকেই।
২০০০ সন পরবর্তীকালে ডিজিটাল মিডিয়ার সহজলভ্যতা, বেসরকারি প্রযোজনা, মাল্টিপ্লেক্সের সুবিধা এমনকি সরকারি অনুদান — সবই আসতে থাকল কিন্তু সিনেমাটা আর আসলো না। কারণ, পত্রিকা খুললেই যেখানে জীবন্ত গল্পের ছড়াছড়ি সেখানে উৎসবমুখী নির্মাতাদের কাছে গল্পই একটা সংকট। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার মুখোমুখি না হয়ে, তা অবজ্ঞা করে ছবি বানাতে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হয় বাস্তবিক বাস্তবতার মিশেলে গড়াবাস্তবতার; যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না নির্মাতা কি দেখাতে চান বা যা দেখাতে চাইছেন তার কারণই-বা কী। দুর্বল চিত্রনাট্য থেকে চরিত্রের জবানে লেপাপোঁছা সংলাপ আর ডাহা ডাহা গালভরা বুলিতে সয়লাব সিনেমাগুলোর বিধেয় যেন একটাই আর তা হলো — মধ্যবিত্ত সংগ্রামী নারী বা বিভ্রান্ত পুরুষের চরিত্র চিত্রায়ন। বিবিধ অজানা কারণে অস্থির নির্মাতারা সুস্থির গল্প বলতে চান বলে দাবি করলেও তাদের গল্পের বুননের মাঝে মানুষের জীবনের গল্পের কোনো ঠাঁই নেই, সময় নিয়ে ডিটেইলিং-এর অবসর নেই। যেন পরীক্ষার হলে বসে সব ক’টা প্রশ্ন টাচ করে যাওয়ার নিয়তে থাকা পরীক্ষার্থী।
মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজকে টার্গেট অডিয়েন্স হিসেবে মাথায় রেখে স্বাধীনধারার অল্পপ্রাণ ছবিগুলো অধিকংশ ক্ষেত্রে আদর্শবাদের ধ্বজা ধরে, জানা সমস্যাবলির ক্লিশে চিহ্নায়ন ও সমাধানের পথ ব্যবহার করে থাকে। এই সমাধানের পথে পথে ছড়িয়ে থাকে এলিট সমাজের দর্শন। এতে না থাকে সমাজের গরিষ্ঠ মানুষের ভাবনার কোনো প্রতিফলন, না থাকে সামাজিক বাস্তবতার কোনো প্রতিফলন। ঠিক যেমন, বিএফডিসির নির্মাতাদের শুনতে হয় যে, তারা দর্শকের বিনোদনের খোরাকের দোহাই যেমন-খুশি-তেমন ছবি বানিয়ে থাকেন, প্রতিতুলনা করলে দেখা যায় যে স্বাধীনধারার ইস্যুভিত্তিক সিনেমা করিয়েরাও দর্শকের নাম ভাঙিয়ে এমনতর সিনেমা করেন। পার্থক্য এইটুকুই যে, তাদের দর্শকবৃন্দ এই শহরনিবাসী নন। তারা সারাবিশ্বে ছড়িয়েছিটিয়ে আছেন, উৎসবের টিকেটের লাইনে। যদিও, তারা সবসময় বলে থাকবেন তাদের ছবি দেশীয় দর্শকদের মাথায় রেখেই বানানো। ‘মাটির ময়না’ থেকে শুরু করে বিদেশি প্রযোজক বা ফেস্টিভ্যালমুখী সিনেমাগুলোর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন-সংস্কৃতির ইস্যুসমূহের প্রাধান্য লক্ষণীয়; যেমন — সাম্প্রদায়িকতা, নারীর ক্ষমতায়ন, লৈঙ্গিক বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা, পরিবেশ বিপর্যয়, আধুনিক ইসলাম বনাম জঙ্গিবাদ, প্রান্তিক সংস্কৃতি ইত্যাদি। আশংকার কথা হলো, উন্নয়ন-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ইস্যুভিত্তিক ছবি করতে গিয়ে তারা (হয়তো) পপুলিস্ট বা জনপ্রিয় ধারার ছবি নির্মাণের কৃৎকৌশলটাই খুইয়ে ফেলেছেন।
আপনি কি অস্বীকার করতে পারবেন — প্রথম মৃত্যুর আগে গুম হয়ে যাওয়া বাংলাদেশ সিনেমার সাচ্চা প্রাণ জহির রায়হানের অবদানের কথা … যিনি একাধারে জনপ্রিয় ছবি করেছেন, অন্যদের করার রাস্তায় তুলে দিয়েছেন আবার দেশের, জাতির, অস্তিত্বের রাজনৈতিক ন্যায়ের প্রশ্নে পলিটিক্যালি কারেক্ট হতে চাওয়াদের ছাড় দিয়ে কথা বলেননি। জহির রায়হান সিনেমার কারিগরি নিরীক্ষাপ্রবণ নির্মাতা যেমন ছিলেন, তেমনি সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বতঃলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এখানে, রায়হানকে স্মরণ করা গেল বাংলাদেশ সিনেমার (অ)ব্যর্থ ঈশ্বরের কোঠায়।
বাংলাদেশের সিনেমা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠার চেষ্টায় বেশ সরল পথেই হাঁটা দিয়েছে। ফিল্মমার্কেটের চেকলিস্ট অনুযায়ী গল্প নির্বাচন, ইস্যু বাছাই, কারিগরি আয়োজন আর উপরিতলে আর্টহাউজ সিনেমার নন্দতাত্ত্বিক চোথা — ব্যস, হয়ে গেল বহুল আলোচিত, দর্শকনন্দিত ছবি। শিল্পকলা ব্যবসায়ী, সরকারি অনুদান ও বিদেশ-(উৎসব)-ফেরত সিনেমাগুলো রাজনৈতিক শুদ্ধতার চাদরে নিজেদের মুড়িয়ে রেখে সমাজের বেবাক প্রশ্নের ও দায়দায়িত্বের ভার তুলে দেয় মানুষের কাঁধে যেনবা রাষ্ট্রে সরকার, ব্যবস্থা বলে কোনো অ্যাজেন্সি নেই। আইডেন্টিটি পলিটিক্সের দোহাই দিয়ে এমনসব বাস্তবতার বয়ান ঘনায় তোলা হয় এসব ছবিতে যার সাথে ‘বাস্তব’-এর আদৌ কোনো মিল আছে কি না তা বলা মুশকিল। আর কিছু না হোক, সুরুচিসম্পন্ন গল্পে এবং আনন্দদায়কভাবে মোটা দাগে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক নির্মাণে এইসব সিনেমার জুড়ি মেলা ভার। আর, বারবার প্রতিবার এইটাই শিল্পবোদ্ধাদের কাছে কোনো-একটি সিনেমার হয়ে উঠার মাপকাঠি হিসেবে তাদের চমৎকৃত করে থাকে। তথাপি, যেসব নারী ও পুরুষ, শিশু, কিশোর পথে-প্রান্তরে গ্রামে-গঞ্জে থাকে তাদের কাছে এই মাপকাঠি বা উন্নয়ন-সংস্কৃতির কোনো মাজেজা নাই এবং এটি তাদের জীবনের সাথে কোনোভাবে সম্পর্কিত নয়। তারা মাটির প্রজার দেশে থাকেও না। তারা এমন দেশে থাকে যেখানে অবৈধ ক্ষমতা ও অপরাজনীতির যোগ না থাকলে নিজের হককথার মূল্য আদায় করা যায় না। তারা এমন দেশে থাকে যেখানে শনিবার বা রবিবার কোনো বিকেলেই এডিস মশা ছুটি করে না। ফেস্টিভ্যাল পিচিং সেশন, প্রডিওসার ল্যাব — এইসব বাহারি শব্দের আড়ালে চাপা পড়ে যায় যে, এইখানে জুতার মাপে পা কাটা হয়, পায়ের মাপে জুতা বানানো হয় না। অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, অগণন ভালো সিনেমার দেশে সৎ বা সত্যের মতন সিনেমার অভাব আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে পদ্মার বালুচরের ন্যায়। ক্ষতি কী! ফিল্মমেকার নামটা তো জারি রাখা যাচ্ছে, সিনেম্যাটিক টেলিভিজুয়াল দিয়ে কারিগরি মুনশিয়ানা তো তুলে ধরা যাচ্ছে বিজ্ঞাপন বিরতির ফাঁকফোকরে।
প্রকাশ থাকুক, তত্ত্ব বা টপিকের বাজারে ঝুঁকিপুর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি আকর্ষণীয় প্রেক্ষাপট। তাতেও আপত্তি করার সুযোগ থাকে না যদি নির্মাতারা এইসব বিষয়কে ঘিরে নির্মিত ছবিতে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রশ্নে সৎ থাকতেন এবং মানুষের পক্ষে থেকে ছবিটা করতেন। যা বলতে গেলে গরহাজির বাংলাদেশের সিনেমার ক্ষেত্রে। ঋত্বিককুমার ঘটক প্রসঙ্গে নবারুণ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, জীবনে হারানোর কিছুই নেই পলিটিক্যাল কারেক্টনেস বা রাজনৈতিক শৃঙ্খল ছাড়া। আর বাকিটা তো এখন, এইচডি ছবির মতোই ঝলমল করছে — শিল্পের মৃত্যু ঘটছে পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের বেনোজলে।
প্রসঙ্গত জানা থাকুক, সিনেমা অনিবার্যভাবে একটি রাজনৈতিক সকর্মক ক্রিয়া। এখানে, নিরপেক্ষতা আদতে অসম্ভব একটি সিদ্ধান্তই শুধু নয়, পরন্তু তা নির্মাতার দুর্বলতার ইশারাই বহন করে। সর্বোপরি, সিনেমাটি আপনি কার জন্য বানাচ্ছেন? নিজের জন্য? মানুষের জন্য? নাকি শোষক নামক সিস্টেমের জন্য? আপনার সিনেমাটি হতে পারে এক টেকে ধারণ করা বা ভিনদেশি শিল্পী-কলাকুশলী দ্বারা নির্মিত, সেটি কী শুধুই সিনেমাটি বাজারজাতকরণের স্লোগ্যান নয়? একটি শিল্পমাধ্যম হিসেবে সিনেমার দায় থাকে ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সময়ের কথা বলার, সময়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে আলেয়ার ফুল কুড়ানোর নয়। উৎসবে তরী ভেড়ানোর চাইতে জরুরি নিজের মানুষের কাছে তাদের গল্প তুলে ধরা। আশেপাশে কি ঘটছে তার ফিরিস্তি তুলে না ধরে, কেন ঘটছে, কীভাবে ঘটছে — সেসব প্রশ্নকে আরও নিকট থেকে দেখার সাহস করা, ছবিতে তা তুলে ধরা। প্রশ্ন তোলা জরুরি : কেন এখনো নিজেদের চলচ্চিত্রভাষা গড়ে উঠে নাই।
কারিগরি-প্রযুক্তির অবাধ অভিগমনের এই সময়ে সালভাদর দালি যেন ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছেন আমাদের চলচ্চিত্র দেখনদারির রোয়াকে : আর বলছেন — ‘সরকারি অনুদানে সৎ শিল্প সম্ভব নয়’। তথাপি, ফেস্টিভ্যালপ্রিয় ভালো ছবি দিয়ে জীবনের কিছু সময় হয়তো কাটানো যাবে। তবে, প্রশ্নের সৃজনশীল সমাধান খুঁজতে এখনও আমাদের নিথুয়া পাথারেই যেতে হবে হয়তো বারবার! মনে রাখবেন,লগ্নিকারীরা নিজস্ব স্বার্থ ভুলে অর্থলগ্নি করে থাকেন না।
দোহাই
Abbing, H. 2002, Why are Artists Poor? : The Exceptional Economy of the Arts, Amsterdam University Press: Amsterdam.
Bourdieu, P. 1993, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, edited by Randal Johnson, Polity Press: Cambridge.
De Valck, M. and Skadi, L. 2009, ‘Film Festival Studies: An Overview of a Burgeoning Field’, Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit, St Andrews Film Studies: St. Andrews.
Hesmondhalgh, D. 2006, ‘Bourdieu, the Media and Cultural Production,’ Media, Culture & Society, vol. 28, no.3, pp.211-231.
Hyde, L. 1983, The Gift: How the Creative Spirit Transforms the World, Canongate: Edinburgh, New York, Melbourne.
Iordanova, D (ed.). 2013, Introduction to The Film Festival Reader, St Andrews Film Studies: St. Andrews.
*লেখক : চলচ্চিত্রনির্মাতা, সংস্কৃতিবীক্ষক ও কলাসমালোচক। ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনিতে ফিল্মস্টাডিজে পিএইচডি করছেন।
… …
- ফিল্মের মধ্যে কবিতা || ইমরান ফিরদাউস - October 17, 2025
- জহির রায়হান : গুমনাম আত্মার সতীর্থ / কথোপকথনগদ্য || বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও ইমরান ফিরদাউস - July 15, 2025
- পলিটিক্স অফ বেঙ্গল : দৃশ্যবাস্তবতার রাজনীতিতে কিছু গরহাজির আত্মা || অরিজিন্যাল : জেমস লিহি / অনুভাষ্য ও অনুবাদ : ইমরান ফিরদাউস - November 22, 2024

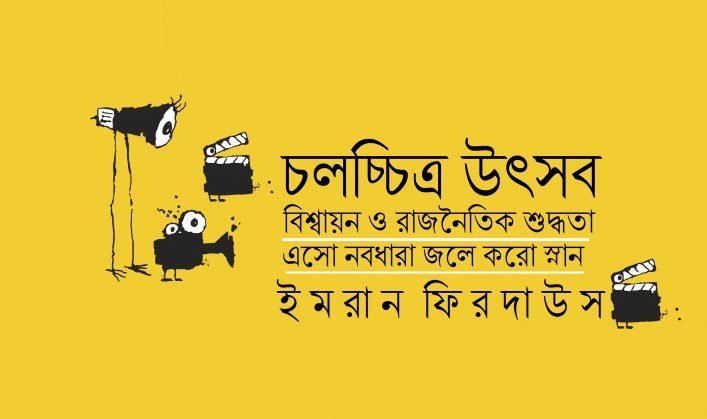
COMMENTS