গ্রামের ছোট নদীর উপরের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁশের সাঁকো পার হচ্ছে এক বালক। বিপরীত-দিক-থেকে-আসা এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন। ছেলেটি মাঝপথে এসে আর পার হতে পারছিল না। দীর্ঘক্ষণের অপেক্ষায় বিরক্ত হয়ে একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন—
ভদ্রলোক : এই খোকা তোমার বাড়ি কোথায়?
খোকা : বান্দর তোর বাপে।
ভদ্রলোক : কী পাজি রে বাবা! এই তুমি এমন গালমন্দ করছ কেন? তোমার বাবার নাম কী?
খোকা : আমার বাড়ি ঊনশিয়া।
ভদ্রলোক : ও! তুমি ঊনশিয়ার বান্দর?
খোকা : জানতাম আপনি এমন বলবেন। এই জন্যে আমি আগেই উত্তর দিয়েছি।
উল্লেখ্য সুকান্ত ভট্টাচার্যের আদি পৈতৃক বাড়ি ঊনশিয়া গ্রামে। সেই গ্রাম একদা প্রচুর বানরের নির্ভয় বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। সেখানকার দুষ্ট ছেলেদের তাই এক-কথায় সংজ্ঞায়িত করা হতো ‘ঊনশিয়ার বান্দর’ হিসেবে। নামের এমন মাহাত্ম্য আরও রয়েছে কতশত!
নেত্রকোণার নামকাহন নিয়ে অনেক কথা হলেও ‘নেত্রকোণা’-র নামকরণের কাহিনি ‘আলোর নিচের অন্ধকার’-এর মতো আড়ালেই রয়ে গেল। তাই ‘নেত্রকোণা’-র নামকরণ এবং তা নিয়ে বিরাজমান বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে, এই নামকরণের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। উল্লেখ্য তৎকালীন পূর্ব-ময়মনসিংহ প্রধানত সুসঙ্গ, নাসিরুজিয়াল, মৈমনসিংহ, সিংধা ও খালিয়াজুরী পরগণায় বিভক্ত ছিল। বর্তমান নেত্রকোণা পৌরসভা এলাকার নাম ছিল কালীগঞ্জ এবং এই কালিগঞ্জ ছিল মৈমনসিংহ পরগণার অধিভুক্ত।
ভূতত্ত্ব অনুসারে প্লাইস্টোসিনকালে (২.৫৮-০.০১২ মিলিয়ন বছর পূর্বে) সমুদ্রতলদেশের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে এতদাঞ্চলের টেকটোনিক প্লেট ফেটে গিয়ে একটি-অপরটির ওপরে উঠে পড়ে। ফলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মোহনায় সৃষ্ট বদ্বীপসমূহ উত্থিত হয়ে বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ভূমি এবং ময়নামতি সোপান বা উচ্চভূমির সৃষ্টি হয়। নিচে-থাকা প্লেট এবং উঁচু প্লেটের ক্রমাবনত দূরবর্তী অংশ নিচু থেকে যায়। ভূতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, এই সোপান-এলাকা এর সংলগ্ন প্লাবনভূমির তুলনায় প্রায় ১০ মিটার উঁচু এলাকায় পরিণত হয়। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আসামের শিলং পার্বত্যাঞ্চলে সৃষ্ট ভূমিকম্পের ফলে মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চলের আরও উত্থান হলেও সিলেটাঞ্চলের অবনমন ঘটে। ভূ-তাত্ত্বিক এই বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই নেত্রকোণা এলাকা জলমগ্ন ও নিচু। ফলে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল দুর্গম ও নৌপথপ্রধান। এ ছাড়া জঙ্গলাকীর্ণ ও নলখাগড়া আচ্ছাদিত হওয়ায় এই এলাকার দখল বজায় রাখা তথা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা বাইরে থেকে আগত দখলদারদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। এই দুর্গমতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় জমিদারগণ প্রজাদের উপর নানারকম অত্যাচার-নির্যাতন চালাতেন। দুর্গম এই এলাকার আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুসংহত করার জন্য সেসময়ের ইংরেজ প্রশাসন বিশাল আয়তনের ময়মনসিংহ জেলাকে বিভাজিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বেশ কয়েকবার।
১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করলেও শান্তিপূর্ণভাবে কখনোই দেশ পরিচালনা করতে পারেনি। তাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম ও বড় ধরনের আঘাত আসে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা ফকির আন্দোলন বা পাগলপন্থী আন্দোলনের মাধ্যমে।এই আন্দোলনের দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাঞ্চলে পাগলপন্থী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সূচনা হয় করম শাহ ওরফে করিম শাহ-এর নেতৃত্বে। এই আন্দোলনের কোনো একপর্যায়ে তিনি তৎকালীন সুসঙ্গ পরগণার লেটিরকান্দা গ্রামে (বর্তমানে পূর্বধলা উপজেলার একটি গ্রাম) তাঁর আস্তানা স্থাপন করেন। এই পর্বের স্থায়িত্ব ছিল ১৭৬৩-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ/১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) সূত্র ধরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সূচনা হয়। পরবর্তীতে এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন, অনুষঙ্গ ও বিষয় যুক্ত হয়। প্রথমেই যুক্ত হয় হাজংদের ‘হাতিখেদা বিরোধী’ আন্দোলন (১৭৭০-১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। হাতিখেদা বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে যখন হাজং নেতা মনা সর্দারকে জমিদারের হাতির পায়ের নিচে নৃশংসভাবে পিষে মেরে ফেলা হয়। জমিদারদের আরও নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন পাওয়া যায় রেভিনিউ বোর্ডের নিকট তৎকালীন কালেক্টরের কৈফিয়তে। বহু টাকা রাজস্ব বকেয়া পড়ায় তদন্তক্রমে ১৭৯০ সালে কালেক্টর কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ‘ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারদের অত্যাচারে ময়মনসিংহ ও জাফরশাহি পরগণার ৮,০৪৯ জন বর্ধিঞ্চু প্রজার মধ্যে ১,০০৫ জন বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে। জামিদারি খাস দখলে আনলে অভয় পেয়ে প্রজাগণ তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘরে ফিরে আসে। বর্তমান সময় পর্যন্ত ৬৪০ জন ফিরে এসেছে। … তাঁরা প্রজার খাজনা আদায় করে কাগজপত্র গোপন করে পুনরায় প্রজার নিকট খাজনার দাবি করে; প্রজারা দ্বিতীয়বার খাজনা প্রদান করতে অস্বীকার করায় তাদেরকে উৎপীড়ন করে নিজেদের রক্ষা করছে’।
১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা কর আরোপের মাধ্যমে জমিদারদের অত্যাচার বৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়। আবার ব্যক্তিগত জেদ বা সামান্য মতবিরোধও প্রায়শ এই অত্যাচারে ইন্ধন জুগিয়েছে। তুচ্ছ অজুহাতে ১৭৯৮ সালে ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার যুগলকিশর রায় চৌধুরী সিংধা পরগণার বহু গ্রাম আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেন। জমিদারদের এই অত্যাচার প্রতিহত করা এবং প্রজা বিদ্রোহ দমনের লক্ষ্যে ১৮১৫ সালে ময়মনসিংহ জেলায় চৌকিদারি ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থার আওতায় ইংরেজ কর্মকর্তা ড্যাম্পিয়ার সুসঙ্গ পরগণার কংস নদের তীরবর্তী ‘নাটোরকোণা’ গ্রামে সর্বপ্রথম থানার কাজ শুরু করেন। উল্লেখ্য পাগলপন্থী আন্দোলন ইংরেজ প্রশাসনের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখান থেকে লেটিরকান্দা ও সুসঙ্গের অন্যান্য এলাকায় নৌপথে পুলিশি অভিযান পরিচালনা সহজ ছিল। এই পাগলপন্থী বিদ্রোহ দমন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বাস্তবায়নের নিমিত্ত ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রথম ইংরেজ সেনাবাহিনীর আগমন ঘটে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর তৎপরতা এবং করিম শাহের মৃত্যুর পর এই আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়।
১৮২০ সালে শেরপুরের জমিদারি বিভক্ত হয়ে যায়। বিভক্ত জমিদারির আয় বৃদ্ধি ও মামলার খরচ জোগানোর জন্য প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপানো হলে করিম শাহের সুযোগ্য উত্তরাধিকার টিপু শাহের মাধ্যমে পাগলপন্থী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। ১৮২৪ সালে বার্মা যুদ্ধ শুরু হলে এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। জমিদার কর্তৃক বিনা পারিশ্রমিকে রাস্তা নির্মাণ, সৈন্যদের জন্য রসদ সরবরাহ, নৌকার জোগান দেওয়া এবং ‘পল্টন রসদ খরচ’ নামক অতিরিক্ত করের বোঝাও চাপানো হয় প্রজাদের ওপর। জমিদারদের নিবর্তনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রজারা ধর্মগুরু টিপু শাহের দলে যোগদান করে। ফলে টিপু শাহের প্রভাব সুসঙ্গ, মৈমনসিংহ ও নাসিরূজিয়াল পরগণা এবং আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সময়ের ধারাবাহিকতায় গারো বিদ্রোহ (১৮৩৭-১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ) শুরু হলে সামগ্রিক পরিস্থিতি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে। বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ১৮৪৮ সালে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী গারো অঞ্চলে প্রবেশ করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে ইংরেজদের নিয়মিত অবস্থানকে শক্তিশালী করার আবশ্যকতা দেখা দেয়।
কোনো স্থানে সরকারি স্থাপনা বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাহিনীর অবকাঠামো নির্মাণের জন্য উক্ত স্থানের ‘কৌশলগত গুরুত্ব’ খুবই প্রণিধানযোগ্য। অর্থাৎ নাটোরকোণা থেকে নৌপথে বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা সহজ হলেও নিজেদের নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল খুবই অরক্ষিত। এ জন্য নিজেদের অবস্থান সুসংহত করা এবং জেলা সদর থেকে তত্ত্বাবধানের সুবিধার্থে সুসঙ্গ পরগণার ‘নাটোরকোণা’ থেকে পুলিশি এই স্থাপনা সদর অর্থাৎ মৈমনসিংহ পরগণার ‘কালিগঞ্জে’ স্থানান্তর করা হয়। ফলে কৌশলগত অবস্থান দৃঢ় হওয়ার পাশাপাশি মৈমনসিংহের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ এবং মগড়া ও কংস নদের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত অধিকতর সহজ হয়। কিন্তু ইংরেজদের বাস্তব অবস্থানের এই পরিবর্তন ঘটলেও কাগজপত্রে অর্থাৎ দাপ্তরিক পত্রযোগাযোগে তারা ‘নাটোরকোণা’ নামকেই ব্যবহার করত। ইংরেজদের উচ্চারণে অর্থাৎ exonymy নিয়মানুযায়ী নাটোরকোণা > নেটেরকোণা > নেতেরকোণা-তে পরিবর্তিত হয়। কালক্রমে তা বাংলায় ‘নেত্রকোণা’ এবং ইংরেজিতে ‘NETRAKONA’ হয়ে যায় এবং বিলুপ্ত হয়ে যায় কালিগঞ্জের নাম। গারো বিদ্রোহীদের দমন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য ইংরেজরা ১৮৮০ সালে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে এই নেত্রকোণাকেই মহকুমায় রূপান্তরের ঘোষণা দেয়।
‘নেত্রকোণা’-র নামকরণ হয়ে গেলেও এখানে বাংলা বর্ণমালার ‘ণ’ ও ‘ন’-এর ব্যবহার নিয়ে শুরু হয় নতুন বিতর্ক। মানবজীবনটাই একটা বিতর্কের খনি। ‘জন্মই আজন্ম পাপ নাকি পৃথিবীর বুকে পদচিহ্ন রেখে যাওয়ার সুযোগ’ তা নিয়ে রয়েছে মতভিন্নতা। নৈরাশ্যবাদীদের মতে ‘জন্মই আজন্ম পাপ’ হলেও প্রত্যয়ী মানুষদের জন্য বিশাল সুযোগ। অর্থকে কেউ দেখছেন ‘অনর্থের মূল হিসেবে’ আবার কেউ বলছেন ‘অর্থ না হলে জীবনটাই অচল’। এমনই রকমারি বিতর্ক আমাদের জীবনকে করেছে রঙিন। বিতর্ক হয় ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপট নিয়ে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন তত্ত্ব ও মতাদর্শ নিয়ে; এমনকি বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথার্থতা নিয়েও রয়েছে মধুর বিতর্ক। পরশুরামের ‘মহেশের মহাযাত্রা’ গল্পে ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে মহেশ ও হরিনাথের মতপার্থক্য খুবই উপভোগ্য। মৈত্রীশ ঘটকের বর্ণনায় ‘আজীবন ভূতে অবিশ্বাসী মহেশ মরে গিয়ে এবং নিজে ভূত হয়ে প্রমাণ পেলেন যে ভূত আছে। এখানে কিন্তু তর্কটি আরও জটিল — শুধু রুচির পার্থক্য নয়, বাস্তব (বা, এই ক্ষেত্রে পরাবাস্তব) জগৎ নিয়ে গভীর মতপার্থক্য, যার সমাধান উপযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে সম্ভব, কিন্তু সেরকম প্রমাণ অনেক সময়েই জোগাড় করা অসম্ভব’। ‘নেত্রকোণা’ নামের বানান নিয়ে নেত্রকোণার সুধীমহলে একটি অনিঃশেষ বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন এই বানানের শেষ ‘ন’ টি হবে ‘ণ’ আবার কেউ বলেন এটি হবে ‘ন’।
‘ণ’ স্কুল অব থট মনে করেন সরকারিভাবে মূর্ধণ্য/‘ণ’ ব্যবহার করে নেত্রকোণা লেখা হয়। বিতর্ক এড়াতে এবং নানা মত ও পথকে এড়ানোর জন্য সহজ এবং কাম্য হলো সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে চলা। তাই অন্যরকম লিখতে হলে সরকারি খাতায় পরিবর্তন করেই ‘নেত্রকোনা’ লেখা উচিত; না-হলে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। তা ছাড়া, ঐতিহ্য বা দীর্ঘদিনের লালিত রীতির গ্রহণযোগ্যতা ‘আইন’-এর সমমর্যাদাপূর্ণ। বলা হয়ে থাকে ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত অর্থাৎ ভাষার অক্ষরে লিখিত না-হলেও শতবর্ষ যাবৎ মানুষ তা গ্রহণ করেছে এবং মেনে চলছে। এজন্য নেত্রকোণা অঞ্চলের ভাষাগত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসা নেত্রকোণাই গ্রহণ করা উচিত। আবার ‘কোণ’ শব্দটি সংস্কৃত। এজন্য সংস্কৃত শব্দের নিয়ম অনুযায়ী কোণ+আ=‘কোণা’-তে অর্থাৎ নেত্রকোণা লিখতে মূর্ধণ্য/‘ণ’ ব্যবহার করাই শ্রেয়।
বাংলা বানান রীতি ও ব্যাকরণ নিয়ে যারা চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে হায়াৎ মামুদ একজন অন্যতম পুরোধা। তাঁর ‘বাংলা লেখার নিয়মকানুন’ গ্রন্থের ‘ণত্ব-জ্ঞানের গুণী’ অংশের ২নম্বর অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন — ‘র’ (=র, ঋ, ³, ৃ, র-ফলা) অথবা ‘ক্ষ’-এর পরে যদি ক-বর্গের ৫টি (ক খ গ ঘ ঙ), প-বর্গের ৫টি (প ফ ব ভ ম) এবং য য় হ-এই মোট ১৩টি অক্ষরের যে-কোনো ১টি বা ২টি অক্ষর আসে, তবে তার পরে মূর্ধণ্য/ণ হবে। প্রথম আলোর বাংলা বানান রীতিতেও অনুরূপ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এই রীতি অনুযায়ী ‘নেত্রকোণা’ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন আমাদের আবেগের স্থান, বাঙালিত্বের আশ্রয়। তিনি তাঁর শ্যামলী কাব্যের ‘উৎসর্গ’ লিখতে গিয়ে ‘ণ’ সহযোগে ‘নেত্রকোণা’ লিখেছেন। যেহেতু কবিগুরু এমনটি লিখেছেন, তাই আমাদেরও লিখতে হবে, এখানে কোনো যুক্তি চলবে না।
যুক্তিগুলো খুরধার। খণ্ডন করা কঠিন। তারপরও রয়েছে পাল্টা যুক্তি। বিশ্লেষণ করা যাক বাস্তবতার আলোকে; সময়ের প্রয়োজনে। কারণ শুদ্ধতা হতে হবে আগুনে পোড়ানো।
তাই ‘ন’ স্কুল অব থট মনে করে সরকারি প্রজ্ঞাপন বা দলিলে বানানটি লেখার পূর্বে এর বৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে কি না তা সাধারণ্যে প্রকাশিত নয়। বাংলাদেশ গেজেটের একস্ট্রা অর্ডিনারি সংখ্যায় গত ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৪ তারিখে প্রকাশিত নেত্রকোণাকে জেলা ঘোষণার বিজ্ঞপ্তিটি ইংরেজিতে প্রকাশিত। সেখানে বানানটি Netrokona লেখা হয়েছে। অপরদিকে, EV Levinge, CSI এর নেতৃত্বে গঠিত ছয় সদস্যের কমিটির Bengal District Administration Committee, 1913-1914 Report-এ‘নেত্রকোণা’ বানান লেখা হয়েছে ‘Netrakona’হিসেবে। অর্থাৎ ইংরেজি বানানেও ভিন্নতা রয়েছে। সরকারিভাবে অর্থাৎ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পত্র যোগাযোগে দুটি বানানই ব্যবহৃত হয়। দাপ্তরিকভাবে Netrakonaলেখা হলেও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে তৈরি করে দেওয়া দাপ্তরিক ই-মেইল হিসাবে Netrokona ব্যবহার করা হয়েছে। সরকারিভাবেই বাংলা ও ইংরেজিতে দুটি বানানই লেখা হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যথাযথ যত্নশীলতা দেখা যায় না। যদিও বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, ইংরেজিতে Netrokona লেখা হলে বাংলা বানানটি ‘নেত্রোকোণা/নেত্রোকোনা’ হিসেবে লেখা উচিত। তাই বলা যায় এটি সংবিধান বা আইনের অলঙ্ঘনীয় কোনো বিষয় নয়। যদি প্রমাণিত হয় এটি ভুল কিংবা ‘এন্ডোনিমি’ অনুযায়ী প্রচলিত সামাজিক উচ্চারণ রীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, তাহলে তা পরিবর্তন করা যেতেই পারে। এমন সাম্প্রতিক নজিরও রয়েছে অনেক। যেমনটি হয়েছে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর ও বগুড়া জেলার নামের ইংরেজি বানান পরিবর্তনে। আবার দু শ বছর ধরে ব্যবহৃত ‘ঢাকা’ নামের ইংরেজি বানান Daccaপরিবর্তন করে স্বৈরশাসকের চাপিয়ে দেওয়া Dhakaব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে সর্বমহলে। সেভাবে নেত্রকোণার সুধীমহলের সম্মিলিত দাবিতে সরকারি প্রজ্ঞাপন পরিবর্তন হতেই পারে।
আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ থেকে উৎপত্তির দোহাই দিয়ে যারা মূর্ধন্য ‘ণ’ ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন তাদের বিষয়েও আপত্তি রয়েছে অনেক বিশেষজ্ঞের। তাঁদের মতে সংস্কৃত শব্দ ‘কর্ণ’ থেকে জাত ‘কোন’ শব্দটি কোনোভাবেই ‘কোণ’ লেখা যায় না। সংস্কৃত থেকে ব্যুৎপন্ন পরবর্তী স্তরের শব্দ আর সংস্কৃত থাকে না। হয় তা অর্ধতৎসম না হয় তদ্ভব হবে। তা ছাড়া, কোণ+আ=কোনা একটি খাঁটি তদ্ভব শব্দ।
‘বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান’ ও ‘বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান’-এ ‘কোনা’ শব্দটি দন্ত্য-‘ন’ দিয়েই লিখিত হয়েছে।সুতরাং যে শব্দটি সংস্কৃত শব্দই নয়, তার ব্যাপারে সংস্কৃত নিয়মের প্রসঙ্গ টেনে আনা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। ‘কোন’ শব্দটি গণিতের জ্যামিতি অংশের কোণ/সমকোণ, শীর্ষকোণ প্রভৃতি প্রচলিত বানানে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হওয়ায় এই বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। তাই ব্যাকরণগতভাবে (নেত্র+কোণ+আ)=নেত্রকোণা লেখা কোনোভাবেই ভাষাবিজ্ঞান সম্মত নয় বলেই তাঁদের দাবি। ঐতিহাসিক ব্যুৎপত্তির বিষয়টিও এখানে বিবেচনাযোগ্য। বর্তমান নেত্রকোণা শহরের পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম ‘নাটোরকোনা’ থেকে ‘নেত্রকোণা’ নামটি উদ্ভূত। ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজি বর্ণে লিখিত NATORKONA থেকে বাংলা উচ্চারণে ‘নেতরকোনা’ হয়েছে। ‘নেতর’ শব্দটি ‘নেত্র’-এর প্রভাবে বা সাদৃশ্যে ‘নেত্র’ হয়ে নেত্র+কোনা=নেত্রকোনায় রূপান্তর লাভ করেছে। অধিকন্তু অর্থবিহীন ইংরেজি উচ্চারণ NATOR/নেতর-এর পরিবর্তে ‘চোখের কোনা’র মতো চমৎকার অর্থবিশিষ্ট (নেত্র+কোণ+আ)= ‘নেত্রকোনা’ সাধারণ মানুষের মধ্যে আকর্ষণ তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবে নেত্রকোনা শব্দে সংস্কৃত নয়, জমিদারি আমলের ইংরেজি বানান (NATORKONA) এবং তার উচ্চারণের প্রভাবই প্রবল।
অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ‘নেত্রকোণা’ ব্যবহার করেছেন বলেই ব্যাকরণের রীতি পরিবর্তিত হয়ে যায় না। ‘হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না’ প্রবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে জমিদার বংশীয় কবিগুরু অসতর্কতাবশত কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবেই লিখিত প্রমাদ রেখে দিতে পারেন; কিন্তু বাকি সবাই সে ভুল অনুসরণ করেই যাবে এমনটি কোনোভাবেই কাম্য নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কবিগুরুর ‘সঞ্চয়িতা’ কাব্যের শিরোনাম অর্থাৎ ‘সঞ্চয়িতা’র গঠনগত শুদ্ধতা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। শুদ্ধতার পক্ষে আমাদের সুদৃঢ় অবস্থান ।কারণ আমরা রবীন্দ্রনাথের মনীষার চর্চা করি, তাঁর বিচ্যুতির নয়। আইনের চোখ অন্ধ; আবেগ এখানে অগ্রহণীয়।
আবার সামাজিক ঐতিহ্যের বিষয়টিও অপরিবর্তনশীল বা স্থায়ী কোনো বিষয় নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্য বা সামাজিকতা পরিবর্তনশীল। এটি শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনীয়। কোনো কোনো ঐতিহ্য কখনো কখনো প্রথমে সংস্কার এবং পরবর্তীতে কুসংস্কারে পরিণত হয়। সুতরাং ‘নেত্রকোণা’ শব্দের বানানকে সংস্কার করে ‘নেত্রকোনা’ ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।
উভয় মতবাদের পক্ষেই জোরালো যুক্তি রয়েছে। তবে, পরিবর্তন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া; যদিও স্বভাবগতভাবে মানুষ পরিবর্তনবিরোধী। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবধারিত পরিবর্তনগুলো ঘটে বলেই ‘বিবর্তনবাদ’ তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এই তত্ত্ব এতটাই শক্তিশালী যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
এখন দেখা যাক ‘ণ’ ও ‘ন’ সম্পর্কে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলা একাডেমির বক্তব্য কী। বাংলা অ্যাকাডেমি ‘বাঙলা উচ্চারণ অভিধান’-এ অনুসৃত উচ্চারণ নীতিতে ণ-এর উচ্চারণ সম্পর্কে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হলো, ‘বাংলা বর্ণমালার আর-একটা বিভীষিকা আছে, মূর্ধন্য এবং দন্ত্য ন’-এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। ‘মূর্ধন্য ণ’-এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই’। আর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ‘মূর্ধন্য ণ’-এর ধ্বনি এখন বাঙ্গালাতে নাই। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ দন্ত্য-‘ন’-এর উচ্চারণ হইতে অভিন্ন’। মুহম্মদ আবদুল হাইও মন্তব্য করেছেন, ‘ধ্বনিগত দিক থেকে ‘ঞ’ এবং ‘ণ’ কে আমরাই সহজেই অপসারিত করতে পারি’। ফলে বাঙলা উচ্চরণ অভিধানে মূর্ধন্য ণ-এর উচ্চারণ নির্দেশের জন্যে সর্বত্র দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সুস্পষ্ট মন্তব্য: “…ট-বর্গীয় ধ্বনির পূর্বে মূর্ধন্য ‘ণ’ ব্যবহার করার কোনো ধ্বনিগত সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ অনুরূপ ক্ষেত্রে আমরা যে প্রতীকই ব্যবহার করি না কেন পরবর্তী ধ্বনির অনুষঙ্গগত (homorganic) উচ্চরণই করবো”। অর্থাৎ ‘ণ’-এর অস্তিত্ব এখানে বিপন্ন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘একটি আষাঢ়ে গল্প’ আমাদের একটি সমাধানের পথ বাতলে দিতে পারে। … দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের মধ্যে নির্জন একটি দ্বীপ। সেখানে উচ্চবর্গীয় সাহেব, বিবি, টেক্কা যেমন আছে তেমনি নিম্নবর্গীয় দুরি-তিরি ও নহলা-দহলাও আছে। তাদের প্রত্যেকের সামাজিক মর্যাদা, দায়িত্ব ও অনুসরণীয় রীতি-নীতি বহু পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে। সেখানে সবাই চাবি দেওয়া নিষ্প্রাণ রোবটের মতো নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। সমগ্র দ্বীপজুড়ে চরম শান্তি এবং অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খলা বিরাজমান। হঠাৎ একদিন সামুদ্রিক ঝড়ে একটি সওদাগরি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে সেই রাজ্যে কতিপয় আগন্তুক ভেসে আসে। স্বাভাবিকভাবেই তারা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিল। অথচ তাদের খাবার, সেবা-শুশ্রূষা না দিয়ে সেখানের সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের জাত-পাত নির্ধারণে- তারা কোন জাতের, তাদের কার কী গোত্র, তাদের সঙ্গে আচরণের প্রটোকল কী হবে, তাদের সঙ্গে কে মিশবে, কাদের সঙ্গে আহার করবে, ঘরে ঘুমাবে নাকি গাছতলায়- দাড়িয়ে ঘুমাবে নাকি শুয়ে ইত্যাদি নির্ধারণ নিয়ে রাজ্যময় এক হৈ হৈ ব্যাপার। দ্বীপ রাজ্যটি এমন বিষম সমস্যার মুখোমুখি আর কখনও হয়নি। ওদিকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে আগন্তুকদের ত্রাহি অবস্থা। অবশেষে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সকল সৌজন্যতা বিসর্জন দিয়ে তারা তাদের সামনে উপস্থাপিত খাবার খেতে শুরু করে দিল এবং তাদের ইচ্ছেমতো চলতে শুরু করল। নিমেষেই সকল সমস্যার সমাধান!
সমাজবিজ্ঞানের একটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত তত্ত্ব হলো ‘Theory of Popular Voting Choices’। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দুটির বেশি বিকল্প থাকলে‘কনডোরসেট প্যারাডক্স’ দেখা দিতে পারে। তবে, মাত্র দুটি বিকল্পের ক্ষেত্রে সাধারণ ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী চিহ্নিত করা খুবই সহজ। কিন্তু ‘নেত্রকোণা’ বানানের এই সমস্যা একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক। সাধারণ মানুষের মতামত এখানে অগুরুত্বপূর্ণ হলেও আবেগ নয়। এখানে প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের যুক্তির লড়াই। ভুলটাকে শুদ্ধ করার কিংবা ঐকমত্যে পৌঁছানোর জন্য নেত্রকোণার সচেতনমহলকেই দায়িত্ব নিতে হবে। প্রসঙ্গত একালের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো Choose The Best Answer পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে অনেকগুলো কাছাকাছি শুদ্ধ বিকল্পের মধ্য থেকে অধিকতর শুদ্ধটাকে বেছে নিতে হয়। আলোচিত দুটি মতামতের পক্ষেই শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। এজন্য যদি বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্তে বা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হন, তবে সাধারণ মানুষকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে তাদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর। উল্লেখ্য পরিবর্তন বা বিপ্লব হয় দুই ভাবে- উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এবং অংশীজনের আন্তরিক উপলব্ধি থেকে উৎসারিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে। দ্বিতীয় ধরনের পরিবর্তন হয় অধিকতর টেকসই। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা বিপ্লবের দ্বিতীয় ধারার প্রতিফলন ঘটবে এবং এর স্থায়িত্ব বেশি হবে এবং চিরতরে অবসান ঘটবে এই বিতর্কের।
নেত্রকোণার নামকাহন (তৃতীয় পর্ব)
- নেত্রকোণার নামকাহন (পঞ্চম পর্ব) / হাওরাঞ্চলের পানি এবং গীতল জীবন || মঈনউল ইসলাম - August 30, 2021
- নেত্রকোণার নামকাহন (চতুর্থ পর্ব) || মঈনউল ইসলাম - January 9, 2021
- নেত্রকোণার নামকাহন (তৃতীয় পর্ব) || মঈনউল ইসলাম - October 9, 2020

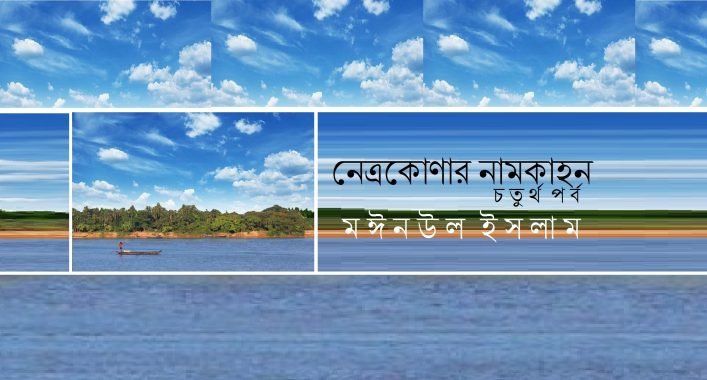
COMMENTS