অতিমারি প্রকট হওয়ার দিনকালে মানবগ্রহের অন্য অনেক শহরের মতো আমাদের শহরটিও প্রায় অকর্মণ্য হতে বসেছিল। করোনামারির ঝাপটা সামলে শহর তার অতিচেনা গতানুগতিক স্রোতে ফেরত যাচ্ছে মনে হলেও লয়-তাল-ছন্দের ব্যাঘাত কিন্তু নগরবাসী ঠিক টের পাচ্ছেন। দুইহাজার বাইশের প্রলয়ঙ্করী বন্যা একে আরো নগ্ন করে দিয়েছে। এতটাই নগ্ন যে, বিরোধী দল থেকে ভোটে দাঁড়িয়ে জয়ী বা সদ্য ফিনিশ ভোটরঙ্গ থেকে দলের নির্দেশে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য মেয়র সায়েবের মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে টাইপের ফাটাকেষ্টসুলভ উত্তাপটাও ম্রিয়মান। অন্যদিকে সরকার বাহাদুরের আধুনিক শহর গড়ে তোলার মারহাবাতুষ্ট অঙ্গীকার খুব একটা কাজে দিচ্ছে না। কেন দিচ্ছে না সে-আলোচনায় গমনের সুযোগ এখানে নেই। ওদিকপানে ধাওয়া করলে রাজনীতির চোরাবালিতে খাবি খাওয়ার সম্ভাবনা আটকানো মুশকিল হবে। রচনাটির মূল উদ্দেশ্য সেটা নয়, কাজেই ওদিকে ছুটোছুটি না করা সমীচীন মনে হচ্ছে। যে-কথাগুলো বলব বলে বসেছি সেখানে বরং থিতু থাকি আপাতত।
মধ্যযুগের ইতিহাসে লেখে, বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা দেশ থেকে দেশে মুসাফির হয়ে ঘুরে বেড়ানোর এক পর্যায়ে মোদের এই শহরে প্রবেশ করেছিলেন। বাবা হযরত শাহজালাল মুজাররাদ ইয়ামনীর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন তখন। দুজনের এই সাক্ষাতের বিবরণ বতুতার ভ্রমণবৃত্তান্তে দলিল হয়ে আছে। চীনদেশের কোনো এক রাজন্যের কাছে শাহজালালের হয়ে উপঢৌকন পৌঁছানোর ওয়াদা রক্ষা করেছিলেন তিনি। সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের মাগরেব অর্থাৎ একালের মরক্কো থেকে দুনিয়া দেখতে বের হওয়া পরিব্রাজকের সঙ্গে শাহজালাল বাবার দেখাসাক্ষাৎ কোন ফেরে ঘটেছিল তার ব্যাপারে ইতিহাসকার ভালো বলতে পারবেন, তবে দুজনের সাক্ষাৎ সুপ্রাচীন কাল থেকে বিচিত্র পরিচয়ে বিবর্তিত শহরটির গুরুত্ব টের পেতে বেশ সাহায্য করে।
অন্যদিকে ইংরেজ প্রশাসক রবার্ট লিন্ডসে বিরচিত আত্মচরিতের পৃষ্ঠা উলটালে তুলনামূলক নিটকবর্তী এক সময়ে শহরটি কেমন ছিল সেই বিষয়ে একটা ধারণা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে ডেপুটি কালেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত লিন্ডসে একুনে বারো বৎসর এখানে ঘরবাড়ি তুলে বসবাস করেছেন। অফুরন্ত বনজ সম্পদ, হাতির দাঁতের সঙ্গে চুনাপাথরের বেশুমার কারবার, যেটা গোটা আসাম অঞ্চল জুড়ে রমরম করে চলত, লিন্ডসের বিবরণে তার আভাস পাওয়া যায়। ইংরেজ রাজের হয়ে কামলা খাটতে এলেও ফাঁকতালে নিজের আখের গোছানোর মওকা খুঁজে নিতে সায়েবের তর সয়নি।
কোম্পানি আমলে সিলেট শাসন করতে আসা দুঁদে সায়েবটি লোক সুবিধের ছিলেন না। রাজস্ব আদায়ে নির্মম ছিলেন শোনা যায়। শাহজালালের মাজার সংলগ্ন এলাকায় যারা বসবাস করতেন তাদের কর নাকি তিনি মওকুব করে দিয়েছিলেন। কর মওকুবের ঘটনা কি আত্মবিবরণীতে ছিল? এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সায়েবের কিতাবখানা অবশ্য দুর্লভ বস্তু নয়। ইংরেজি ও বাংলা ভাষান্তর পাঠকের জন্য অনেকদিন থেকে সুলভ রয়েছে। সিলেটে আমার বারো বছর নামে আব্দুল হামিদ মানিক এর তরজমা করেছিলেন একসময়। মানিকের তরজমাটি অনেকে তখন সাগ্রহে পাঠ করেছেন। ব্রিটিশভারতে বঙ্গদর্শন শিরোনামে করা বিলেতপ্রবাসী লেখক ফেরদৌস টিপুর সাম্প্রতিক তরজমাটিও সুখপাঠ্য। বিলেতে থাকার সুবাদে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার ব্যবহারের মওকা টিপুর ভাষান্তরকে সমৃদ্ধ করেছে। নতুন কিছু তথ্যও যুক্ত হয়েছে সেখানে। সুতরাং আগ্রহীজনের সন্দেহ মিটিয়ে নিতে বাধা নেই।
সাপ্তাহিক বিচিত্রার কোনো এক ঈদসংখ্যায় লিন্ডসে সায়েবের কাজকারবার নিয়ে ইতিহাসকার মুনতাসীর মামুন বড়োসড়ো গদ্য লিখেছিলেন। গদ্যটি মুনতাসীরের বর্ণনাগুণে মন কেড়েছিল বেশ। গদ্যে সন্নিবেশিত তথ্যের উৎস কোথা থেকে কীভাবে চয়ন ও যাচাই করেছেন সেটা এখন আর স্মরণে নেই। সে যা-ই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে, সেকালের ইংরেজ সায়েবসুবোর পথ ধরে রবার্ট লিন্ডসেও একদিন এই শহরে পা রেখেছিলেন। ওই সুবাদে নিজের আখের গুছিয়ে নিতে ভুল হয়নি তাঁর। সওদাপাতি করে টাকা সাপটেছিলেন ব্যাপক। হাতি চালানের কারবার থেকে আরম্ভ করে চুনাপাথর, লোহা-কাঠ এমনকি জাহাজ তৈরির ব্যবসা বাদ যায়নি সেখানে। নিজের পকেট ভারী করার পাশাপাশি ইংরেজ বাহাদুরের রাজকোষ তাতে ফুলেফেঁপে উঠলেও লিন্ডসের আমলে প্রজাগণের ভাগ্যে লবডঙ্কা ছাড়া কিছু জোটেনি। কোম্পানির স্বার্থ আর নিজ ভাগ্যের চাকা ঘোরানো একমাত্র মামলা হয়ে উঠেছিল সেখানে।
ইতিহাস তথ্য দিচ্ছে, তাঁর আমলে ভয়ানক বন্যার কবলে গোটা তল্লাট জলমগ্ন হয়ে পড়ে। বানভাসী প্রজাকে সাহস ও ভরসা দানের কাজে স্থানীয়রা সায়েবকে হাত লাগাতে দেখেনি। ঝরনারপারের সৈয়দ পরিবার অত্যাচারী প্রশাসকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন। ওটা দমন করতে লিন্ডসকে বেগ পেতে হয়েছিল। শহরের শাহী ঈদগাহ ময়দান ও আশপাশ জুড়ে চলা সংঘর্ষে সৈয়দরা পরাভূত হলেও বিদ্রোহটি পলাশীর প্রান্তরকে আরেকবার স্মরণে রাখতে মনকে মজবুর করে।
লিন্ডসের আত্মকাহন প্রাচীন ভূঅঞ্চলটিকে খুবসুরত হিসেবে চিহ্নিত করলেও স্থানীয় লোকজনের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব অনুকূল ছিল না। ইংরেজদের পরিভাষায় নেটিভ নামে ঢেরাকাটা জনগোষ্ঠীর জীবনাচারকে দরদি-সংবেদী চোখ দিয়ে দেখার দায় তাঁকে উতলা করেনি। মুঘল আমলে ভারতবর্ষে আসা ফরাসি পরিব্রাজক ও চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের মধ্যে যার প্রাচুর্য চোখে পড়ে। বার্নিয়ারের মধ্যে গুণটির আধিক্য এ-কারণে ছিল যে, টাকাপয়সা হাতানোর মতলবে ভদ্রলোক ভারতবর্ষে প্রবেশ করেননি। ভাগ্যবিড়ম্বিত মুঘল সম্রাট দারা শিকোহর সঙ্গে জুড়ে থাকা ফরাসির সফরনামা কেবল মুঘল রাজাদের কাহিনিবর্ণনে নিজেকে নিঃশেষ করেনি, সংবেদী চোখ দিয়ে প্রজাকুলের আটপৌরে জীবনকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে, ভূবর্ষটি অঢেল সম্পদ ও জীবনাচারের বৈভব দিয়ে বোনা মনোরম ইন্দ্রজাল। এখানে প্রবেশ করার হাজারটা ছিদ্র থাকলেও বের হওয়ার ছিদ্র একটাও নেই। রবার্ট লিন্ডসের আত্মচরিত ওসবের ধার ধারেনি। দেশিভাই রবার্ট ক্লাইভকে গুরু মেনে ভারতবর্ষে প্রবেশের হাজার ছিদ্রকে তিনি দোহন করার মোক্ষম উপায় ঠাউরে নিয়েছিলেন।
বিনয় ঘোষের বাদশাহী আমল নামে খ্যাত কিতাবটি আদতে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের সফরনামার ভাষান্তর ছিল। বিনয় সেখানে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে যথাবিহিত প্রাসঙ্গিক করেছিলেন। বার্নিয়ারের ভারতবৃত্তান্ত দুই মহারথীকে নাকি মুগ্ধ করেছিল। এর মধ্যে বিরল সেই বীক্ষণের সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন যেটি রাজা ও প্রজা পরিবেষ্টিত ভূবর্ষের চেহারা ঠার করতে সাহায্য করে। যে-মুগ্ধতা বার্নিয়ারকে অতিকায় ভূখণ্ড থেকে বের হওয়ার পথ নেই ভাবতে প্ররোচিত করে, দেশটির সুবিপুল বৈচিত্র্যে তাঁকে ঠায় বসিয়ে রাখে, পায়ের তলায় সর্ষেদানার খোঁচা টের পেয়ে তিনি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করেন, অবিকল এই মুগ্ধতা লিন্ডসে বা তাঁর মতো শত-শত ইংরেজ সায়েবকে দেশটির ব্যাপারে অন্য কিছু ভাবতে লোভী করে তুলেছিল। এর প্রতিটি রন্ধ্রকে দয়ামায়াহীন হাত দিয়ে দোহনের ভাবনায় তাঁরা অধীর ছিলেন। আল-বেরুনি, ইবনে বতুতা বা বার্নিয়ারের থেকে এখানেই তাঁরা পৃথক। রবার্ট লিন্ডসের আত্মচরিতকে এ-রকম এক ইতিহাসের দলিল হিসেবে দেখা যায় হয়তো।
আরেকজনের নাম এইবেলা না নিলেই নয়। সম্পর্কে তিনি খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের পরদাদা লাগেন। মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যক্ষের বাসভবন, যাকে থ্যাকারে টিলা নামে ডাকা হয়, তার ওপর সিনিয়র থ্যাকারে থাকবার জন্য একখানা দালান তুলেছিলেন। দালান তোলার কাহিনি ভদ্রলোকের জীবনীর ওপর ভিত্তি করে রচিত কিতাব ‘Sylhet’ Thackeray-তে দলিল হয়ে আছে। আরেক ইংরেজ কর্মচারী ফ্রান্সিস বি ব্রাডলি বার্ট এটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ব্রাডলি বিরচিত কিতাব থেকে ধারণা পাওয়া যায় সুরমা তখন কতটা নিকটবর্তী ছিল থ্যাকারে টিলার। বাঘ-গণ্ডার আর বেশুমার হাতির সঙ্গে অজগর বিস্তৃত এই টিলাবেষ্টিত অরণ্যে যথেষ্ট সুলভ ছিল তখন। এ-রকম এক পরিবেশে দালান তুলে নিজের ভাগ্য বদলের চ্যালেঞ্জ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সিনিয়র থ্যাকারে। চুনাপাথর আর হাতির বিষয়টি বাদ যায়নি সেখানেও। অরণ্য পরিবেষ্টিত শহর থেকে ধৃত হাতির পাল (গোটা ষাট ছিল বোধহয়) দূর বিহার প্রদেশের পাটনায় চালান করার ঘটনায় থ্যাকারে কীভাবে সফল হয়েছিলেন তার মনোজ্ঞ বিবরণ ব্রাডলি কিতাবে দিয়েছেন।
বুনো হাতিকে পোষ মানানোর জন্য তৈরি খেদা বা টোপ গোটা আসাম অঞ্চল জুড়ে চলেছে এই সেদিনতক। বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের মধ্যভাগে লাউয়াছড়ার গভীরে হাতি দিয়ে গাছ টানতে দেখেছি মনে পড়ে। ওই শতকের পাঁচ-ছয়ের দশকে পাহাড়বেষ্টিত ফেঞ্চুগঞ্জ, কুলাউড়া, বড়লেখায় হাতি-চিতাবাঘ-টেপিবাঘের বাড়বাড়ন্ত ছিল শোনা যায়। বাচ্চা হাতির জন্য তৈরি গর্ত আকৃতির সুড়ঙ্গ লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হতো। হাতি সবসময় দল বেঁধে চলে। এক-একটা হাতির পাল থেকে কোনো বাচ্চা হাতি খেদায় পা ফসকে পড়ে গেলে কম্মো সাবাড়। তখন তাকে পোষ মানানোর ট্রেনিং দিতে খেদায় নামতেন মাহুত। ট্রেনিং যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে মাহুতের দিন কাটত হাতিসঙ্গে। থ্যাকারের আমল একুনে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ। এখনকার বিচারে প্রায় প্রাগৈতিহাসিক সময়টায় ভূঅঞ্চলে কী পরিমাণ হাতি বিচরণ করত সে-কথা ভেবে গায়ে শিহরণ জাগে। প্রকৃতির নিজ হাতে সৃষ্ট অমূল্য এই অতিকায় সুন্দরকে ইংরেজরা দূরদেশে চালান নয়তো তার দাঁত উপরে নিতে নির্বিচারে নিধন করেছিল। আফ্রিকায় বিচরণরত হাতিদের ক্ষেত্রে যেটি অতীতে বা এখনো প্রতিদিন ঘটছে। গজদন্ত উপড়ে নিতে মরিয়া চোরাই শিকারিদের ঠেকাতে কড়া নজরদারি থাকলেও হাতির মরণ ঠেকানো যাচ্ছে না।
এ তো গেল হাতির কথা, সিনিয়র থ্যাকারের আত্মকাহনে চা-বাগানের বিবরণ ছিল কি? মনে পড়ছে না। তবে হ্যাঁ, থমাস কারসন নামে দেশ-বিদেশ করতে থাকা ভদ্রলোকের বিবরণে তার কিছুটা উঠে এসেছিল। কাছাড় থেকে সিলেট অবধি বিস্তৃত চা আবাদের সংস্কৃতির খবরাখবর নিতে সায়েব শহরে ঢুকেছিলেন। চা-বাগানের কর্মকর্তা, আজকাল যাকে অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার ডাকা হয়, ওই দায়িত্বে কামলাও খেটেছেন বছর দুই। উদ্দেশ্য ছিল চা আবাদের অলিগলি ও ব্যবসায়িক ফন্দিফিকির শিখে নেওয়া। কারসনের বিবরণ থেকে জানতে পাই আসাম জুড়ে বিস্তৃত চা-বাগানের একচ্ছত্র মালিকানা ইংরেজের হলেও মার্কিনিদের তাতে শরিকানা ছিল। এই যেমন কারসনের ওপর যে-তিনটি বাগানের একটি দেখভালের দায়িত্ব বর্তায় সেখানে তাঁর ওপরওয়ালা ছিলেন মার্কিনদেশি। বাগানী পরিভাষায় বড়োসায়েব মার্কিনিটি, কারসন লিখছেন, মোটের ওপর মদে চুর থাকতেন সারাক্ষণ। সংগত কারণে তাঁর কাছ থেকে চা চাষ ও ব্যবসার কেরামতি তিনি লবজ করতে পারেননি। শহরের প্রান্ত ঘেঁষে বিস্তৃত কেসরগুল টি-এস্টেটের অধীন লাকিছড়া নামে বাগানের কথা কারসন নিজ জবানে লিখেছেন। বাগানটির হদিস, যেটুকু ঘেঁটেছি, কোথাও পাইনি। তবে কি লাখাইছড়াকে মিন করেছেন তিনি? লাখাইছড়া তো সিলেটের নয়! তার অবস্থান শ্রীমঙ্গল। জেমস ফিনলে কোম্পানির অধীন বাগানটি বেশ সুপরিচিত এখন। লাকিছড়া যদি কারসনের তথ্য মোতাবেক কেসরগুল-র অধীনে থাকে তাহলে সেটা লাক্কাতুরা হলেও হতে পারে। সময়ের সঙ্গে নামধামের রদবদল ইতিহাসকেও ঘোলাটে করে তোলে!
বাগানকে ঘিরে সচল চা-শ্রমিকদের খুঁটিনাটি কারসনের বিবরণ থেকে বিশেষ পাওয়া যায় না। গায়েগতরে খাটা বাগানকামলাদের আহার-বিহার-দুখসুখের গল্প বলার দায় তাঁকে তাড়িত করেনি। বাগানের শিরায়-শিরায় সঞ্চারিত চা-মজুরের ঘামশ্রমকে ওপরওয়ালা যে-চোখে দেখে থাকে তিনিও সেই চোখ দিয়ে তাদেরকে নজর করেছেন। তারিফ যৎসামান্য যা করেছেন সেখানে মনিব ও গোলামের ফারাক পরিষ্কার ঠার করা যায়। কারসন লিখছেন :
Nothing can look more beautiful or more gratifying to the eye of the owner than a tract of tea, pruned level as a table and topped with new fresh young leaf-shoots, four to eight inches high, in full flush, ready for the pluckers’ nimble fingers. [দ্রষ্টব্য : Ranching, Sport and Travel by Thomas Carson, F.R.G.S; উৎস : gutenberg.org]
চায়ের কুঁড়ি ঝুড়িতে উঠানো মনোরম শিল্পই বটে! চার থেকে আট ইঞ্চি উচ্চতার কুঁড়ি দিয়ে ঝুড়ি ভর্তির কাজে যারা ঘাম ঝরায় তাদেরকে তাঁবে রাখার প্রয়োজন কারসন অল্পদিনে বুঝে গিয়েছিলেন। বেয়াড়া কিসিমের কুলি বা পাতি তোলা মজুরকে কী করে শায়েস্তা করতে হয় তার একচিলতে উল্লেখ পাচ্ছি সেখানে। বেয়াদব এক কুলি তাঁর দিকে কোদাল নিয়ে তেড়ে এলে কারসন তাকে আচ্ছামতন পিটুনি দিয়েছিলেন। আরেক বেয়াদবকে বাধ্য হয়ে এমন একখানা ঘুষি ঝাড়েন, সায়েবের পেল্লায় মুষ্ঠাঘাত হজম করতে না পেরে হতভাগা তাৎক্ষণিক পটল তুলেছিল। কারসন লোকটি ক্রীড়াপ্রেমী ছিলেন। টাফ গাই তাতে সন্দেহ নেই, তবে রোমাঞ্চিত হতে বা আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে থাকতে ভালবোসতেন। থ্রিল ও অ্যামিউজমেন্ট-র সুরটা তাঁর রচিত ভ্রমণবৃত্তান্তে বেশ পাওয়া যায়। এর ওপর ভর দিয়ে তিনি লিখেছেন :
We thought it advisable at all costs to keep the coolies in a proper state of subjection. Thus, when on a certain occasion a coolie of mine raised his kodalie (hoe) to strike me I had to give him a very severe thrashing. Another time a man appeared somewhat insolent in his talk to me and I unfortunately hit him a blow on the body, from the effects of which he died next day. Some of these people suffer from enlarged spleens and even a slight jar on that part of their anatomy may prove fatal. [দ্রষ্টব্য : Ranching, Sport and Travel by Thomas Carson, F.R.G.S; উৎস : gutenberg.org]
কারসনের বিবরণের শেষ বাক্যটি এখানে খেয়াল করা জরুরি। বেয়াদব কুলিটি কেন মুষ্ঠাঘাতে অক্কা পেল তার কারণ ভাবতে বসে প্লীহার প্রসঙ্গ তিনি টেনেছেন। এইসব কুলিকামিনের সিংহভাগ, কারসন ধারণা করছেন, লোকগুলোর প্লীহা এতদূর নাজুক ও জখমি থাকে যে সাদা সায়েবের চাবুক আর মুষ্ঠাঘাত হজম করা তাদের পক্ষে খতরনাক হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজ আমলে তারা কেমন ছিল সেটা এই একটি বাক্য থেকে পরিষ্কার বুঝে ফেলা যায়। একালেও তথৈবচ।
বাগানকামলারা ঝা চকচক উন্নয়নের দিনকালে কতটা নাজুক দিন কাটাচ্ছে সেটা বছর দুই আগে মাইনে বা তনখা নিয়ে হুলুস্থূল কাণ্ডে নগ্নভাবে ধরা পড়েছিল। পাতি তোলা কামের ঘানি টেনে যাদের জীবন কাটে তারা কারসনের আমলে জখমি ছিল, এখনো তা-ই বটে! প্রগৈতিহাসিক এক শ্রমিকশ্রেণি, যারা কিনা উদ্ধৃত্ত শ্রমের মাশুল আজতক দিয়েই চলেছে! ওটাকে থামানোর দায় কারো নেই। না বাগানমালিক না সরকার না সরকারবিরোধী নেতাকুল…, উদ্ধৃত্ত শ্রমের বিরামহীন উৎপাদকগোষ্ঠী সকলের কাছে এতটা সুদূর যে তাদেরকে অচিহ্নিত ভাবতে মন সায় দিয়ে বসে।
একজন চাশ্রমিকের কাছে পাতি তোলার চেয়ে মর্যাদাকর কাজ জগতে দুটি নেই। চাকুরির উমেদারি করার দিনকালে মৌলভীবাজারে অধমকে কয়েক বছর থাকতে হয়েছিল। শ্রীমঙ্গলের বাগানগুলোয় ঘোরা নেশায় দাঁড়িয়েছিল তখন। এমনি এক ঘোরাঘুরির মুহূর্তে কানে এসেছিল গানের কলি। এক নারী চাশ্রমিক গাইছিলেন : ‘সাঁঝে ফুটিল ঝিঙা ফুল রে / ঝিঙা ফুল নিলো জাতিকুল / মনে বড়ো আশা ছিল পাতি তোলা কাম লিবো / সায়েব মোরে দিলো কোদাল মারার কাম রে / ঝিঙা ফুল নিলো জাতিকুল।’ গানের আন্তঅর্থ সরল। ঝিঙে ফুল যখন ফোটে তখন অভিসারে যাবার সময় ঘনায়। প্রেমের রঙে রঙিন হয় মন। অভিসারে গমনের ক্ষণ ঘনিয়েছে কিন্তু তাতে বাধ সাধছে মনস্তাপ। শরমে রঙিন কামিনী এইবেলা ভাবছে,—মনের মানুষকে সে কেমন করে বলবে সায়েব তাকে কোদাল মারার কামে লাগিয়েছে! দুই আঙুলে আলগোছে চায়ের কুঁড়ি তুলে আনবে যে-হাত সেই হাতে কর্কশ কোদাল ধরিয়ে দিয়েছে সায়েব। জাতিকুলমানের আর বাকি থাকছে কী!
পাতি তোলার ফান্দে আটক চাশ্রমিকরা বোধ করি জগতের সবচেয়ে বড়ো হতভাগা। পেশা বদলের ভাবনায় যদিও-বা কাতর হয়, বাইরের অতিকায় পৃথিবীকে কী করে মোকাবিলা করবে সেই তরাসে তারা পুনরায় ফেরত যায় বেগার খাটনির দুঃসহ নির্জনতায়। চল মিনি আসাম যাব গানের কথা এইবেলা মনে আপনা থেকে ভাসে। কালী দাসগুপ্ত বিরচিত বহুশ্রুত গানটির মর্মে গাঁথা রয়েছে বাগান পত্তনের আদি ইতিহাস। ইংরেজ আমলে যে-জবরদস্তি ও প্রলোভনের ফাঁদ দক্ষিণ ভারত থেকে নেপাল অবধি বিস্তৃত এক-একটি অঞ্চল থেকে এই জনগোষ্ঠীকে রেলে করে আসামে আসতে বাধ্য করেছিল তার আভাস গানটিতে বেদনাঘন কৌতুকরসে বহমান।
চাশ্রমিকের জীবন উভয়সংকটের নামান্তর। সে না পারে বাগান ছাড়তে, না পারে বেগার খাটনির চাপ সহ্য করে বাগানে নিজের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা দিতে। মর্মবেদনটা ধরা পড়েছে গানের কথায় : সর্দার বলে কাম কাম / বাবু বইলে ধইরে আন / সাহেব বলে লিব পিঠের চাম / হে যদুরাম / ফাঁকি দিয়া পঠাইলি আসাম। যদুরাম আদিতে ইংরেজ আর এখন সেটা বাগানমালিকের পরিচয়কে অ্যানক্যাশ করে দেশ-বিদেশের সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী ব্যবসায়ী নয়তো শিল্পপতি। একেকটি চা-বাগান হচ্ছে স্বয়ং একেকটি দেশ। তার নির্জনতায় অকাতরে শহিদ হয় কুলিকামিন। দুঃখ ভুলতে ভাত পঁচানো মদ গিলে আর টিলাবাবু থেকে ম্যানেজারের কামলা খাটে ইমানদার গোলামের ন্যায়। নামে তারা চাশ্রমিক, শানমান বিচারে গোলাম বৈ অন্য কিছু নয়। কারসনের আমলে তারা বেকুব ছিল, একালেও তাই।
যা-ই হোক, কারসন তাঁর জবানীতে নাগা-কুকি-খাসিদের কথাও লিখেছেন যৎকিঞ্চিত। মন্দিরের কথা লিখেছেন। বাগানমালিক আয়োজিত বাৎসরিক মেলার বিবরণ দিয়েছেন। ঘন নিবিড় জঙ্গল, যেখানে বাঘ-চিতাবাঘ-বনশূকর থেকে কুমির-অজগর সবটাই ব্যাপক, যেখানে হাতির পিঠে সওয়ার হওয়া ছাড়া প্রবেশের পথ নেই, তার উল্লেখ পাচ্ছি সেখানে। বাঁশ, প্রজাপতি, মৌচাষের খবরাখবর করেছেন সায়েব। আরো পাচ্ছি স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে সখ্য। পোলো খেলা আর মদ্যপানের বিবরণ। এসবের বাইরে কাঁঠালের গলিভাই দুরিয়ান নামক ফলটির নামগান জপ করেছেন। দুরিয়ান বাংলাদেশে তেমন দেখা না গেলেও এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের দেশগুলোয় এর কদর ব্যাপক। শহরে রোজ সন্ধ্যায় বটেশ্বর-হরিপুর-খাদিম-জৈন্তা থেকে কিছু লোক মীরাবাজার, ধোপাদিঘিরপাড়, লালদিঘিরপাড়ে পসরা সাজিয়ে বসেন। মাঝেমধ্যে সেখানে দুরিয়ানের দেখা মিলবে। দাম বেশ চড়া। ফলটির ব্যাপারে জানতে আন্তর্জাল যথেষ্ট, সুতরাং বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। কারসন যদিও সোৎসাহে সেটা দিয়েছেন। বিদঘুটে গন্ধ সত্ত্বেও এর স্বাদকে অমৃততুল্য মনে হয়েছিল তাঁর।
সায়েবসুবোর কথা বাদ দিলে এই তল্লাটে রবিঠাকুরের আগমনকে একবার স্মরণ করা লাগে। তাঁর তখন ব্যাপক নামডাক। শেষের কবিতায় যে-শহরকে অমরত্ব দিয়ে গেলেন সেই শিলংয়ে আবকাশ যাপনে এসেছিলেন কবি। সিংহবাড়ি সহ শহরের বিশিষ্টজনের দূতিয়ালী আর পীড়াপীড়াকে না করতে পারেননি তখন। যাত্রাপথ অতীব দুর্গম জেনেও শহরটিতে একপাক ঘুরে আসার সম্মতি তাঁকে দিতে হয়েছিল। সেকালে শিলং থেকে শহরে আসার সহজ উপায় ছিল খাসিদের পিঠে চেপে পাহাড় ধরে নামতে থাকা। মানুষের পিঠে চড়ে শহরগমনে ঠাকুরকে রাজি করানো যায়নি। অগত্যা ঘুরপথে কুলাউড়া হয়ে এখানে পা রেখেছিলেন। পাদ্রী টমাস সায়েবের বাংলো বাড়িতে যাপন করেছিলেন কয়েক রজনী। সেকালের টাউন হলে বক্তিমাও দিয়েছিলেন। মণিপুরী নৃত্য মুগ্ধ করেছিল কবিকে। একে সঙ্গী করে ফিরেছিলেন শান্তিনিকেতন। যাবার সময় সুন্দরী শ্রীভূমিকে বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে নির্বাসিতা মনে হয়েছিল কবির। নির্বাসিতা ভাবার কারণ অবশ্য জটিল কিছু নয়। শহরটি বাঙালি অধ্যুষিত হলেও ছিল আসামের অন্তর্গত। বাংলাকে নিজের করে নিলেও কোথায় জানি পৃথক লাগে তাকে! যেমন পৃথক চাটগাঁ। আহার-বিহার থেকে শুরু করে মুখের বুলি ও জীবনাচারের প্রতি অঙ্গে অসমিয়া জলবায়ুর দাপট কবির তাই পড়তে অসুবিধা হয়নি। শহরের সুবিপুল সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি বিপুল সংবর্ধনায় অভিষিক্ত ঠাকুরের বুঝতে বাকি থাকেনি, মেঘালয়ের ঢাল ঘেঁষে বিস্তৃত পাহাড়ি জনপদটি স্বভাবের দিক থেকে আলাদা। বাংলাকে অঙ্গে জুড়ে নিলেও তার পৃথকত্বে সে সাক্ষাৎ সুন্দরী।
ওইভাবে থাকার কথা ছিল তার। আসামের জলবায়ুর সঙ্গে একীভূত শ্রীময়ী রূপে। ইংরেজ আমলে চালু সুরমা ভ্যালির গরিমা নিয়ে। মেঘালয় জুড়ে ছড়ানো পাহাড়সারিতে একাত্ম হয়ে, যার মনোজ্ঞ বিবরণ কবি মণীন্দ্র গুপ্ত অক্ষয় মালবেরিতে দিয়েছেন। তার জন্য এভাবে থাকাটা সহজ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেশভাগ সেখানে কোপ বসায়। হিন্দু-মুসলমানে মানচিত্র ভাগ-বাটোয়ারার পেরেশানি সামলে নিতে শহরটিকে রেফারেন্ডামের সম্মুখীন করা হয়। সিলেট গণভোট নামে খ্যাত সেই তাণ্ডব তাকে ছিন্ন করে আসাম থেকে। ইতিহাসের নাটকীয় আবর্তনের পথ ধরে শহরটি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কোনো মিলনরেখার অস্তিত্ব জীবিত নেই! উন্নয়নের ষণ্ডগতি মিলনরেখায় সক্রিয় ইতিহাসকে স্মরণ করার তাগিদ বোধ করেনি। ঘরে-ঘরে করোনামারি হানা দেওয়ার আগের বছরগুলোয় যেমন স্মরণ করেনি, অতিমারির আপদ কাটিয়ে শহর যে-পথ ধরে চলছে সেখানেও উক্ত মিলনরেখাকে পাঠ যাওয়ার জায়গা রাখা হয়নি। এই দেশে উন্নয়ন হচ্ছে এমতো বস্তু যার সঙ্গে একটি জনপদের জীবনসংস্কৃতির সংযোগ থাকে না। ফেলে আসা অতীত, চলিঞ্চু বর্তমান এবং আসন্ন ভবিষ্যতের জীবনসংস্কৃতিতে সচল সংযোগরেখাকে একবিন্দুতে মিল করে আগানোর ভাবনা মোদের ষণ্ডমার্কা উন্নয়নে কোনোকালেই গুরুত্ব পায়নি। সুতরাং শহরের হালফিল উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে তার জীবনসংস্কৃতির ছিটেফোঁটা মালুম করা সম্ভব নয়।
এ এক নয়া শহর! বাংলাদেশের রাষ্ট্রসীমায় একীভূত, যদিও তার জলবায়ুতে মেঘালয়-চেরাপুঞ্জি আর আসামের আকাশসীমায় ঘনীভূত বৈশিষ্ট্যের প্রকোপ আজো অমলিন। বাংলাদেশকে আপনার করে নিলেও নিভৃত দূরত্ব আজোবধি বিরাজ করছে সেখানে। বেঙ্গলি, আবাদি নামে দেশের বাদবাকি অঞ্চলের মানুষগুলোকে নিজের থেকে পৃথক ভাবার বাতিক সে তাই ছাড়তে পারে না। বাংলা জবানে দিবারাতি নিঃশ্বাস নিলেও শুদ্ধ বাংলা আওরানোর ক্ষণে তার মুখের বুলিতে কমলালেবুর বাস বেরিয়ে পড়ে। রবিঠাকুরের সঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রথম দেখাসাক্ষাতের সরস বিবরণে একই ব্যাপার ঘটতে দেখি। সৈয়দের মুখের বুলি থেকে ঠাকুর তাঁকে খাসা সিলেটি বলে তাৎক্ষণিক চিনে নিয়েছিলেন।
অঞ্চলটির লোকজন এ-রকমই! বাংলা জবানে জিহ্বা শান দিয়ে চলার ক্ষণে নাগরী নিয়ে তারা গর্বে ছাতি ফোলায়। দেশের বাদবাকি মানুষজন হয়তো একে আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ভাবেন। সুযোগ বুঝে ট্রোল করতেও ছাড়েন না। সিলেটি ও চাটগাঁর ভাষাকে ইউনেস্কো যতই পৃথক ভাষারীতি বলে দাগ কাটুক, দেশের বিদ্বানসমাজ ও ভাষাবিশেষজ্ঞরা সিলেটি ভাষাকে বাংলার একটি উপভাষা হিসেবে দেখতে ভালোবাসেন। তবু, সাক্ষাৎ সিলেটি কোনো লোক বোধ করি জানে, নিজের বাইরে আস্ত একটা দেশকে বেঙ্গলি বা আবাদি বলে পৃথক করাটা নিছক আঞ্চলিক সংকীর্ণতার বিষয় নয়, এর মধ্যে ইতিহাসের নির্মম সব চোরাই ফাঁদ এখনো সক্রিয় রয়েছে, যার টানে গোটা তল্লাটটি বাংলায় থেকেও বাংলায় থাকে না। ঘটনাটি রবিঠাকুর বিলক্ষণ টের পেয়েছিলেন কিন্তু একালে সেটা অনেকে ধরতে পারেন না।
…
অধমের কথার বাওগতিক অন্যদিকে খেই হারাচ্ছে মনে হয়। যে-কথাগুলো বলব বলে বকুনির সূত্রপাত সেদিকে ফেরত যাওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের ধূসর পৃষ্ঠায় খাবি-খাওয়ার স্মৃতিকাতর বদখোয়াব ছেড়ে বর্তমানে ফেরা যাক। করোনামারির আগে থেকে শুরু হওয়া উন্নয়নের জেল্লা ও তার পরবর্তী অভিঘাত নিয়ে ভণিতায় যে-কথা তুলব-তুলব করে তুলতে পারিনি, এখন তার জের ধরে বলি,—সময়ের সঙ্গে একটি শহর নিজের ডালপালা ছড়াবে এটা স্বাভাবিক। রাস্তাঘাটের সঙ্গে পয়ঃপ্রণালির সংস্কার, যেটা করোনার আগে গতি পেয়েছিল, শত বিড়ম্বনা সত্ত্বেও শহরবাসী একে ওয়েলকাম জানাতে দ্বিধা করেনি। কালের গতিতে নর্দমায় পরিণত ও জবরদখলের শিকার লতার মতো ছড়িয়ে থাকা ছড়াগুলো উদ্ধার জরুরি ছিল। নদী ও ছড়াকে পরিবেষ্টন করে ওয়াকওয়ে গড়ে তোলা আর কোনোমতে বেঁচেবর্তে থাকা দু-একটা দিঘিকে নান্দনিক করার ভাবনা লোকের মনে ধরেছিল। একচিলতে সবুজের সঙ্গে পাখির কিচিরমিচির ধরে রাখতে জানে এ-রকম দুয়েকটা ছোটবড়ো পার্কের দাবি বহু পুরাতন। যেমন সনাতন এই দাবি,—শহরের জনসমাগমের প্রধান কেন্দ্রগুলোয় সবুজায়ন ঘটুক। দেখে চোখ জুড়াবে এমন শৈল্পিক ভাস্কর্য ও স্থাপনায় ভরে উঠুক ভিড়াক্রান্ত একেকটি চত্বর। ইতিহাসে শিলীভূত কিংবা ইতিহাসের মার সহ্য করে আজো সক্রিয় যত লক্ষণ শহরটিকে আলাদা ও বিশিষ্ট করেছে সেগুলোকে যেন এভাবে মানুষ অনায়াস চিনে নিতে পারে। করোনামারির প্রাকক্ষণে শহরকে নান্দনিক দেখতে পাওয়ার উচ্চাভিলাষী খোয়াবে অনেকেই মগ্ন ছিলেন কমবেশি।
প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে, ইংরেজ আমলে গড়ে ওঠা হাসান মার্কেটকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারলে বন্দরবাজারের চেহারা সমূল পালটে যাওয়ার ভাবনা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। বহুজন কথাটি আগে তুলেছেন এবং তুলছিলেন। রিকাবীবাজারটা সড়কদ্বীপে মোড় নিক;—শহরের সংস্কৃতিকর্মীদের চাওয়াটাকে অবান্তর ভাবার সুযোগ ছিল না। রিকাবীবাজার ও আশপাশের চৌহদ্দিকে পরিবেষ্টন করে সাংস্কৃতিক চত্বর গড়ে তোলার যজ্ঞ শুরু করা যেতে পারত। সুরমা নদীকে হুমকির মধ্যে রাখা কাজিরবাজারকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াটা অন্তিম ভাবছিলেন অনেকে। বন্দরবাজারের মূল চত্বর থেকে কাজিরবাজার অবধি এলাকার সঙ্গে টেমস নদীর কোল ঘেঁষে বিস্তৃত অংশটির খানিক সাদৃশ্য বোধ করি পাওয়া যায়। শহরের প্রবেশমুখ হিসেবে গণ্য এলাকাটিকে ইচ্ছে করলে ওই আদলে সাজানো কঠিন ছিল না। বহুজনের মুখে-মুখে চাউর ইচ্ছেঘুড়িকে তখন আকসার উড়তে দেখেছি আকাশে!
কিনব্রিজটা যেমন ছিল তেমন থাকবে তবে তার সংস্কার দরকারি। সার্কিট হাউজ, আলী আমজাদের ঘড়ি, সারদা হল, সিটি কর্পোরেশেনের গাড়ি রাখার ভাগাড়ে পরিণত পৌর পাঠাগার…সারবেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা স্থাপনাগুলোর ফোকর গলে যেসব স্থাপনা নামধারী আবর্জনার স্তূপ, সেগুলোকে শৃঙ্খলায় আনার কথা সবাই বলাবলি করছিলেন। নদী দখলমুক্ত করার তোড়জোড় চলছিল দেশ জুড়ে। সুরমা নদীর দুইপাশে ছড়ানো অবৈধ দোকানপাট গুঁড়িয়ে দিতে দেখেছি তখন। মনে আশা, এবার বোধহয় হতভাগী সুরমার গতি হতে যাচ্ছে। তার তীরে বসে নিঃশ্বাস নেওয়ার আরাম পাবে মানুষ। দুদণ্ড নদীর হাওয়া গায়ে লাগানোর পরিবেশ এতদিন বাদে শহরে ফেরত আসতে চলেছে। করোনার কারণে নদীকে দখলমুক্ত করার কাজে ভাটা নেমে আসে। তারপর তাকে আর ফিরতে দেখিনি। পরিবেশ অধিদপ্তরের লোকজন কোথায় ফেরারি হলেন সে-খবর নেওয়ার তাড়া কারো ছিল না। না কোনো সাংঘাতিক তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তুলে এনেছিলেন উনাদের ফেরার হওয়ার কারণ!
করোনার অণুজীব দাপট হারিয়ে নির্জীব হয়েছে দেখে সবাই তখন হাঁফ ছাড়তে ব্যস্ত। সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। গেলেন চিরচেনা নদীতীরে। ফুচকা-বাদাম ও চটপটির তালাশে। নদীর ঘাটলা থেকে প্রস্রাবের বাস ছড়াচ্ছিল। আমিও সঙ্গী ছিলাম, তথ্যটি সঙ্গে নিয়ে,—করোনাকালে নদীর ঘাটলা নেশাখোর আর ভাসমান লোকজনের অভয়াশ্র্রমে মোড় নিয়েছিল। ঘাটলার আন্ধার কোণে, ওয়ান ফাইন মর্নিং, এক নারীর লাশ দেখতে পেয়েছিল ভাসমান হতভাগার দল। কে বা কারা তাকে ধর্ষণ ও হত্যা করার পর বস্তায় মুড়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল। নারীটি যেখানে লাশ হয়ে পড়েছিলেন সেই জায়গাটি দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছোপ-ছোপ অন্ধকারে একটা চামচিকা আমার নাক ঘেঁষে ফুড়ুৎ উড়াল দিলো বাইরে। ধর্ষিতা ও পরে নিহত এই নারী কি তবে চামচিকায় রূপান্তর লাভ করেছেন এবং যাপন করছেন গুমোট অন্ধকার? আবাল্যচেনা শহরটির মতোই যাকে হতভাগী বলে চিনে নিতে বিলম্ব হচ্ছে না!
পড়ন্ত এক বিকেলবেলার কাহিনি ছিল সেটা। ঝপ করে সন্ধ্যা নামবে এ-রকম মুহূর্ত গাঢ় হচ্ছিল নদীজলে। সুরমার ঘোলাজলের ওপর দক্ষ বায়ুসেনার মতো পাক খাচ্ছিল চিল, আর ওদিকে আবছায়া রেখায় পরিণত ইঞ্জিননৌকারা ভটভট শব্দ তুলে লোক পারাপারে নিমগ্ন ছিল। আলী আমজাদের ঘড়িঘরের চূড়ায় দুটি বয়স্য কাককে বসতে দেখছি তখন। নিরুদ্যম আবেশঘোরে অলস ডানা ঝাপটাচ্ছিল। তাদের এই ডানা ঝাপটানো মোটেও বাস্তবসম্মত ছিল না। কাক নয় বরং প্লাস্টিকে মোড়ানো একজোড়া মূর্তিমান পাখিপ্রেত ডানা ঝাপটাচ্ছিল সেখানে। পাখিপ্রেতে নিজেকে নজরবন্দি করার ক্ষণে মনে পড়ল ইংরেজ আমলে বানানো কিনব্রিজের পাটাতন একসময় কাঠের ছিল। ছেলেবেলায় তাকে সে-রকম দেখেছি বৈকি। নড়বড়ে আর ঝুঁকিপূর্ণ এক সাঁকো। তার ওপর দিয়ে রিকশাগাড়ি পারাপার করত দিনমান। সিএনজির বদলে ছিল তিন চাকার বেবিট্যাক্সি। বিদঘুটে সেই যানের জান্তব আওয়াজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রিজের ওপর দেদার পাক খেতো জালালি কৈতর। মাঝেমধ্যে নদীর জলে ভোঁস করে মাথা তুলত শুশুক। একে-একে তারা কোথায় ফেরারি হয়েছে জানি না। প্রস্রাবের কটু গন্ধ আর ঘাটলার ঘুপচিকোণে ধর্ষিতা নারীটি ছাড়া এখন সেখানে কিছু পড়ে নেই!
জালালি কৈতরকে কেবল শাহজালাল বাবার দরগায় গেলে মিলবে। তাদের উড়াউড়ি বন্য নয়। নাতিউচ্চ টিলায় বাবা চিরকালের জন্য বিরাম নিয়েছেন। সেই টিলা, যার ভিতরে বাবার শিষ্যরা তাঁর জন্য এক সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দিয়েছিল। গহীন কোটর ছিল তাঁর দিনরাতের আস্তানা। সেখানে বসে খোদার ধ্যানে লিপ্ত ও নিরাকার বাবার কাঁধে বসে থাকত আশ্চর্য জালালি কৈতর! শহরটির কী যেন নাম ছিল তখন? হরিকেল? শ্রীহট্ট? সিলহট? জালালাবাদ? অথবা অন্যকিছু? সে যেন কার অংশ ছিল? শিবপত্নী সতীর ছিন্নহস্ত শুনেছি নিরালা এ-নগরে একদিন পতিত হয়েছিল আর তখন থেকে সে শ্রীভূমি। কামরূপ কামাখ্যার সারথি। ডাকিনী-যোগিনী-কাপালিকে রহসময়ী। হতেও পারে। শ্রী চৈতন্যর ঠিকুজিকোষ্ঠীর সঙ্গে তার নাকি যোগ রয়েছে। পিতৃপুরুষের ভিটেমাটির খবর নিতে ঢাকাদক্ষিণ যাওয়ার পথে এই শহরে গোরাচাঁদ নিমাই সন্ন্যাসীর পায়ের ছাপ পড়েছিল। দূর অতীতে বিলীন ঘটনার সবটাই জাদুমন্ত্রবলে নিরুদ্দেশ হয়েছে অজানায়। যেমন নিরুদ্দেশ সুরমার জলে ভোঁস করে মাথা ওপরে ভাসিয়ে তোলা শুশুক!
…
লোকজনের ঘরে-ঘরে অতিমারি হানা দেওয়ার আগে থেকে জানা ছিল, যারা চলে গেছে তারা আর ফিরবে না। তবে হ্যাঁ, যারা আছে তাদের শ্রী ধরে রাখতে শহরটিকে যুগের নিয়ম অনুসারে সাজানো যেতে পারে। তার তোড়জোড় চলছিল বেশ। এই অঞ্চলের সন্তান কথাশিল্পী মিরজা আবদুল হাই যমনিস সংবাদ নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন। দেশের শহরগুলোয় গণশৌচাগারের শোচনীয় ঘাটতিকে আখ্যানে প্রাসঙ্গিক করেছিলেন তিনি। এখন তার দু-একটা গড়ে উঠলেও প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলো গোনায় আসবে না। গণশৌচাগারের সঙ্গে নান্দনিক স্থাপনা সময়ের দাবি ছিল। তার পাশাপাশি রাত্তিরে নিয়ন আলোর বন্যায় আলোকিত সড়ক দেখতে পারার খায়েশ লোকজনের মনে যদি উঁকি দিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে একে আকাশকুসুম কল্পনা ভাবতে যাব কোন দুখে! সুনামগঞ্জে রওয়ানা করার প্রধান সড়ক ও সংলগ্ন জনপদ, সারা দেশ থেকে শহরে প্রবেশ অথবা বেরিয়ে যাওয়ার মূল কেন্দ্র কদমতলির চারপাশকে দিলবাহার করে তুলতে পারলে আরামটা এখানকার লোকজনই অধিক পেতেন। ময়লা ফেলা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের আধুনিক তরিকা রপ্ত করা গেলে বিষে নীল সোনারগাঁ-লালমাটিয়ায় ময়লা পোড়ানোর অসহনীয় অত্যাচার থেকে নগরবাসীর রেহাই মিলত। করোনাদিনের আগে শহরকে সময়উপযোগী কেতায় সাজানোর ছকে এসব গোনায় ধরা হয়েছিল বৈকি।
সোনারাগাঁ ও লালমাটিয়া নিয়ে দু-কথা সময় থাকতে বলে ফেলা ভালো। শহরতলির অংশ ভূঅঞ্চলকে উপকণ্ঠে রূপদানের লোভ দেখিয়ে লোকের পকেট থেকে টাকাপয়সা হাতিয়ে নেওয়ার মওকা আপাত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ভেস্তে গিয়েছিল। ভেস্তে যাওয়ার লাভজনক দিক ছিল শরৎকালটা সেখানে বেশ টের পাওয়া যেত। কাশফুলে ছেয়ে যেত সীমারেখায় দাগানো এক-একটি বিক্রিত নতুবা অবিক্রিত প্লট আকারে নিথর পড়ে থাকা ভূঅঞ্চল। আশায় গুঁড়ে বালি। ময়লা পোড়ানোর দাপটে কাশফুল সেখানে ম্রিয়মান ও নিরুদ্দেশ। কার বাপের সাধ্যি ওই ভূঅঞ্চলে ঢুকে ক্যাটকিন্স ওরফে কাশফুলের চোখ-জোড়ানো বাহার দেখবে! তারা হাকালুকি হাওরের অংশ ছিল বা কিয়ৎপরিমাণে আছে ভেবে সুখ নেওয়ার উপায় অবশিষ্ট নেই। যেমন নেই এ-কথা ভেবে স্মৃতিকাতর হওয়া,—উপশহর এলাকাটি এভাবে একদিন ডুবরির হাওর নামে বিদিত এক বিলের অধীন ছিল। পায়ে শেকলবাঁধা জেলখাটা দাগী আসামিরা রোজকামলার অংশ হিসেবে বিলের শুকনো ভূমিরেখায় মোষের পাল চরিয়ে বেড়াত, আর তাদের পাহারায় থাকত কাঁধে রাইফেল ঝুলানো পুলিশ।
আহা ডুবুরির হাওর! উতরোল বর্ষায় পানির ঢল ও গহনা নৌকায় ভরভরন্ত হয়ে উঠতে দেখেছি তাকে। দাগী আসামিদের হাত উপচে উঠত ভাট ও শালুকফুলের বাহার। তার ভাগ পেতাম মোরা নাদান ছেলেপিলের দল। শীতে বিলের একাংশে পানি নেমে গেলে শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা বসত। চড়কে টাঙানো বড়শি পিঠে গেঁথে বনবন করে পাক খাচ্ছে দক্ষ বাজিকর! কী করে সম্ভব সেটা ভেবে অবাক যেত মন। মেলা শেষ হলে ফুটবল, ক্রিকেট আর কাবাডির মজমা চলত অবিরাম। ডুবরির হাওর নামখানা আজো টিকে আছে কিন্তু সেখানে কোনো হাওর নেই। ওখানে এখন মস্ত সড়ক। সবজিবাজার। পেল্লায় দালানকোঠা। গা ঘিনঘিন নর্দমা দিয়ে বইছে কালো জলের স্রোত। তার ওপরে সেতু। সেতুর ওপর সবেগে ধাইছে মোটরযান আর ক্রমশ ছোট থেকে ছোট হয়ে আসা পিঁপড়েসারি মানবপ্রজাতি।
করোনা প্রকট হওয়ার আগের দিনগুলোয় অতিচেনা চিত্রকল্পটি বদলে যেতে শুরু করবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু না, কিসসু বদলায়নি। দুইহাজার বাইশের ডাকাতি বানে ডুবরির হাওরকে গিলে বাড়তে থাকা উপশহর ডুবতে বসেছিল। দুইহাজার চার সালের বন্যায় আর্ধেকটা ডুবেছিল, বাইশের বান প্রবল রোষে এলাকাটিকে ডুবিয়ে রাখল মাসাধিক। এ কী তবে প্রকৃতির প্রতিশোধ? ডুবরির হাওরের গহিন পাতালে ঘুমন্ত দেওলা কি জেগে উঠেছে? নিজের থৈ থৈ সায়রে সন্তরণের সুখ নিতে উপশহরকে অগাধ জলরাশির মাঝে ডুবিয়ে মারার ছল করছে সে? হতেও পারে। ছেলেবেলায় আম্মাদের ঘুমপাড়ানিয়া গান তো একটাই ছিল : হুঁশ! চুপচাপ ঘুমা কইছি! হাওর থাকি দেওলা উঠসে আইজ! যদি না ঘুমাও দেওলা কিন্তু লইয়া যাইব গিয়া! অদেখা দেওলার ভয়ে কাতর বালকের সাধ্য কী চোখ খোলা রাখে!
…
করোনার আগের কয়েকটি বছর, দুইহাজার পনেরো-ষোলো থেকে ঊনিশ অবধি শহরের লোকজন পাগলা ষাঁড়ের পাল্লায় পড়লে যেমন ঘটে, সেভাবে ছুটছিল। চারপাশটা বদলে যেতে দেখেছি দ্রুত। বদলানোর বেগ আরো আগে, যেমন ধরা যাক নতুন শতাব্দীর পয়লা প্রহর থেকে ষণ্ড হতে চাইলেও ঢিমেতাল ভাব ধরে আগাচ্ছিল। এর মধ্যে উপশহর ও জিন্দাবাজারটা কেবল ছিল পাগলা ঘোড়া। আকাশচুম্বি দালানকোঠা উপশহরকে অচেনা করে দিতে থাকে আর বিপণিবিতানের জেল্লায় ছেয়ে যায় জিন্দাবাজার। নয়া শহরের ওটা ছিল আদি বনেদ।
এইবেলা মনে পড়ছে, শহরের প্রবীণ প্রজন্মকে একসময় বলতে শুনেছি, মানে তারা বলাবলি করতেন,—‘দালান তুলরায় ভালা কথা কিন্তু দরগার মিনারোর উপরে দিয়া যাইয়ো না। আদব রাখাটাউ ভালা মনে অয়।’ সংস্কার সবসময় খারাপ না-ও হতে পারে। শহর থেকে বেমালুম গায়েব মুরব্বিদের জামানায় আমরা নিতান্ত দুধের ছাওয়াল ছিলাম। তবু মনে আছে, চালিবন্দর থেকে কালীঘাট, কাজিরবাজার হয়ে শেখঘাট অবধি ছড়ানো এলাকায় দালানকোঠার বাড়বাড়ন্ত থাকলেও তিন কিংবা মেরেকেটে পাঁচতলার অধিক দালান কাউকে তুলতে দেখিনি। মীরবক্সটুলা থেকে আম্বরখানা যাওয়ার সড়কে ইতিউতি দালানকোঠা চোখে পড়লেও এক তলা বাড়ির সংখ্যাই অধিক ছিল। পাঠানটুলা-বাগবাড়ি, হাউজিং এস্টেট, লেচুবাগান বা চৌকিদেখি হয়ে খাসদবির-গোয়াইপাড়া-সাপ্লাই, হাজারীবাগ-শাহীঈদগাহ-আরামবাগ থেকে টিলাগড় ও শাপলাবাগ, কিংবা টিলাগড় ছাড়িয়ে মেজরটিলা থেকে খাদিম…, বিস্তৃত এলাকাটি মোটের ওপর সুনসান ছিল তখন। ঈদগাহ ও বালুচরের পুরোটাই টিলায় ঠাসা ছিল। সন্ধ্যা হলে ঝিঁঝি ও জোনাকি ছাড়া কোনো মানুষের হল্লাগল্লা টের পাওয়ার উপায় থাকত না। রাত গভীর হলে ওদিকটা কেউ মাড়াতে চাইতেন না। দৃশ্যচিত্রটি নয়ের দশক শেষ হতেই পালটে যেতে শুরু করে, যাকে আর পরে ফেরত আনা যায়নি।
শহরটি একদিন এ-রকম ছিল, একতলা নয়তো দুতলা বাড়ির সামনে একচিলতে উঠান। রকমারি গাছের সারি সেখানে। রায়নগর-রাজবাড়ির কোল ঘেঁষে বাড়ন্ত মিতালি আবাসিক এলাকা তখনো দালানকোঠায় সয়লাব হয়নি। দালান বানানোর উপযোগী করতে টিলা কাটার তোড়জোড় চলছিল কেবল। মিতালীর সেই টিলার ওপরে উঠলে আস্ত শহর দেখা যেত। সবুজে নিকানো এক শহর! মানিক পীরের মাজার, যেটা এখন শহরের সবচেয়ে বড়ো কবরস্থান, তার চূড়ায় ওঠা ছিল গা ছমছম অভিজ্ঞতার নামান্তর। সার-সার কবরে ছাওয়া জায়গাটি এই সেদিনতক দারুণ সব অতিকায় বৃক্ষে ভরভরন্ত ছিল। আব্বার কবর ওখানে। কতবার গিয়েছি তার সঙ্গে দুটো কথা বলতে। প্যাঁচানো সিড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে পাখি আর প্রজাপতির এন্তার উড়াউড়ি ছিল সেদিনকার ঘটনা। করোনামারির দিনকালে মানিক পীরের কবরস্থানে লাশের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নগর কর্তৃপক্ষ ভাবলেন এত লাশ তারা রাখবেন কোথায়! মস্ত টিলায় ছাওয়া কবরস্থান যদিও সংকুলান হওয়ার মতো যথেষ্ট পরিসর ধারণ করে, তবু তারা সেটা ভাবলেন। করোনা শেষ হতে-না-হতে ইসলামের বরখেলাপ গণ্য করে সকল কবরের সমাধিফলক গুঁড়িয়ে সমান করে দেওয়া হলো! মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় এ-রকম থাকে শুনেছি। একখণ্ড পাথর ছাড়া কবরের কোনো চিহ্ন সেখানে রাখা হয় না। না কোনো সমাধিফলক কিংবা ও-রকম কিছু। মানিক পীরের কবরস্থান অদ্য সে-রকম এক মরুভূমি বটে!
কবর সমান হয়েছে তাতে আপত্তির কারণ দেখি না। কবরস্থানে যাওয়া মানে তো মৃতদের রুহের সদগতি কামনা করা নয়, বরং নিজের কপালে নজদিক মরণকে স্মরণ করা। গোরস্তান হলো এমন এক জায়গা যেখানে মানুষ তার সকল পরিচয় ও প্রসাধন হারিয়ে একলাটি শুয়ে থাকে। তার দেহ গলেপঁচে মাটিতে মিশে যায়। মাটি তাকে একটু-একটু করে খায়। মাটির নিচে সক্রিয় শত হাজার কীটপতঙ্গ ও অণুজীব মিলে তাকে ভক্ষণ করে। মাটি সারবান হয় এতে। তার মজ্জা চুষে তখন মাথা তুলে কচি কিশলয়। পাখির ঠুকরে খাওয়া বীজ থেকে অতিকায় মহীরুহ জন্ম নিতে থাকে। আব্বার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতাম, তিনি বোধহয় এ-রকম কোনো মহীরুহ হয়ে মানিক পীরের টিলায় দাঁড়িয়ে আছেন অথবা দাঁড়ানোর পালাটি সারছেন কেবল।
করোনার আগে অবধি এটাই চলছিল। মানিক পীরের কবরে গেলে মনে হতো আব্বার রুহ খোদার দিকে উড়াল দিলেও তার দেহ থেকে জন্ম নিয়েছে আশ্চর্য জারুল গাছ। ডালে জারুল ফুলের বাহার। ফাটাকেষ্ট মেয়র ও নগর কর্তৃপক্ষ সেখানে বাধ সাধলেন। করোনা শেষ হলে আমরা গেলাম কবরস্থান। আমাদের যে যার আব্বা-আম্মা ও স্বজনদের কবর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না জারুল-সেগুন-মেহগনি আর অতিকায় রেইনট্রির সারি। কোকিল নেই। পাখির কিচিরমিচির উধাও। দু-একটা কাক-চিলকে দেখলাম মাথার ওপর পাক খাচ্ছে। প্রকৃতির ঝাড়ুদার পাখিরাও নামার সাহস পাচ্ছে না এই মরুভূমে। গোটা কবরস্থান জুড়ে মানুষের মাতন ছাড়া বাকিটা খা খা! সিঁড়িগুলো টাইলস দিয়ে নতুন করে বাঁধানো, মুখ দেখা যায়। মেয়র সায়েবের মুখ ছাড়া কিসসু দেখার উপায় নেই সেখানে। মনে হলো, এই তো, কেমন দাঁত কেলিয়ে হাসছেন আমাদের উন্নয়ন!
মানিক পীরের কবরস্থানে ওটা ছিল শেষ যাওয়া। আর যেতে ইচ্ছে করে না। আব্বা তো নেই সেখানে। জারুল গাছ যেহেতু নেই, তার থাকার প্রশ্নই ওঠে না। আব্বার রুহ অনেক আগে খোদার আরশে স্থান করে নিয়েছে। কোরানে পড়েছি মানুষ মারা গেলে তার রুহ এক লহমায় পঞ্চাশ হাজার বছর সমান রাস্তা পাড়ি দেয়। খোদার আরশের নিকটবর্তী স্থানে বিরাম নিতে থাকে ক্রমশ। দেহটা বেঁচে ছিল জারুল ফুল হয়ে। জারুল যখন নেই কী লাভ গিয়ে! এ-রকম শত-শত জারুলকে শহর থেকে করোনা বিদায় নেওয়ার পর গায়েব করা হয়েছে। মেয়র সায়েব তাদেরকে হত্যা করেছেন অকাতর। বুক কাঁপেনি একরতি।
শহরে এখন দালানকোঠার মচ্ছব! অতিকায় স্কাইস্ক্র্যাপারে মোরা দুবাই হবো। ওটাই আমাদের উন্নতির মূলমন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী করোনামারি চলাকালে দেশ সিঙ্গাপুর হতে যাচ্ছে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। অপদার্থের দল তখন দাঁত কেলিয়ে হেসেছে। হেসো না বাছা! এটা হাসির কথা নয়। সিঙ্গাপুর-দুবাই হওয়ার দিকেই হাঁটছি মোরা। এগারো হাজার কোটি টাকা হেলেদুলে সিঙ্গাপুরে ঢুকেছে। আরো কত হাজার ঢুকছে দুবাই-কাতার-মালয়েশিয়ায়। টাকা পাড়ি দিচ্ছে লন্ডন-প্যারিস-টরেন্টো বা সুইজারল্যান্ড। বাংলার আকাশ-বাতাসে খৈয়ের মতো টাকা উড়ছে। যারা হাত বাড়িয়ে ধরতে পারছে তারাই একালের দেবতা। শহরের কোনো-না-কোনো প্রান্তে বসে করোনামারি সামলে নেওয়া দেবতারা শত কোটির ব্যবসা বাগানোর আঁক কষছেন। তার থেকে কিছু কালো টাকা সাদা হচ্ছে শহর জুড়ে ছড়ানো বিপণিবিতান আর অভিজাত হোটেল-মোটেল ও রেস্তোরাঁয়। কালো টাকা সাদা সায়েব হয়ে ঢুকছে নয়াসড়ক। নিজের জায়গা খুঁজে নিচ্ছে কুমারপাড়ায়। টাকা এক বিশ্বজনীন চলক। তার ধাক্কা প্রান্তে-পড়ে-থাকা শহর, শহরতলি এমনকি গ্রামকেও ছেড়ে কথা কয় না, কোনোদিন কয়নি। এই শহর মড়কের পূর্বাভাস পেয়েছিল মিলেনিয়াম শুরুর বছর। করোনার ঘোরপ্যাঁচে খানিক থমকে ছিল মড়ক। এখন সে মুক্ত বিহঙ্গ। ঝাঁকের কৈয়ের মতো গজিয়ে-ওঠা রিসোর্ট আর শত হাজার ইনভেস্টমেন্টে তাকে উড়তে দেখছি শহরের যত্রতত্র। রাজধানী ঢাকার মতো নয়, ওটা সম্ভব নয়, টাকা তথাপি উড়ছে একদা সবুজে নিকানো শান্ত মফস্বল শহরে!
তো, দাপুটে এই মড়কের জেরে ঝা চকচক ব্রান্ডের দোকানপাট শহরে দেখা দিলো সারসার। জিন্দাবাজারটা একমাত্র থাকল না আর! আড়ংয়ে ঢুকে ঈদের কেনাকাটায় এল বৈচিত্র্য ও বাহার। আড়ং তার নিজেকে টিকিয়ে রাখতে আরেক ধাপ পেল্লাই হলো। তাকে টেক্কা দিতে কাপড়ের দোকানপাটে ছেয়ে যেতে লাগল শহর। তার সঙ্গে একেকটি কেন্দ্রস্থলে রাজ করতে এলেন পানসী ও পাঁচভাইর মতো নয়া জামানার হোটেল-রেস্টুরেন্ট। শামিয়ানা টাঙানো বিয়েবাড়ির মতো খোলা চত্বর, ভিতরে রেস্টুরেন্টের আদলে সারিসারি টেবিল, দুইয়ের রসায়নে জমাট রসুইঘরে মানুষ উপচে পড়ছে। খাবার পরিবেশনার অভিনব তরিকার নিচে একে-একে চাপা পড়েছে ওইসব হোটেল যাদেরকে একসময় জিন্দাবাজারের জান মানা হতো। পঞ্চখানা মরহুম। জালালাবাদ আর বেঁচে নেই। একটা দশক জুড়ে রাজ করতে থাকা প্রীতিরাজও টিকতে পারেনি শেষতক। সস্তা ভাতের হোটেল খ্যাত রয়েলটা বোধ করি এখনো টিকে আছে। নিভু নিভু জ্বলছে তার আয়ু। বন্দরবাজারে হোটেল নীরা জীবিত আছে কি? নতুন সব হোটেলের ভিড়ে তাকে তো খুঁজে পাই না! এই হোটেলকে ঘিরে কবি-লেখক-নাট্যজনদের আড্ডা বসত একসময়। বাউল শাহ আবদুল করিম শহরে এলে এখানে উঠতেন। খোয়াব বের করার দিনগুলোয় হোটেলে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। আপনা খেয়ালে কত কথাই বলেছিলেন। আমাদের আবদার মিটাতে নিজের দু-একটা গানও গেয়েছিলেন সেদিন।
ওদিকে চাইনিজ খাবারের রেস্তোরাঁগুলো কোন ফাঁকে শহর থেকে উবে গেল টের পাইনি। এখন দেখছি করোনামারি শুরু হওয়ার বেশ আগে থেকে তারা উবে যেতে শুরু করেছিল। তাদের জায়গাটি তাই বলে শূন্য পড়ে নেই। প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না। চাইনিজ রেস্তোরাঁ বিদায় নিতে-না-নিতে দেশিবিদেশি রকমারি খাবারের পসরা নিয়ে হাজির হয়েছেন নতুন খাবারবিক্রেতা। উপশহর, জিন্দাবাজার, দর্শনদেউড়ি থেকে আরম্ভ করে শাহী ঈদগাহ, নয়াসড়ক আর কুমারপাড়ায় এখন উনাদের দাপট। খাদ্যসম্ভারের দিক থেকে শহরটি কসমোপলিটান হতে যাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্কৃতিদেহে নিজেকে অঙ্গীভূত করার পালা সাঙ্গ করছে সে।
বহুজাতিক খাদ্যসংস্কৃতির বিচারে সে অবশ্য এখনো টডলার, হামাগুড়ি দিচ্ছে কেবল। আসল কেএফসি, ম্যাকডোনাল্ডস-র মতো ফুডচেইন এখানে জাঁকিয়ে বসেনি। বাংলাদেশে এক টুকরো লন্ডন বিদিত শহরে তাদের আগমন সহসা ঘটতেও পারে। ম্যাকডোনাল্ডস থেকে খাবার কেনার হিম্মতদার একটি প্রজন্ম দেশে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। শহরটি তার ব্যতিক্রম নয়। করোনাঝড় কাটিয়ে ওঠা শাহরিক দৃশ্যপট একখানা ম্যাকডোনাল্ডস-র অপেক্ষায় সকাতর মনে হচ্ছে। ম্যাকডোনাল্ডস যদি আসে তাহলে এই কনট্রাস্ট সবাই দেখতে পাবে,—জগৎখ্যাত ফুডচেইন থেকে খাবার কিনতে লোকের লম্বা সারি, তার ঠিক পাশেই টিসিবির ট্রাক থেকে কেজিখানেক চাল-ডাল-নুন-তেল বাজারদর থেকে কমে কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েছে পাল-পাল হতভাগার দল! মধ্যবিত্ত আপিসকামলাও লজ্জাশরম ধুয়ে লাইনে শামিল সেখানে। হাভাতের লম্বা মিছিলে তাকেও দেখতে পাচ্ছে শহর।
খাদ্যসংস্কৃতির বহুজাতিক চরিত্র শহরে এতদিন ছিল না। সন্ধ্যার নাস্তা ও রাতের খাবার বলতে লোকে স্ট্রিটফুডের ঘরোয়া সংস্করণ সিঙ্গারা-সমুচা-জিলিপি-ডালপুরি-পেঁয়াজুর দোকান, বিস্বাদ চটপটি আর ভাতের হোটেলকে বুঝত। এইবেলা স্ট্রিটফুড নিজেকে তিনচাকার গাড়িতে যুতে দিয়েছেন। পিজা-বার্গার-স্যান্ডউইচ-গ্রিল আর শিক কাবাবের রমরমা দাপট সেখানে। ফুচকা-চটপটির দোকানে লেগেছে ঢাকাই হাওয়া। জিলিপির দোকানগুলো শহরের কোনাকুনচিতে টিকে থাকলেও তাদের জেল্লা অস্তমিত। নয়ের দশকের গোঁড়ায় শহরে বোম্বাই জিলিপির প্রচলনকে জনপ্রিয় করে তোলা ফওজিয়ার শানমানগুণ কিছু আর বেঁচে নেই। আম্বরখানার কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত দোকানটি হটিয়ে নতুন জিলিপি-সিঙ্গারার দোকান বসলেও সেগুলোকে ফওজিয়ার ছায়া ভাবাটাও অপমানজনক ঠেকে।
মিষ্টি কিংবা দইয়ের জন্য এই শহর কোনোদিনই বিশিষ্ট ছিল না। তবু মোহনলাল ঘোষের দই-মিষ্টির কদর ছিল একসময়। এই ধাঁচের দোকান যেগুলো মূলত চট্টগ্রাম থেকে সিলেটে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, ওইসব বনফুল–ফুলকলি–মধুবন–পিউরিয়ার মিষ্টিতে সেই জাদু নেই যেটা দেশের অন্য অনেক অঞ্চলকে বিখ্যাত করে রেখেছে। সবেধন নীলমণি মির্জাজাঙ্গালের চোরাকুঠরিতে বনতে থাকা মিষ্টি ও নিমকির মানটাও বোধ করি বিগত দিনের ছায়া। করোনার পর তার অধঃপতন দেখছে শহরের মিষ্টিপ্রেমীগণ। সময়ের সঙ্গে এভাবে উবে গেছে জিন্দাবাজারের ফুটপাত ঘেঁষে রাজ করতে থাকা জিলিপি ও পুরি-পেঁয়াজুর দোকান। তাদের বৈভবকে ফেরত আনার মতো কারিগরের আকাল এখন। করোনার দাপট নিস্তেজ হয়ে আসলেও পুতিন-বাইডেন নামধারী অণুজীবরা নতুন মড়ক হয়ে দেখা দিয়েছেন সদ্য। লোকের জীবনযুদ্ধের বাও ও টিকে থাকার তরিকা যে কতটা বিভীষিকাতুল্য হয়ে উঠছে তার নীরব প্রমাণ হয়তো এতেই নিহিত।
…
শুরু করেছিলাম করোনামারি হানা দেওয়ার আগের কয়েকটি বছর জুড়ে চোখের সামনে ঘটতে থাকা ষণ্ড উন্নয়নের কাহিনি দিয়ে। পরিশেষে এসে দেখছি কিবোর্ড অন্য দিকে ধাইছে। আর্মিকাট ও সুইসাইড পিৎজা নামের মামুলি দুটি রচনা লিখে ওঠার তাগিদ করোনাঝড়ের প্রাকলগ্নে কী কারণে মাথায় ভর করেছিল সেটি বলব বলেই-না এত ভ্যানতারা। চেষ্টা করেও সেদিকপানে যাওয়া গেল না। সুইসাইড পিৎজা লিখে ওঠার কার্যকারণ কিছুটা মনে হয় বলতে পেরেছি। শহরজুড়ে চুলকাটার নতুন আয়োজন, মানে ওই সেলুনকালচার নিয়ে বাত আপাতত মুলতবি রাখতেই হচ্ছে। ফাঁকতাল বুঝে কোনো একদিন ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছে থাকল। শহর জুড়ে ঘটমান উন্নয়নে পুলকিত হওয়ার খোয়াব থেকে বানানো ইচ্ছেগুলি, ওই সময় যার আবেশ মনকে বেশ নেশাতুর করেছিল, উপসংহারে গমনের মুহূর্তে সেদিকে ফিরে তাকানো যাক একবার।
আরবার বলি কথাটা, মনে বড়ো আশা ছিল, দৈত্যাকৃতির ট্রাক-বাসগুলোকে শহরের নাভিতে ঢুকতে না দেওয়ার উপায় বের করবে মোদের এই ফাটাকেষ্ট উন্নয়ন। উপশহরমুখী সড়কের দুপাশ জুড়ে ছিতরে থাকা বিদঘুটে সবজিবাজারকে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে সে। বিদ্যুতের খুঁটিকে প্যাঁচ দিয়ে ছড়ানো বিচিত্র কিসিমের তারের জঙ্গলকে মাটির নিচে পাঠানোর পরিকল্পনা টক অব্য দ্য টাউন ছিল মনে পড়ছে। শাহজালালের মাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে ‘তার’ নামক তারকাঁটার প্যাঁচ অপসারিত হতে দেখে পুলকিত ছিল অন্তর। তার মধ্যে নাইটমেয়ার কি ছিল না? ছিল বৈকি। স্থাপনা স্মৃতি মুছে দেয়;—কথাটি কে বলেছিলেন মনে পড়ছে না, যদিও এর সারসত্যে সংশয় মিটে গিয়েছে। স্মৃতি মুছে দেওয়ার কত কাহিনি বলাই হলো না শেষতক! মুছে যাওয়ার চটজলদি তালিকা তৈরি করা বেশ কঠিন। আবু সিনা ছাত্রাবাসকে তবু স্মরণ করতে বাধ্য এই মন। ওসমানী মেডিকেল কলেজে পড়ুয়াদের জন্য যে-ছাত্রাবাসগুলো শহরে রয়েছে তার মধ্যে ওটা তোফা ছিল দেখতে। ছাত্রাবাসটি আর নেই! তার বদলি খাপছাড়া এক বহুতল ভবন গজিয়েছে সেখানে,—মেডিকেল পড়ুয়াদের থাকার জায়গা করে দিতে। বাদপ্রতিবাদে ফল মিলেনি। ফাটাকেষ্ট উন্নয়নের সময় কোথায় যে প্রতিবাদে কান দিবে!
বোঝা গেল, আমাদের সকল উন্নয়ন, আধুনিক শহর তৈরির ফন্দিফিকিরের সবটাই পুতুল নাচের ইতিকথার বিখ্যাত উক্তির স্মারক : শরীর! শরীর! তোমার মন নাই, কুসুম? মোদের ষণ্ড উন্নয়ন এমনধারাই বটে! মন নয় তার কেবল দেহটাকে চাই। মনের চাষাবাদ সেখানে বিলকুল মানা। দশকের-পর-দশক ধরে এই মাইনক্যা চিপায় আমরা যারা পড়ে আছি তারা এখন যতই ঢাকাই সিনেমার অমর ডায়ালগটি আওড়াই, যতই চিৎকার করে বলি, ‘ছেড়ে দে শয়তান। তুই আমার দেহ পাবি, মন পাবি না।’;—ষণ্ড উন্নয়নের অট্টহাসি তাতে থামানো যাবে না। আমরা কমবেশি বেকুব। মনের ঠিকাদারি নিতে কেউ আর ব্যস্ত নেই এই শহর কিংবা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো অন্য শহরগুলোয়। মন পাবি না বলাটা হচ্ছে এক বাজে অভ্যাস। বদখোয়াব। অক্ষমের সান্ত্বনা পাওয়ার প্রাণান্ত প্রয়াস। দেহটাই মন;—কথাখান সুবোধ তুমি বুঝে নিও সত্বর। দেহের খেলায় আনন্দ শুষে নেওয়ার নাম হলো পুণ্য। জগতের সেই আনন্দযজ্ঞে তুমি শরিক হও। অতিমারির ভীতি ঝেড়ে স্মার্ট সিটিজেন হওয়ার ওটাই আয়ুধ। এর বাইরে সবটাই ফক্কা।
শহর সংক্রান্ত অন্যান্য রচনা
আহমদ মিনহাজ রচনারাশি
- আধুয়া গ্রামের নৌকাপূজা : নানান ধারার গানের গ্রামীণ মেলা || বিমান তালুকদার - February 2, 2026
- ঊষর দিন ধূসর রাত : উপন্যাসের তন্তু ও তাঁত || রাশিদা স্বরলিপি - January 24, 2026
- সরস্বতী বিশ্বলোকে || সুশান্ত দাস - January 23, 2026

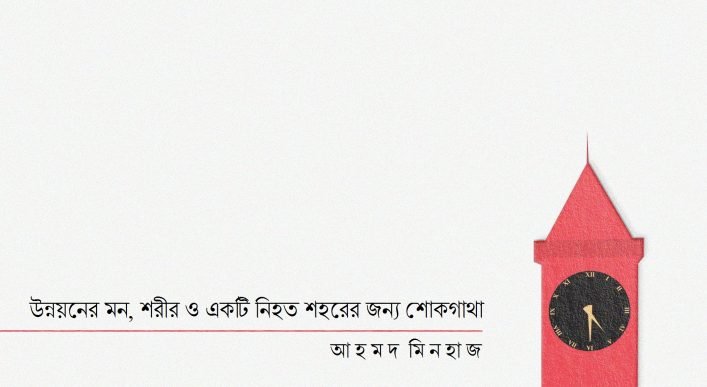
COMMENTS