সত্তর সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি ঢাকায় অবস্থান করছিলাম। একদিন আমার মামাতো ভাই ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর গুলশানের বাসায় শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার ঘরোয়া আসরে গুণীজনদের সঙ্গে কৈশোরোত্তীর্ণ তরুণ আমাকেও আমন্ত্রণ করেন। সেই সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে ওস্তাদ নাজাকাত আলী ও সালামত আলী ভ্রাতৃদ্বয় রাগেশ্রী, মালকোষ ও কতিপয় ঠুমরি পরিবেশন করেন। তাদের সংগীত আমাদের সবাইকে আবিষ্ট ও আচ্ছন্ন করে ফেলে। সংগীতের আসর শেষ হলে ভিকারভাই তাঁর এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই ছিপছিপে স্মিত হাসির তরুণ বন্ধুটি ছিলেন জনাব ফজলে হাসান আবেদ। এবং সেদিনই জানতে পারি তিনি বানিয়াচঙের বিখ্যাত হাসান পরিবারের সন্তান।
ফজলে হাসান আবেদ তখন চট্টগ্রামে শেল-কোম্প্যানিতে কর্পোরেট ফিন্যান্স বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ভিকারভাই এবং আবেদভাই বিলেতে একই বাড়িতে থাকতেন। বিলেতে শিক্ষাজীবন ও কিছুকাল কর্মজীবন যাপনের পর আবেদভাই দেশে ফেরেন। ভিকারভাই ও আবেদভাই দুজনেই তাদের কর্মজীবনের পাশাপাশি শিল্পসাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন। সংগীত ছাড়াও চিত্রকলায় তাদের দুজনেরই ছিল প্রবল আকর্ষণ। রাজনীতি ও সামাজিক বিবর্তন নিয়ে তারা তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রায়ই লিপ্ত হতেন।
দেশে তখন রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা। সময়টা সত্তরের মাঝামাঝি। নভেম্বর মাসে ঘটল সমস্ত উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়। ভিকারভাই ও আবেদভাই তাদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে ব্যাপৃত হলেন, গড়ে তুললেন ‘হেল্প’ কর্মসূচি। তারা ঝড়ে-ক্ষতিগ্রস্ত মনপুরা দ্বীপে তাদের সহায়তা কার্যক্রম নিয়ে যান।
১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধ। আবেদভাই ও ভিকারভাই দেশ ছেড়ে বিলেতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযুক্ততার কারণে দেশে থাকা তাদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। বিলেতে গিয়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে পশ্চিমা বিশ্বে জনমত গড়ার কাজে এবং ভারতে অবস্থানরত শরণার্থীদের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গড়ে তোলেন ‘অ্যাকশন বাংলাদেশ’ও ‘হেল্প বাংলাদেশ’ নামে দু-দুটো কর্মসূচি।
মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভিকারভাই সিলেট শহরের মীরের ময়দানে আমাদের বাসায় আসেন এবং দেশে ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনার ব্যাপারে সিলেটের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলোচনার জন্য তৎপর হন। সেইসময় কমরেড বরুণ রায় শাল্লা ও দিরাই অঞ্চলে ভারত-প্রত্যাগত ঘরবাড়ি-হারানো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাণ কর্মসূচি পরিচালনার প্রস্তাব করেন। সেই-অনুযায়ী কিছু ওষুধপত্রাদি সহ ভিকারভাই একটি ছোট্ট দল নিয়ে দিরাইয়ে চলে যান। সেইখানে প্রাথমিক পর্বের একটি ত্রাণ বণ্টন কর্মসূচির প্রবর্তন হয়। এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসে, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, আবেদভাই তাঁর এক সঙ্গী জনাব আলী আশরাফকে নিয়ে আমাদের বাসায় আসেন এবং কীভাবে এই ত্রাণ কর্মসূচিটি অধিকতর সংগঠিত উপায়ে আরও লক্ষ্যাভিমুখী করে তোলা যায়, এইসব প্রসঙ্গ ধরে আমার অগ্রজ (সহোদর) অ্যাডভোকেট মোশতাক হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই ভিকারভাইকে তাঁর পারিবারিক ও পেশাগত প্রয়োজনে ফের বিলেতে চলে যেতে হয়। আবেদভাই গোটা ত্রাণ কর্মসূচিটি রূপায়ণে নেপথ্য থেকে এই পর্যায়ে সম্মুখে এসে কাজ শুরু করেন। দুর্গম হাওরাঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে ঘোরাঘুরি দিয়ে আবেদভাইয়ের সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ দর্শন শুরু হয়।
আবেদভাই এই কর্মসূচিটিকে পরিচালনার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন এবং ‘বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাসিস্ট্যান্স কমিটি’ নামে সংগঠন নিবন্ধিত করলেন। জন্ম নিলো ব্র্যাক।
ব্র্যাকের সূচনাপর্বের আরেকটি কর্মসূচির উল্লেখ করা প্রয়োজন। সিলেট শহর ও তৎপার্শ্ব লোকালয়ে অনেক মনিপুরী জনগোষ্ঠীর বাস। যুদ্ধকালীন এই জনগোষ্ঠীর অনেকেই নিরাপত্তাহীনতায় সীমান্তবর্তী ভারতে চলে গিয়েছিলেন। মুক্ত বাংলাদেশে তারা দলে দলে ফিরে আসতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সুদক্ষ কাঠমিস্ত্রী এবং বিশেষভাবেই নারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন বয়নশিল্পী। আবেদভাইয়ের নির্দেশনায় আমার অগ্রজ মনিপুরী সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেন। জরিপে প্রাপ্ত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়। এই প্রস্তাবনাটি আমাদের বাসায় অতি পুরাতন রেমিংটন টাইপরাইটারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০১টি পরিবারকে কাঠমিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি ও তাঁতের আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই পুরো পরিকল্পনাটি UNROD (United Nations Relief Operation Dacca)-এর আর্থিক সহযোগে বাস্তবায়ন করা হয়।
এই সময়ে আবেদভাই প্রায়শই শাল্লায় অবস্থান করতেন। যাওয়া-আসার পথে আমাদের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও বিরতি নিতেন। আমার মনে আছে, এ-সময় আবেদভাই বলেছিলেন যে, “আমি পূর্ণ একবছর ত্রাণকাজে লিপ্ত থাকব এবং দায়িত্বটা শেষ করেই আমার পূর্বতন পেশায় ফিরে যাব।” ব্র্যাকের কাজ এমনভাবে বিস্তৃত হতে থাকে যে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দ্বিতীয় কোথাও যাবার ফুরসত আবেদভাইয়ের আর হয়নি। তিনিও জড়িয়ে গেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে ব্র্যাকের সঙ্গে, ব্র্যাকও তেমনি আবেদ ভাইয়ের স্বপ্নদর্শনে উত্তরোত্তর এগিয়েছে সম্মুখপানে।
এ-সময় গৃহপুনর্নির্মাণের এক বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণসামগ্রী তথা বাঁশ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী ভারতের আসাম রাজ্য থেকে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা গৃহীত হয়। এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবেদভাইয়ের সহকর্মী জনাব আলী আশরাফ। তিনি করিমগঞ্জ থেকে আমার অগ্রজকে জানান যে ভারতীয় সীমান্তরক্ষায় নিয়োজিত বাহিনী তথা বিএসএফ বাঁশের সুবৃহৎ চালানটি বাংলাদেশে নিয়ে আসার অনুমোদন দিচ্ছে না। আমার অগ্রজ তৎক্ষণাৎ আওয়ামী লীগের নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজীর দ্বারস্থ হন। উনি করিমগঞ্জের মহকুমাপ্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাঁশের চালান মুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেন। উল্লেখ্য, এই বাঁশ এবং ঢেউটিন ব্যবহার করে দিরাই ও শাল্লায় বিশ হাজার গৃহহীনের গৃহনির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহপুনর্নির্মাণের কর্মসূচি সম্পন্ন করা হয়। ত্রাণসামগ্রীর অধিকাংশ চালানই তখন জাতিসংঘের কার্গো উড়োজাহাজযোগে ঢাকা থেকে সিলেটে আসত। অন্তর্বর্তীকালীন সংরক্ষণাগার হিসেবে আমাদের বাসার বহির্ভাগের একাংশ ব্যবহৃত হতো বস্তুসামগ্রী সাময়িক সুরক্ষার জন্য। গন্তব্যস্থলের সঙ্গে ত্রাণকর্মকদলের প্রয়োজনীয় যোগাযোগ সম্পন্ন হলে শেরপুর ভায়া হয়ে নৌপথে মালামাল দিরাই-শাল্লায় পৌঁছাত।
১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে আমি ইন্টারন্যাশন্যাল ভল্যান্ট্যারি সার্ভিসেস (আইভিএস)-এ যোগ দেই। অপরদিকে আমার দুই বন্ধু মসরুর ও মোশতাক ব্র্যাকে যোগ দেয়। মসরুর ছিল ব্র্যাকের লজিস্টিক বিভাগের দায়িত্বে এবং পরবর্তীকালে ব্র্যাক প্রিন্টার্স স্থাপনে মুখ্য উদ্যোগী। মোশতাকের কাজ ছিল গবেষণা বিভাগে। ঢাকায় গেলে মসরুর-মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্র্যাকে যেতাম। সে-সময়ে সুযোগ পেলে আবেদভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতাম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও আবেদভাই স্মিত হাসির সঙ্গে আমাকে সম্ভাষণ করতেন এবং চা পানের ফুরসতে উন্নয়ন বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয় পেতাম যথেষ্ট অন্তরঙ্গভাবে। সে-সময় আবেদভাইয়ের অকালপ্রয়াত স্ত্রী বাহার ভাবীর (আয়েশা আবেদ) স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটে। বাহারভাবী ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও অগ্রসর চৈতন্যের ব্যক্তিত্ব।
এরপর ১৯৭৯ সালের দিকে একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এফআইভিডিবি গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই সময়ে সংগঠন নির্মাণসংক্রান্ত শলাপরামর্শ করার জন্য আমাদের তথা আইভিএস-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ডেভিড ফ্রেঞ্চ, তৎকালীন সহকর্মী সুলতানা কামাল ও আমি আবেদভাইয়ের কাছে যেতাম। তখনই আমরা সংগঠন নির্মাণ ও বিকাশের ধীশক্তিসম্পন্ন কুশলী শিল্পীর প্রতিকৃতি দেখেছি আবেদভাইয়ের মধ্যে, পরবর্তী দেড়/দুই দশকের মধ্যেই যিনি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠাননির্মাতার অভিধা লাভ করবেন। উন্নয়নশীল একটি দেশের শত বিঘ্নপূর্ণ পরিবেশে থেকেও প্রতিষ্ঠান সৃজনের এহেন সুচারু নজির দুনিয়ার নবতর উদ্যোক্তাদের জন্য অনুপ্রেরণাকর।
১৯৮০ সালে রেমেন ম্যাগস্যাস্যাই অ্যাওয়ার্ড পেলেন আবেদভাই। বিশ্বজোড়া খ্যাতি, সম্মান ও সমাদরের সেই যাত্রা আবেদভাইয়ের আজও অব্যাহতভাবে বজায় রয়েছে। অ্যাওয়ার্ড ঘোষণার অব্যবহিত পরেই আবেদভাইয়ের সঙ্গে দিরাই-শাল্লা ভ্রমণের সুযোগ পাই। সে-যাত্রা কাজের সুবাদে ভ্রমণ হলেও আবেদভাইয়ের ব্যক্তি-প্রতিকৃতিটি নিবিড়ভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই আজ স্মরণ করে উঠি। হাওর-অধ্যুষিত জলবহুল অঞ্চলগুলোতে সে-সময় খাওয়ার স্যালাইন ঘরে তৈরি করার কৌশল শিখনের একটি নিরীক্ষাপর্যায়িক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল। এই নিরীক্ষাটি ধীরে ধীরে এতই কার্যকর প্রমাণিত হয় যে একে প্রসারিত করে পরবর্তীকালে সমস্ত দেশ জুড়ে ঘরে ঘরে শেখানো হয়। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর আধিক্য সত্ত্বেও গোটা বাংলাদেশে ডায়রিয়ার প্রকোপ রোধের এই অভিযানে ব্র্যাক ছিল বাস্তবায়নকারীর ভূমিকায় এবং এই প্রতিষ্ঠানের অবদান দেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন খাতে অবিস্মরণীয়। এভাবেই উন্নয়নশাস্ত্রে Learning Process Approach (শিখনপ্রয়াসী উদ্যোগ) সূচিত হয়।
১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা সিলেটে এফআইভিডিবির তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি প্রতিফলন ও পরিকল্পনা সভার আয়োজন করি। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আবেদভাইকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি এসেছিলেন। সভার মূল অধিবেশনে উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা ও শিখনপ্রয়াসী উদ্যোগ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। আমাদের সহকর্মীগণ ছাড়াও সিলেটের বিশিষ্টজনেরা এ-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৮৫ সনে আমরা এফআইভিডিবির জন্যে একটি পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। এখানেও আবেদভাইকে আমরা বিশেষ উপদেশনাকারী হিসেবে পেয়েছিলাম। তিনি আমাদের সংগঠনের গোড়ার দিককার পার্সপেক্টিভ প্ল্যান নির্মাণে মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন। একই বছরে সিলেটে আড়ং-এর একটি শাখা স্থাপন করা হয়। আমার সুযোগ হয়েছিল এক্ষেত্রে আবেদভাইকে সার্বিক সহযোগিতা করার।
১৯৯০ সালে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পৃক্ত সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলি, যা ‘গণসাক্ষরতা অভিযান’ বা CAMPE হিসেবে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটির কাউন্সিলর-সভাপতি ছিলেন আবেদভাই। এইখানে উল্লেখ্য, অনেকদিন এই নেটওয়ার্কের সহ-সভাপতি হিসেবে আমি বৃত ছিলাম। CAMPE শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যকরভাবে লবি ও অ্যাডভোকেসির কাজ করে যাচ্ছে।
আমার সুযোগ হয়েছিল বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আবেদভাইয়ের সঙ্গী হওয়ার, এর মধ্যে ১৯৯২ সালে চিলির স্যান্তিয়াগোতে এনজিওদের আন্তর্জাতিক জোট এল্টাইয়ার (El Taller) প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলনে যোগদান অন্যতম। উল্লেখ্য, স্যান্তিয়াগোতেই আমরা শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক পাওলো ফ্রেইরির সাক্ষাৎ ও সাহচর্য লাভ করি। এখানে আরেকটি স্মৃতির উল্লেখ করতে চাই। ২০০৪ সালে প্রবাসী বাঙালিদের আমন্ত্রণে আমরা নিউইয়র্কে যাই। একদিন সকালবেলায় আবেদভাই ও আমি ছিলাম অবসরের মেজাজে, কোনো কাজ ছিল না তেমন, সে-বেলাটায় আমি ও আবেদভাই রবিঠাকুর থেকে শুরু করে জীবনানন্দ হয়ে শেইক্সপিয়রের সনেট, শেলি, জন ডান ও টিএস এলিয়টের কবিতার আলাপচারিতায় মেতে উঠি। সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম, এতসংখ্যক কবিতা আবেদভাইয়ের স্মৃতিস্থ দেখে। এবং লক্ষ করেছিলাম কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারে তাঁর সপ্রেম আগ্রহ।
১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ করেই আমার অসুখ ধরা পড়ে। ঢাকায় ডাক্তারদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে চিকিৎসা শুরু হয়। আমার অসুখের খবর শুনে আবেদভাই আমাকে দেখতে আসেন। আবেদভাই ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন বন্ধু মিলে আমাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অনতিবিলম্বে সিঙ্গাপুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আমার এই ব্যক্তিগত দুঃসময়ে আবেদভাই ও অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের সহায়তা আমাকে ফের জীবনে ফেরায়ে এনেছে।
আমার আজীবনের সুহৃদ ও সহপাঠী বন্ধু ড. জিয়াউদ্দীন আহমেদেরও রয়েছে আবেদভাইয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা। উল্লেখ্য, ড. জিয়াউদ্দীন প্রফেসর অফ নেফ্রোলোজি হিসেবে ফিলাডেলফিয়ার ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত। আমাদের সুযোগ হয়েছিল সিলেটের নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের নিয়ে আবেদভাইকে একটি সংবর্ধনা প্রদানের। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে এই নাগরিক সংবর্ধনা আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে আবেদভাইয়ের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহানুধ্যায়ী ব্যারিস্টার ভিকারুল ইসলাম চৌধুরীও তৎসঙ্গে সংবর্ধিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত অবাক-করা ব্যাপার ছিল এ-ই যে, সিলেটের নাগরিকবৃন্দ অনেকেই জানতেন না স্যার এফ.এইচ. আবেদ সিলেটেরই সন্তান। সিলেটের কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত নাগরিক সংবর্ধনা সভায় জেলার এবং গোটা বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো থেকে আগত ফজলে হাসান আবেদের গুণগ্রাহীদের জমায়েত হয়েছিল। সমবেত দর্শনার্থীদের সকলে এসেছিলেন শুধু আবেদভাইয়ের সঙ্গে একবার করমর্দন করতে এবং তাঁর কথা শুনতে। সভার আনুষ্ঠানিকতা শেষে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী লোকগান ও মনিপুরী নৃত্য পরিবেশিত হয়েছিল সংবর্ধিতদের সম্মানে।
আবেদভাইয়ের মধ্যে আমি কতকগুলি বিরল গুণ লক্ষ করেছি বিগত চল্লিশ বছরের পথচলার নানা বাঁকে। এর মধ্যে একবাক্যে কয়েকটি গুণের উল্লেখ করা যায়, যেমন : তাঁর দূরদৃষ্টি, নেতৃত্ব, সৃজনকুশলতা, সুনিপূণ ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি বৃহত্তর পরিসরে কাজের অদম্য স্পৃহা। ব্যক্তিগত জীবনে আবেদভাই চিত্রকলা ও সংগীতের সমুজদার, সদালাপী ও অত্যন্ত বন্ধুবৎসল। তিনি নিজে যেমন স্বপ্ন দেখতে জানেন, স্বপ্ন দেখাতে জানেন তাঁর সহযাত্রী সবাইকে, স্বপ্ন রূপায়ণের পথটাও তিনি নির্দেশ করতে পারেন। যারাই সান্নিধ্যে গেছেন, অথবা তাঁকে দেখেছেন নিবিড় মনোযোগে দূর থেকে, তাঁর স্বপ্নদর্শী সাহসের প্রেরণা লাভ করেছেন সকলেই।
আমরা প্রায়শ লক্ষ করি যে স্বপ্নদ্রষ্টা চারপাশে অনেকেই থাকেন যারা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হন নিজের স্বপ্ন, অন্যদিকে নিরেট বাস্তবায়নকারীও অনেকেই যারা স্বপ্ন দেখতে জানেন না। আবেদভাইয়ের মধ্যে সেই বিরল গুণের মেলবন্ধন ঘটেছে, যে-কারণে তিনি আমাদের অনেকের কাছেই দিশারী হয়েছেন। কর্মজীবনে আবেদভাই অত্যন্ত নিয়মানুবর্তী ও সময়নিষ্ঠ; সচরাচর অতিমাত্রায় নিয়মানুবর্তী ও সময়নিষ্ঠদের ক্ষেত্রে সৃজনকুশলতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়, এবং আবেদভাই এখানেই পৃথক ও সার্বভৌমপ্রায়। তাঁর এই আশি-পদার্পণের পরিণত প্রজ্ঞার জীবনে তিনি আজও ত্বরান্বিত করে চলেছেন মানুষের স্বপ্নের অনুরূপায়ণ।
যেহীন আহমদ : প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী, এফআইভিডিবি; নিবন্ধরচয়িতা ২০১৮ অক্টোবরে লোকান্তরিত।
সদ্যপ্রয়াত ফজলে হাসান আবেদের বয়স আশি বছরে পদার্পণ উদযাপনের অংশ হিশেবে ২০১৬ এপ্রিলে ব্র্যাক থেকে বেরোয় ‘স্যার ফজলে হাসান আবেদ সংবর্ধনা গ্রন্থ’। বর্তমান রচনাটা কালেক্ট করা হয়েছে সেই সংবর্ধনাগ্রন্থ থেকে। — গানপার
… …
- আধুয়া গ্রামের নৌকাপূজা : নানান ধারার গানের গ্রামীণ মেলা || বিমান তালুকদার - February 2, 2026
- ঊষর দিন ধূসর রাত : উপন্যাসের তন্তু ও তাঁত || রাশিদা স্বরলিপি - January 24, 2026
- সরস্বতী বিশ্বলোকে || সুশান্ত দাস - January 23, 2026

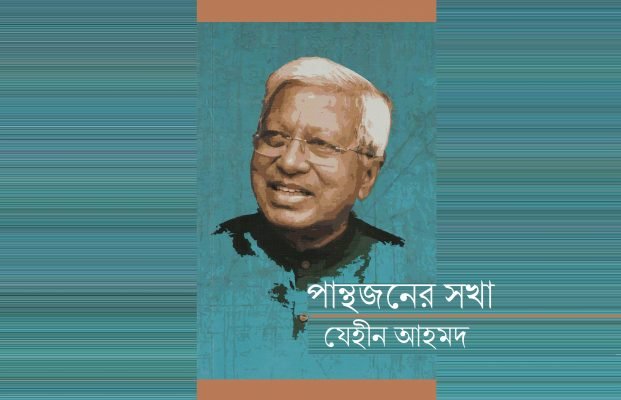
COMMENTS