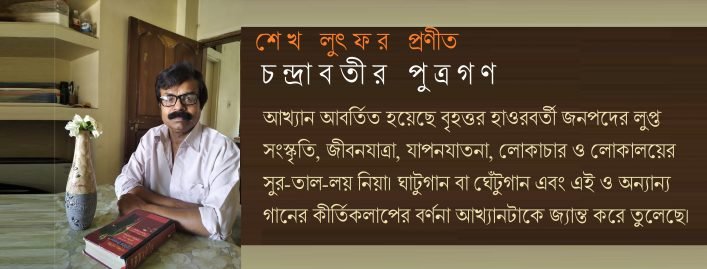
বিষহরি বিত্তান্ত
ভাদ্র মাসে কানায় কানায় ভরা থাকে কালাইবিলের পাথার। অনেক উঁচুতে থাকা আসমানটা নেমে আসে হাতের নাগালে — তখন রোদ-বৃষ্টি আর মাতাল হাওয়া কত সুরে কথা কয়! এই বিল দৈর্ঘ্যে অন্তত চার মাইল আর প্রস্থে কমপক্ষে তিন মাইল। পুব-দক্ষিণ কোনা থেকে শাঁ শাঁ করে ছুটে আসছে বাতাস। যতদূর চোখ যায় খালি ঢেউ আর ঢেউ। ঢেউয়ে ঢেউয়ে কালাই পাথারের বিল আজ থৈ থৈ সমুদ্র। আফালে আফালে ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চিকচিক করে বিষুরি-জিনের নাতিপুতিদের রাগী চোখ। খাঁ খাঁ রোদ মাথায় নিয়ে তিন মাইল হেঁটে খেলা এসে বিলপারের চাতালে দাঁড়ায়। মাথার চকচকে কালো বাবরিটা দুরন্ত বাতাসে আউলঝাউল, ঘামে-গরমে শ্যামলা মুখটা লালটি বরন, হাতের খাঁচায় একজোড়া কবুতর। মাথার ওপর কাঁসা-পিতলের থালার মতো সুরুজটা খাঁ খাঁ জ্বলছেই, পায়ের নিচে কার্পেটের মতো তুলতুলা দুর্বাঘাস, সামনে থমথমে গভীর পানির বিষহরির থলি। অর্থাৎ কালাই বিলের অথৈ ডহর। দুপুর হলে কেউ পারতপক্ষে এখানে একা একা আসে না। চৈত মাসেও বিষহরির থলিতে পানি থাকে মাথা-সমান। রাক্ষসের মতো বড় বড় গজার মাছগুলা পানির ওপর পিঠ ভাসিয়ে, গোল গোল চোখ মেলে একঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। চারপাশে সাত গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, বিষুরির থলিতে জোড়া কবুতর মানত করে কেউ কিছু চাইলে সুফল মিলে শতভাগ। খাড়া-দুপুরের রোদে বিষুরির থলি এখন ঝিকঝিক করছে। তোমার মনে যদি কোনো গোপন দুঃখ থাকে, বুকে যদি না-বলা কষ্ট থাকে আর যদি সেই দুঃখ-কষ্ট লাঘবের আশায় মানত করে থাকো জোড়া কবুতর তবে তো তোমাকে আসতেই হবে এই কালাই পাথারের সামনে। মানত যদি তোমার খাঁটি দিলের হয়, যদি তুমি সহি নিয়তে, নির্ভীক মনে বিষুরির সামনে এসে দাঁড়াতে পারো তবে বিষহরি তোমাকে বিমুখ করবে না।
দক্ষিণ থেকে শন শন করে ছুটে আসছে গরম বাতাস। আশপাশের দশ গ্রামের মানুষের বিশ্বাস : জিন বলো আর দেবতা বলো সবই এই গরম বাতাসে ভর করে ছুটে আসে। এই গরম বাতাস গায়ে লাগতেই যদি ডরাইছো, তাইলে তুমি শেষ। তাই খেলা বুকটা পাষাণ করে সামনে তাকায় : চোখের মালুমে জনমানুষের কোনো কায়া নাই। চৌপাশে শুধু টলটলা পরিষ্কার পানি আর পানি। ডহরের মাঝখানটায় যেন নীল আসমানটা নেমে এসেছে এমনিধারা নীল! মাইল-তিনেক দক্ষিণে সেই বুড়ো হিজল গাছ দুইটা দুপুরের নির্জনতায় আপন ভাইয়ের মতো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তারা কতশত বছর ধরে যেন দাঁড়িয়ে আছে!
এই গাছ দুইটা আর বিষুরির থলিকে নিয়ে কত কথা, কত কাহিনি মানুষের মনে মনে, মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। বাড়ির আশপাশে পাগার-ডুবার পচা পানিতে যেমন হাজারে-বিজারে রোগজীবাণু লুকিয়ে থাকে তেমনি গ্রামের মানুষের মন-মগজে, রক্তে হাজার বছর ধরে লুকিয়ে আছে এইসব অন্ধবিশ্বাস। তাই গ্রামের বুড়ারা আজো বলে, একদিন এমন দিন ছিল যে বড় বড় বিয়ে কিংবা শিন্নি-সালাতের জন্য ওই হিজলতলায় এসে জোড়হাতে মিনতি করে বললে আপনাআপনি কাঁসা-পিতলের ডেক-ডেকচি, থালা-বাটি ডহর থেকে ঝনঝন করে উঠে আসত। তারপর ওইগুলা নিয়ে গিয়ে বিয়েশাদি, শিন্নি-সালাত শেষে ধুয়ে-মুছে আবার এনে ফিরিয়ে দাও। তো একবার ছ’আনি গ্রামের কছিমুদ্দি নামের এক বুড়া এইসব জিনিস নিয়ে আসার পর লোভের বশে আর ফিরিয়ে দিলো না। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই সব ডেক-ডেকচি তার ঘর থেকে ঝনঝন শব্দে বেরিয়ে আসে। তারপর তারা সারবেঁধে বিষুরির থলির দিকে নেমে যেতে থাকে। সাথে টেনে নিতে থাকে কছিমুদ্দি বুড়াকেও। বুড়া গলা ফাটিয়ে ডাকছে তার আপনজনদের, রোদন করে করে গেরামবাসীকে মিনতি করছে তাকে ধরে রাখার জন্য। কিন্তু ভয়ে কেউ এগিয়ে এল না। সবাই তফাতে দাঁড়িয়ে নির্বাক পুতুলের মতো বাসনকুসনের চলে যাওয়া, বুড়াকে টেনে নিয়ে যাওয়া দেখছে। দেখতে দেখতে কছিমুদ্দি ওই জোড়া হিজলের তলা দিয়ে নেমে গেল কালাই পাথারের গভীর ডহরে। কছিমুদ্দি কিন্তু আর ফিরে এল না। পরদিন সকালে সবাই গিয়ে দেখে : কছিমুদ্দির মাথার খুলি আর হাড়গুলা পড়ে আছে জোড়া হিজলের তলে, শরীরের সব মাংস-মজ্জা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে বিষুরির রাক্ষস গজার মাছেরা!
আসার সময় খেলার মা বারবার বলে দিয়েছে, — বিষুরির কাছে গ্যায়া ডরাইছ না বাজান। ‘ডরাইলে ডরে খা, না ডরাইলে কিচ্ছু না।’
তবু খেলার গতর শিরশির করে। এই ভাদ্দরের কাঠফাটা রোদ-গরমের মাঝে কেমন শীত শীত করে! প্রাণটা শামুকের মতো কুঁকড়ে আসতে চায়। মনে হয় কে যেন পেছনে দঁড়িয়ে তার ঘাড়ে গরম নিশ্বাস ফালছে! অথচ একটু আগেও সে রোদের তেজে ঘামছিল। খেলা আল্লার নামে বাঁশের খাঁচা থেকে কবুতর দুইটা বের করে। মনে মনে ‘বিষুরি! বিষুরি!’ বার-কয় জপে। চোখ বন্ধ করে বারবার মনে করতে চেষ্টা করে তার মায়ের দুঃখী দুঃখী মুখটা। তাবাদে অবলা জীব দুইটাকে সে বুকের কাছে চেপে ধরে আবার চোখ বন্ধ করে। এইবার মনে মনে তার মায়ের শিখিয়ে-দেওয়া কথাগুলাই পষ্ট করে বলতে থাকে, — ‘অগো বিষুরির জিন, আমার মায়ের মনের ইচ্ছা তুমি পূরণ কইরা দ্যাও, আমার মায়ের মনের বিষ তুমি দূর কৈরা দ্যাও।’
খেলা চোখ মেলে দেখে কবুতর দুইটা বিষুরির থলির উপর দিয়ে দক্ষিণমুখো উড়ে যাচ্ছে। তার মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। তার মায়ের মানত বিষহরি কবুল করেছে। তা না হলে কবুতর দুইটা ল্যাংড়া-লোলার মতন তার হাতেই রয়ে যেত অথবা দক্ষিণে উড়ে না গিয়ে যেত উত্তরে। তাবাদে খেলা আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ায় না। মাথা সোজা করে শাঁ শাঁ হাঁটতে থাকে। একহাঁটায় সে নির্জন মাঠটা পেরিয়ে মানু মিয়ার বিলপারের কান্দায় এসে দাঁড়ায়। মাইল-দেড়েক পথের মাঝে সে একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। মাথাটা একটুও নত করেনি। মাথা নোয়ালেই বিষহরি তার ঘাড়টা মট করে ভেঙে দেবে। পেছন ফিরে তাকালে মানত যাবে বিফলে।
মানু মিয়ার বিলপারের কান্দার পর থেকেই একটা-দুইটা করে ঘরবাড়ির শুরু। রুক্ষ কালো মাটির এলাকাটায় মাটির দেওয়ালের উপর তালপাতার ছানি দেওয়া ছোট ছোট ঘর। সারাটা অঞ্চলে একটা মানুষের কোনো সাড়া নাই। এদিকেই কাদু-কালু, অহাকালু আর মাগীকুদ্দুদের বাড়ি। এখন গলা ফাটিয়ে ডাকলেও কাউকে পাওয়া যাবে না। সবাই গেছে গিরস্তের বাড়ি কামে। মাগীকুদ্দুদের পাড়া পেরিয়ে কলুপাড়া। কলুরাও এখন গ্রামে গ্রামে তেল বেচতে গেছে। গোটা এলাকাটাই গরিবদরিব মানুষের বসত। এই চার-পাঁচপাড়ার মাঝে একমাত্র মানু মিয়াই দাপুটে চাষা। আর পশ্চিমে মড়লরা। কুতকুতা কালো, ন্যাংটা আর এ্যাবাড্যাবা চেহারার ছোট ছোট বাচ্চারা বিলপারের কাদা-পানিতে ডুবসাঁতার খেলছে। ছোট ছোট বাড়িগুলার কলাপাতার দেউড়ির ফাঁক দিয়ে রোগা রোগা মলিন গতরের মেয়েলোক দেখা যাচ্ছে। এইসব দেখতে দেখতে খেলা ঈদগাহের চাতাল পেরিয়ে সোজা আঙ্কুরের দোকানে ঢুকে।
দোকানে আঙ্কুর আর বিকাশবাবু মুখোমুখি বসে আলাপ করছে আর বিড়ি টানছে। খেলার পায়ের শব্দে দুইজনই মাথা তোলে। বিকাশ খেলাকে দেখে একটু মুচকি হাসে আর আঙ্কুর অবাক গলায় জানতে চায়, — তুই?
— হ। বিষুরির থলিত গেছলাম।
আঙ্কুর হা হা করে হেসে ওঠে, — মানুষ রকেট লইয়া চাঁদের দেশ থাইক্যা বেড়াইয়া আইছে আর তুই কৈতর লইয়া বেড়াইতে যাছস বিষুরির থলিত! কী কৈয়াম দুঃখের কতা?
বিকাশবাবুর মুচকি হাসিটা নিশব্দে আরেকটু চওড়া হয়। তাই দেখে খেলাও হাসে। প্রাণভরে হাসতে হাসতে খেলা আঙ্কুরের টু-ব্যান্ড রেডিয়োটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিকলাঙ্গ আঙ্কুর শিশুকালে ঘরে বসে বসে নোয়াখালির এক হুজুরের কাছে আলিফ, বা, তা, ছা-র সাথে অ, আ, ক, খ শিখেছিল। তারপর নিজের চেষ্টায় আর মনের কষ্টে অনেক কিছু শিখেছে। দোকান দেওয়ার পর যখন রেডিও কিনল তখন থেকেই যেন আঙ্কুরের মনটা পাল্টাতে থাকে। বদলে যেতে থাকে তার চিন্তা-চেতনা।
আঙ্কুর আর ঘাটুদলের পালা-মাস্টার বিকাশবাবু এই দোকানকোঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কীসব-যে আলাপ করে! সব অবাক অবাক কথা বলে। এই রেডিয়োর মারফত আঙ্কুর এখন অনেককিছু জানে। জানতে জানতেই একদিন গান লিখতে শুরু করে। আজ আঙ্কুর দশগ্রামের মধ্যে সেরা গাতক। এইখানেই শেষ না। এখন তার সাথে কথা বললে মনে হয় সে রীতিমতো স্কুল-কলেজে পড়ুয়া শিক্ষিত মানুষ। হয়তো এইসব গুণের জন্য, হয়তো ভালো বিচ্ছেদ লেখার জন্য কিংবা নিঃসঙ্গ-দুঃখী এই মানুষটাকে খেলা এমনি-এমনিই ভালোবাসে। বন্ধু ভাবে। তাই সে হাসতে হাসতেই কয়, — মা পাডাইছিন। বাদদে এইসব। অহন একটা বিড়ি দে।
আঙ্কুর আর বিকাশবাবু দুইজনই একটু সরে গিয়ে খেলাকে বসার জন্য জায়গা করে দেয়। আঙ্কুর খেলাকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে আরেকটা নতুন বিড়ি ধরিয়ে বলে, — নিজের খায়া নিজের ট্যাহায় আর কত পরের ডঙ্কা বাজাইবে?
এই কথায় খেলা গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর হয় বিকাশবাবুও। শিক্ষিত ও চিরকুমার বিকাশবাবু তার রাজনৈতিক মতাদর্শ ও প্রখর ব্যক্তিত্ব নিয়ে চুপচাপ বিড়ি টানতেই থাকে। খেলা একবার আঙ্কুরকে দেখে, একবার বিকাশবাবুকে দেখে। সে জানে আঙ্কুর কী বলতে চায়। তাই একটু ভেবেই বলে, — কী করাম ক? আর যা-ই করি, আমি ঘাডুদলের কর্তা অইতাম না।
— ক্যা?
— ঝামেলা আছে।
— কী ঝামেলা ?
— আছে…।
বলতে বলতে খেলা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।
বিকাশবাবু দোকানের ছোট্ট জানালা দিয়ে কালাই পাথারের দিকে তাকিয়ে ছিল। শেষ-হয়ে-আসা বিড়ির মোথাটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে খেলার দিকে মন দেয়, — এখন কী তোমার ঝামেলা কম ?
— খেলা হাসতে হাসতে বলে, অন্তত কর্তাগিরির ঝামেলা নাই।
— উত্তম কথা। কিন্তু এই ঘাটুদলটা কার?
প্রশ্নটা করে বিকাশবাবু খেলার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকে। খেলা একটুও না-ভেবে হাসিহাসি মুখেই বলে, — আমগর।
— আমগর মানে কার ?
— আমগর সবার।
— দলটা আমাদের সবার? ভালো কথা। কিন্তু দলের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলা কি সবার মত নিয়ে নেওয়া হয়?
এইবার খেলার মুখটা হা হয়ে যায়। সে বিকাশবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দেরি করছে দেখে আঙ্কুর বলে, — মাসে তিন ট্যাহা খরচ না কৈরাও মানু মিয়া দলের কর্তা। আর পরীর খরচ বাদেই দলের পিছনে তর মাসিক খরচ দশ ট্যাহা ছাড়ায়। তাবাদে ধর বছর শেষে মানু মিয়া দলের কোনো হিসাব দ্যায়?
— না।
— হিসাব চায়া কোনোদিন পাইছস?
— না।
— তাইলে ?
— তাইলে কী ?
এই কথা বলে আঙ্কুর বিড়ির ছাই ঝাড়ে। তার ফর্সা মুখটা বেশ লাল দেখায়। তাই সে মুখ নিচু করে খেলাকে বলে, — বাড়িত গ্যায়া তুই নিজেই ভাবিছ। ঘোড়ামোবারকের মতন দুই-তিনজন চোর-ডাকাইত ছাড়া দলের সবাই তরে পছন্দ করে, মাইন্য করে, মন থাইক্যা ভালোওবাসে। বিপদে-আপদে সবার আগে তুই-ই দলের গরিবদরিবের ভরসা। কিন্তু দলের যে-কোনো বিষয়ে মানু মিয়ার কথাই শেষ কথা। এইসব ভাববার জিনিস। বুঝবার জিনিস। বুইঝ্যা দ্যাখ : মানুষও তর ট্যাহাও তর। মইধ্যে থাইক্যা মানু মিয়ার মতন একটা লুচ্চা, গরিবের রক্তচোষা জোঁক, দেশবিরোধী মুসলিমলীগের পা-চাটা কুত্তা দলের কর্তা হইয়া গেরামের নিরীহ মাইনশের মাথার উফরে লাঠি ঘোরায়। ভাবিছ…আমার কতাডা একটু ভাবিছ…।
খেলা এইসব বহুবার ভেবেছে। কিন্তু গা করে না। সে ফুর্তিবাজ। পেছনের দিনগুলা আমোদ-ফুর্তিতেই কাটিয়েছে। বুড়া বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান এবং অর্থসামর্থ্যও যথেষ্ট থাকায় ফুর্তি বাবদ খরচটাও সহজেই যোগাড় হয়ে যায়। তাই বলে সে বোকা কিংবা অবুঝও না। মানু মিয়ার মতো গ্রামের যারা খেলাকে পাগল কিংবা হুজুগে বলে রায় দিয়ে দেয় তারাও শতভাগ সঠিক না।
দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে বিকাশ উঠে পড়ে। খেলাও ওঠে। বাড়িতে তার মা নিশ্চয়ই তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। তাই আর দেরি করা ঠিক না। দুইজন হাঁটতে হাঁটতে কলুপাড়া পেরিয়ে বড় সড়কের জামতলার ছায়ায় এসে দাঁড়ায়। বিকাশ যাবে সোজা দক্ষিণে আর খেলা যাবে পশ্চিমের ছোট সড়ক ধরে। বিকাশ একবার আড় চোখে খেলার দিকে তাকিয়ে তার কাঁধে একটা হাত রাখে, — বুঝলা খেলা, ঘাটুদলের নামে মানু মিয়া আমাদের সবাইকে তার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। দলের শিল্পী, কলাকুশলী সহ সবাইকে সে তার গ্রাম্য মাতব্বরির ঘুটি হিসাবে, দরকার মতো লাঠি হিসাবে ব্যবহার করছে। দশ বছর ত করল। আর কত? তুমি তরুণ, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং দরদি মানুষ। নেতা হওয়ার সবগুলা গুণ তোমার মাঝে আছে। ক্ষমতাবান নেতা যদি অসৎ হয় তাহলে সর্বনাশ ছাড়া সমাজকে সে কী দিতে পারে? তোমার এইসব বুঝবার কথা, ভাববার কথা। দলের কোনো বিষয়েই আমাদের কারো মতামতের দুইআনা দাম নাই। একটা টু শব্দ করলে মানু মিয়া চোখ লাল করে তাকিয়ে থাকে। কর্তাগিরির নামে আজ মানু মিয়া দলের সবার গলা টিপে ধরে স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। মাগীকুদ্দু, অহাকালু, কাদু-কালুরা গরিব মানুষ। তুমি তো অর্থবিত্তেও মানু মিয়ার চে কোনো অংশে কম না। দলের পিছনে খরচও করছ দু-হাতে। কাজেই এইসব বিষয়ে তোমার কিছু ভাবা উচিত।
— কিন্তু…।
কিন্তু বলে খেলা বিকাশবাবুর দিকে তাকায়। বিকাশ আস্তে করে গলা খাকারি দিয়ে বলে, — আমি দল ভেঙে দেবার কথা বলছি না। কিংবা তুমি নতুন আরেকটা দল গঠন করতেও বলছি না। আমি শুধু দলনেতার বদল চাইছি।
খেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার বাড়ির দিকের পথে পা বাড়ায়। বিকাশও তার নিজের পথে হাঁটতে শুরু করে।
বাড়ির সামনে আমগাছের ছায় খেলার মা ছেলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বারবার মায়ের গতরের লোমগুলা শিরশির করে দাঁড়িয়ে উঠছে। মনে একটা আতঙ্ক, খেলা যদি ভয় পায়, মনের ভুলে যদি পিছন ফিরে তাকায়! তার পরানজুড়ানো ছেলের যদি কিছু হয়! তাবাদে মায়ের এই বুক-কাঁপানো অবস্থার মাঝেই একে একে মনে পড়ে তার সবগুলা মরা সন্তানের মুখ। সবচে বড়টা ছিল মেয়ে। চোখ দুইটা ছিল অবিকল তার নানার মতো। মেয়েটার নাম রেখেছিল আয়েশা বেগম। তিন বছর বয়সের সময় আয়েশাকে রক্ত-আমাশয়ে ধরেছিল। যাদু আর বিছানা থেকে ওঠেনি। লবণের পোটলার মতো বিছানায় পড়ে পড়ে মেয়েটা খালি চাকা চাকা রক্ত হাগতো। তার ঘরের মানুষটা দুনিয়ার যত কবিরাজ ডেকে এনেও কিছু করতে পারেনি। সাতদিনের দিন সব শেষ হয়ে গেল। এই রকম নানান উছিলায় আল্লা তাকে সাতটা সন্তান দিয়েও নিয়ে গেছে। সব হারানোর পর তার শূন্য বুক আলো করে আসে খেলা। আয়েশার বাপ ছেলের মুখ দেখে উপরের দিকে আঙুল ইশারা করে বলেছিল, — সব বিধাতার খেলা…, তাই আমিও আমার পুতের নাম রাখলাম খেলা।
খেলার মা বাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে উত্তরের দিকে তাকিয়েছিল। যেখানে সুতিয়া নদী পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে, ঠিক তার উত্তর পাড়ের কবরখানায় ঘুমিয়ে আছে তার সোনামানিকেরা। সেখানে বড় একটা বটগাছ। তার নিচে ছোট ছোট কবরের সারি। কবরের উপর সারাদিন বটগাছের ছায়া থাকে। রাতে জোনাকপোকারা বাতি জ্বালিয়ে মেলা জমায়। খেলার মা নিজের বুকে হাত রাখে। এখানে সে সব-কটা সন্তানের তালাশ পায়। তার ডান বুকে আছে একলা খেলা। আর বাম বুকে সব-কটা মরা সন্তান। এখনও সে আলাপের মাঝে হঠাৎ হঠাৎ বলে ফেলে, — আমার বড় মেয়ে আয়েশা থাকলে অহন আমি নাতি কোলে লইয়া পাড়া বেড়াইতাম।
খেলার মা উত্তর থেকে পুবে তাকায়। বাড়িতে আসার পথটা যেখানে বাঁক নিয়ে বাঁশঝাড়ের আড়ালে পড়েছে সেখানে চোখের নজর গেঁথে রাখে। একটা সন্তান দশমাস দশদিন পেটে ধরা, তাকে জন্ম দেওয়া, লালন-পালন করে মানুষ করে তোলায় মায়ের বুকের এক কলস রক্ত পানি করার সমান, দুনিয়ার ইতিহাসের সমান লম্বা তার সুখ-দুঃখ-বেদনার কাহিনি। এক মা ছাড়া এই বেদন কে বোঝে? কে বুঝতে পারবে মায়ের বুকের আমোদ-আল্লাদ, হাহাকার! সেই সন্তান যখন যোগ্য হয়েও মায়ের বুকের বেদন বোঝে না তখন আল্লা ছাড়া তার কে আছে নিগাবান? তাই তো খেলার মনমতি ঘরমুখু করার জন্য তার মা জোড়া খাসি দিয়ে মসজিদে সিন্নি দিয়েছে। সিন্নি পাঠিয়েছে মিসকিন সাহেবের মাজারে এবং আজ আবার জোড়া কৈতর দিয়ে খেলাকে পাঠিয়েছে বিষুরির থলিতে। রোজ রোজ ফজরের নামাজের পর কোরআন পড়ে খোদার দরবারে হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে মা চোখে ঘা করে ফেলেছে। তবু যদি খোদার দয়া হয়। হায় বিধাতা তুমি ছাড়া আমার কে আছে! কে আছে এই অভাগীর?
এইসব ভাবতে ভাবতে মা চোখ মোছে।
খেলার মায়ের অপেক্ষাটা আস্তে আস্তে তার মনে একটা আশা হয়ে জেগে ওঠে। বিষুরির কাছে তার একটাই চাওয়া, তার খেলা যেন ঘাটু ছেড়ে বিয়ে করে সংসারী হয়। আসছে জৈষ্ঠ্য মাসে তার ছেলের বয়স হবে আঠাশ। খেলার সমবয়সীরা এখন তিন-চারটা সন্তানের বাপ। আর খেলা…। খেলার মা একবার পথ দেখে তো আরেকবার সুরুজ দেখে। অনুমান করতে চেষ্টা করে, খেলার কী খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে?
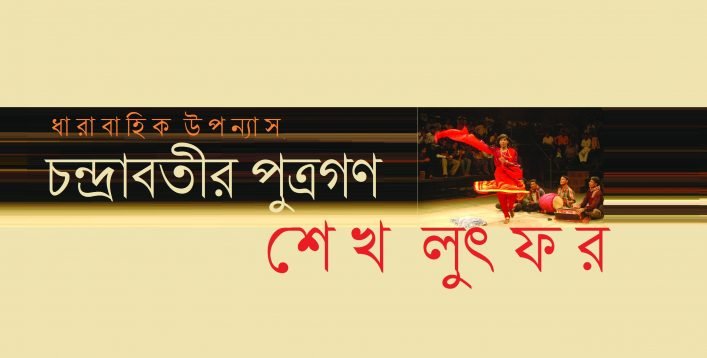
চন্দ্রাবতীর পুত্রগণ : আগের পর্ব
শেখ লুৎফর রচনারাশি
- চন্দ্রাবতীর পুত্রগণ ৯ || শেখ লুৎফর - July 8, 2022
- চন্দ্রাবতীর পুত্রগণ :: পর্ব ৮ || শেখ লুৎফর - November 20, 2021
- চন্দ্রাবতীর পুত্রগণ :: পর্ব ৭ || শেখ লুৎফর - October 30, 2021


COMMENTS