প্রাককথন অথবা কৈফিয়ত
লাইন থেকে ছিটকে পড়া রেলগাড়ির মতো হঠাৎ ‘ইসলামবীক্ষণ’-এর অবতারণা কেন সে-কৈফিয়ত টানতে যেয়ে ‘গানপার’-এ প্রকাশিত ‘রবিকবির পরব্রহ্ম’ শীর্ষক ছয় পর্বের রচনাটির কথা অগত্যা স্মরণ করতে হচ্ছে। ফার্নান্দো পেসোয়া পাঠের মুহূর্তে রবিকে কেন মনে পড়েছিল তার সদুত্তর তখন খুঁজে পাইনি! ঠিক যেমন রবিকে নিয়ে ধান ভানতে বসে ইসলাম প্রসঙ্গের অবতারণা নিছক কাকতালীয় ঘটনা কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারিনি। এ হয়তো পাঠপ্রক্রিয়ার রহস্য যা একজন রচয়িতাকে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে তাড়া করে ফিরে! সে যা-ই হোক, ‘রবিকবির পরব্রহ্ম’ ‘গানপার’ ছেপেছেন ভালো কথা, কিন্তু দুঃসহ পাঠ-সীমাবদ্ধতা ও ভাবনার দীনতা দোষে রচনাটি পরিণত উপসংহার পায়নি বলেই মনে হচ্ছে। রবিকবি নিয়ে লিখতে গিয়ে যদি এই দশা হয় সেখানে ইসলামের অতিকায় জগতে গমন কতটা সঠিক হলো জানি না! প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য ও জটিলতার সঙ্গে ইসলাম নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষে বহমান স্পর্শকাতর সব বাদানুবাদ বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও এই রচনাখ্যান অনুরূপ দশায় উপনীত হতে যাচ্ছে কি না ভেবে অস্বস্তি হচ্ছে খুব!
রবির কথা যদি ধরি, তাঁকে নিয়ে লেখার বিপদ ছিল এই লোকের মনের গড়ন সারাজীবন বিশেষ পালটায়নি অথবা সময়ের চাপে যতখানি পালটেছে সেখানে এমন চোরাবালি রয়েছে একবার পা দিলে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়ে। তরুণ বয়সে যে-চোখ দিয়ে তাঁকে দেখেছি আর এখন যেভাবে দেখি দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও রবিপাঠ ও পুনর্পাঠ মোটের ওপর একপেশে হতে বাধ্য এবং নতুন করে ফিরে তাকানোর ক্ষণে সেটা টেরও পেয়েছি। বিরল পাঠক যদি ধৈর্য ধরে রচনাটি শেষ অবধি পাঠ গিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে পাঠ অন্তে তাঁর মেজাজ খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়। আবাল্য সহজ জলযানের মতো তাঁর কবিতায় ভ্রমণ করেছি, গানের সুরেলা আবেশে শ্রবণ করেছি, গল্প-আখ্যান-নাটকে বিচরণ করতে দেখেছি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ-বক্তৃতা ও দিস্তা-দিস্তা চিঠিপত্রে চোখ রাখার সময় তাঁর সঙ্গে নিজের সংযোগ টের পেয়েছি, দেশ-বিদেশের গুণীজনরা তাঁকে যেভাবে পাঠ করেন বলে জেনেছি, অর্থাৎ সকল স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝে ভ্রামণিক হয়ে রবি সম্পর্কে কথা বলা যুক্তিসংগত মনে হয়েছিল। ব্যক্তিগত অনুভবকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু গোঁজামিল অগত্যা থেকেই গেছে। অবশ্য এর জন্য মনে অনুতাপ নেই। চারপাশে অজস্র বনসাইয়ের ভিড়ে রবিবৃক্ষকে নজর করতে পারা আনন্দের এবং সে-আনন্দ উপভোগে বাধার কারণ দেখি না। ইসলাম নিয়েও একই কথা বলতে চাই, এই রচনাখ্যান নিছক একজন ব্যক্তির নিজস্ব পাঠ প্রতিক্রিয়া ও অনুভবের রসায়ন এবং কাউকে অযথা আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য থেকে বিরচিত নয়।
মোদ্দা কথা ভক্তি অথবা প্রত্যাখ্যানের পরিবর্তে সদা সচল পাঠ-মেরামত ব্যাখ্যার যে-দিগন্ত উন্মোচিত করায় একজন আলোচক বা অনুসন্ধানীর জন্য সেটা হলো লাভের দিক। ইসলাম নিয়ে কাহানি ফাঁদার এ হয়তো কারণ! দ্বিতীয় কারণের কথা বলতে গেলে মিশরদেশি লেখক ড. তাহা হোসেইনের নাম নিতে হয়। আরববিশ্বে ‘আরবি সাহিত্যের ডিন’ বলে পরিচিত এই লেখক সম্পর্কে সম্প্রতি ইন্টারনেটে খোঁজখবর করতে গিয়ে পাঠ-মেরামত বিষয়টি আরও জোরদার হয়েছিল বলা যায়। ইসলাম নিয়ে লিখতে বসে টের পেলাম এতদিন একরৈখিক পঠন-পাঠন আর ধারণার মধ্যে বিরাজিত থেকে কোরান, মোহাম্মদ ও ইসলামকে নিজের ‘আকল’-এ ছকে নিয়েছিলাম! এখন দেখতে পাচ্ছি সেখানে অসংগতি যেমন ছিল, ক্ষেত্রবিশেষে সুবেদী হওয়ার পরিবর্তে অসহিষ্ণুও ছিলাম ব্যাপক! প্রচলিত ভক্তি অথবা বিদ্বেষের বাইরে গিয়ে বিরচিত এই রচনাখ্যান তাই বিবেচক হওয়ার পয়গাম নিয়ে হাজির হওয়ায় ‘গানপার’-এ পাঠাতে আর দ্বিধা থাকেনি।
ইসলামের মতো জটিল বিষয়ে লেখার সুবাদে অনেক কিছু নতুন করে ভাবতে পেরেছি, স্ববিরোধিতার জায়গাগুলো পরখ করা গিয়েছিল, নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আর বোঝাপড়াও কমবেশি ঘটেছে, এসব কারণে তথাকথিত প্রগতিপন্থী অবস্থানের সঙ্গে গাদ্দারি করছি এই অভিযোগ পরিচিতজন তুলবেন জেনেও পিছপা হইনি। স্বীকার করা প্রয়োজন, লম্বা এই সফরের পেছনে ড. তাহা হোসেইন ভূমিকা রাখলেও ‘জাহিলিয়া বা অন্ধকার যুগ’র কবিতার উৎস সন্ধান করতে যেয়ে তাঁর নেতিবাচক ইসলামবীক্ষণ মনে জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু বিস্তারিত পঠন-পাঠনের আগে অধিক বলাটা সমীচীন ভাবিনি। সেইসঙ্গে বিবেচনায় রেখেছি, ইসলামের সমালোচনা করলেও তাঁর পাঠপদ্ধতি সেখানে অবিবেচনাপ্রসূত মনে হয়নি, যা এক্ষেত্রে আজকাল সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বাঁধাধরা ছক থেকে বেরিয়ে নতুন পাঠে প্রেরণা দান করায় তাঁকে বরং এই ফাঁকে কুর্নিশ জানানো জরুরি মনে করি।
অগত্যা এ-কথা বলাই যায়, ইসলাম-পূর্ব অন্ধকার যুগের কবিতা সম্পর্কে নিজের অনুসন্ধান শেষে স্পর্শকাতর যে-তর্কের সূত্রপাত ড. তাহা ঘটিয়েছিলেন তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বক্ষ্যমাণ রচনার উদ্ভব। যদিও ড. তাহা ও তাঁর সাহিত্যকৃতির আলোচনা একাধিক প্রবাহে বিন্যাস্ত এই রচনার মূল উদ্দেশ্য নয় এবং সেটা বিরল কোনও পাঠক সুদীর্ঘ এই যাত্রায় সঙ্গী হলে নিজেই বুঝে যাবেন। আলোচনার পরিধি বিবেচনায় তিনি হচ্ছেন পার্শ্বচরিত্র এবং অত্র রচনায় তাঁর আগমন ও প্রস্থান সেভাবেই ঘটেছে। ইসলামবীক্ষণে ডুব দেওয়ার জন্য একটি সূত্রমুখ প্রয়োজন ছিল এবং তিনি সেটা পূরণ করছেন দেখে যাত্রার শুরুটা তাঁকে দিয়ে ঘটানো সঠিক মনে হয়েছে। রচনার সামগ্রিক বিষয়বস্তু যেন পাঠকের বোধগম্য হয় সে-জন্য শুরুতে এর প্রবাহবিন্যাস দু-কথায় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি : —
‘ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা’ শীর্ষক এই রচনালেখ্য সাতটি প্রবাহ বা অংশে ভাগ হয়ে বিস্তৃত হয়েছে। প্রথম প্রবাহ ইসলাম-পূর্ব আরবের কবিতা নিয়ে ড. তাহা হোসেইনের ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও আরব মানসচেতনায় ইসলামি সংস্কৃতির অভিঘাত সংক্রান্ত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। কোরানে বর্ণিত ফিতরাত বা স্রষ্টার একত্বের ওপর সহজাত ইমান নিয়ে ধরায় আগত মানবকে মুসলমানের স্মারক গণ্যকারী আকিদা এবং তার সঙ্গে অন্য আকিদার দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ সেই সূত্রে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে। জ্ঞানের গভীরতা-অগভীরতা বিচারে কোরান কেন একটি প্রসঙ্গমূলক টেক্সট (Referential Text) তার ইশারা পাঠক পাবেন দ্বিতীয় প্রবাহের আলোচনায় এবং পরবর্তী প্রবাহ সমূহে গমনের পর বিষয়টি ক্রমশ তাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে ধরা দেবে মনে করি। তিনটি ভাগে বিন্যাস্ত তৃতীয় প্রবাহ আল্লাহর সিফাত বা মৌল গুণাবলির খবর করতে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ অর্থাৎ তাসাউফে গমনের চেষ্টা করেছে। বঙ্গ তথা উপমহাদেশে সুফিভাবিক বাউল ও মরমি ধারায় চর্চিত স্রষ্টার ভেদবিচার সংক্রান্ত আধ্যাত্মবাদ আর কোরান ও বিশ্বজনীন সুফি ভাবধারায় ব্যক্ত আধ্যাত্মবাদ কেন এক বিষয় ‘নহে’ সে-প্রসঙ্গটি সংগত কারণে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে।
রাষ্ট্র প্রণোদিত সমাজিক জীবনধারায় অভ্যস্ত জনগণের ইসলাম অনুশীলনের হালত ও খাসলত আর ‘ইমান, মুমিন ও মুনাফিক’-এর সংজ্ঞা স্থির করে যে-ইসলাম, উভয়ের প্রভেদ ও দ্বন্দ্ব বিষয়ে তির্যক কিছু কথাবার্তা চতুর্থ প্রবাহের চরিত্র স্থির করে দিয়েছে। ব্যক্তি মোহাম্মদের বৈষিয়ক জীবনধারায় সংঘটিত ঘটনার নিরিখে তাঁর মনোজগতের গড়ন বুঝে নেওয়ার প্রয়াস এই পর্বের গতিবিধি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে। দুই কিস্তি জুড়ে প্রবাহিত পঞ্চম প্রবাহে কোরান ও ইসলামি টেক্সটের তরজমা বিষয়ে জরুরি আলোচনা পাঠের জন্য পাঠকের প্রতি সবিশেষ অনুরোধ থাকবে। সেইসঙ্গে হারাম-হালাল নিয়ে মুমিন মুসলমানের দিগদারি ও ইসলাম সমালোচকদের টিটকারিকে এক সূত্রে গেঁথে একটি রূপরেখা তুলে ধরা ও উপসংহারে পৌঁছানোর উপক্রম আশা করি তাঁরা নজর করবেন। ষষ্ঠ প্রবাহ মূলত ইসলামের গতিপ্রকৃতি ও সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনার খোঁজখবর করেছে এবং সেই সুবাদে মধ্যপন্থী ইসলামের প্রাসঙ্গিকতা যাচাইয়ের চেষ্টাও করা হয়েছে। মোট ছয়টি প্রবাহে বিস্তৃত সপ্তম প্রবাহকে এ-পর্যন্ত উত্থাপিত সকল প্রসঙ্গের ঐকতান বলা যেতে পারে। চরমপন্থী ইসলামের উত্থানের নেপথ্য কার্যকারণ অনুসন্ধান এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামকে প্রত্যাখ্যানে মরিয়া অ্যান্টি-ইসলামিস্ট বাকোয়াজি ও এই ঘরানায় অবস্থিত প্রাক্তন মুসলমানদের (ex-Muslims) বুদ্ধিবৃত্তিক ফটকাবাজি নিয়ে বিস্তারিত বয়ান পাঠক একবার হলেও বিবেচনায় নেবেন আশা করি।
তো মোটের ওপর এই হচ্ছে ভিত্তি; এছাড়াও সমগ্র রচনালেখ্যের ফাঁকফোকর দিয়ে যেসব অনুষঙ্গ চুঁইয়ে পড়েছে সেগুলো পাঠকের দিমাগে যদি টোকা দিয়ে যায়, সেটা এই রচনার পরম প্রাপ্তি বলে ধরে নেবো। মূল আলোচনায় গমনের আগে কবুল করা প্রয়োজন, ইসলামের বিচিত্রগামী অতিকায় জগৎ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় তথ্য ও ব্যাখ্যাগত ভুলভ্রান্তি থাকা বিচিত্র নয়। সহৃদয় পাঠক যদি ভ্রান্তি নিরসনে দু-কলম লিখেন তাহলে ভ্রম সংশোধনের অবকাশ জোটে। বিস্তারে গমনের ক্ষণে অগত্যা মনে রাখতে চাই, ইসলাম ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মাঝে বেড়ে ওঠা এক সাধারণ ব্যক্তির মনে জন্ম নেওয়া কৌতূহল মিটানোর তাগিদ আর নিজের বোধ-বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে উত্তর খোঁজার প্রয়াস ব্যতীত এই রচনার দ্বিতীয় কোনও উদ্দেশ্য তখনও ছিল না এবং এখনও নেই। লেখাটির সঞ্চালক ‘গানপার’ কর্তৃপক্ষ ও পাঠকরা আশা করি এটা বিবেচনায় নেবেন।
আলোচনায় উত্থাপিত প্রসঙ্গের খণ্ডিত ও প্রক্ষিপ্ত পাঠে ব্যক্তি-অনুভূতি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা করি বলে সমগ্র রচনাটি পাঠ করার জন্য পাঠকের প্রতি সবিনয় অনুরোধ থাকবে। দয়া করে বিচ্ছিন্ন প্রবাহ বা অংশ অথবা অনুচ্ছেদ পাঠ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না। কোনও শব্দ, বাক্য অথবা অনুচ্ছেদ যদি অনুভূতি ক্ষুণ্নকারী মনে হয় সেক্ষেত্রে সর্বাগ্রে সমগ্র রচনার সঙ্গে তার যোগসূত্র উপলব্ধির জন্য বিনীত অনুরোধ করি। লেখাটি Polemic বা বিতর্কমূলক পদ্ধতির আশ্রয়ে রচিত হওয়ার কারণে এত কথা বলতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে এই রচনায় ব্যক্ত ভাবনা, ব্যাখ্যা, মতামত এবং ব্যবহৃত তথ্যের উৎস ইত্যাদির দায়ভার রচয়িতা তার নিজ স্কন্ধে বহন ও স্বীকার করছেন।
এই সুযোগে বলে রাখি, কৃতজ্ঞ থাকব বিরল সেই পাঠকের প্রতি যিনি ধৈর্য ধরে রচনাটি শুরু থেকে শেষ অবধি ধারাবাহিক পাঠ যাবেন এবং এর দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল তোলার তাগিদে গাঠনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন, যেন নিজের সীমাবদ্ধতা শুধরে নিয়ে নতুন করে ভাবার বল পাই মনে। গৌরচন্দ্রিকায় আপাতত এ-কথাগুলো বলার ছিল, এখন সেখানে দাঁড়ি টেনে মূল প্রসঙ্গে গমনের সময় হয়েছে।
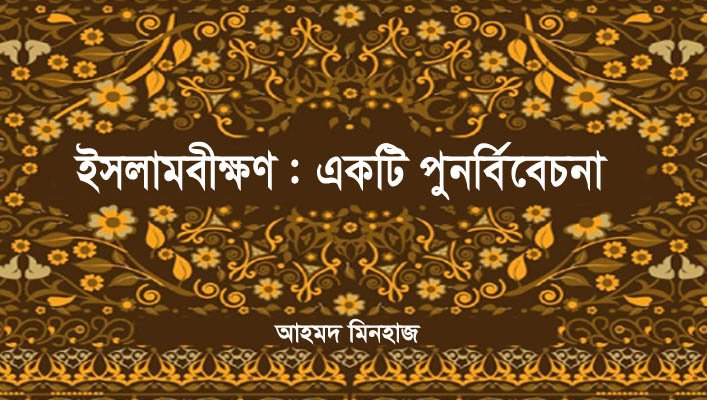
প্রথম প্রবাহ : অন্ধকার যুগের কবিতা এবং অন্ধ ‘তাহা’-র কোরান পাঠ ও চিহ্নবিহীন টেক্সট
মিশরের প্রত্যন্ত গ্রামে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ড. তাহা হোসেইন দীর্ঘ আয়ুর অধিকারী ছিলেন বলে ইতিহাসে লেখে। লম্বা জীবন পেলেও যে-ভবসংসারে একদিন তাঁর আগমন ঘটেছিল তাকে নয়ন ভরে দেখার সুযোগ কপালে জোটেনি। হাতুড়ে বদ্যির ভুল চিকিৎসায় দুই বছর বয়সে চোখের জ্যোতি হারানোর পর বাকি জীবন সেটা আর ফেরত পাননি। অগত্যা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি জীবনের অন্তে পৌঁছে যে-কাণ্ড ঘটায় ড. তাহা সেটা প্রারম্ভে ঘটাতে বাধ্য ছিলেন! মানব-সংসারের রঙ্গতামাশা আশ মিটিয়ে দেখার পর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একসময় সেই তামাশা অনুভবের বোধ হারিয়ে ফেলে এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আন্ধা সাজার ভান-ভণিতায় জীবনের বাকি দিনগুলো পার করে। তার হয়তো মনে হয় এতদিন যা দেখেছে এর কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সেটার থই পাওয়া কঠিন! অগত্যা চোখ বুজে আন্ধা সাজার ভান করাই শ্রেয়, কেননা এতে আর কিছু না হোক সংসাররঙ্গ দর্শনের দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই মিলে।
তো এই ভান-ভণিতার চক্করে রূপময় যে-জগৎ চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিজের ভিতরে টের পায় সেটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডোবানো হলেও সেখানে বসে আলো ঝলমল সংসারকে দূর থেকে নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিবেচনা করার অনুভূতিটা হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই সময় পরিপক্ক হয়েছে টের পেলে চোখ বুজে আন্ধা সাজে এবং মনের চোখ দিয়ে জগতের সঙ্গে নিজের কারবার সারতে থাকে! কে বলতে পারে বোর্হেস হয়তো এহেন পরিপক্ক বয়সে পৌঁছানোর পর ‘আর কিছু দেখার প্রয়োজন নেই, অনুভব করলেই চলবে’ এমতো ভাবনা থেকে চোখ বোজা শুরু করেছিলেন কি না! জগদীশ্বর বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন এই লোক পেকে ঝুনা নারিকেলে পরিণত হয়েছে। অগত্যা নিজের গ্রোগ্রামিংয়ে তিনি পরিবর্তন ঘটালেন। অতঃপর একদিন চোখ বোজা অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠার পর বোর্হেস বুঝতে পারেন চোখের পাতা খোলা রাখা ও না-রাখায় এখন আর কিছু যায় আসে না; অবশেষে তিনি গোলকধাঁধায় ঢুকতে পেরেছেন, যা অন্ধকারে ডোবানো হলেও জীবনের চিরায়ত সত্য সেখানেই অবস্থান করে! তাহা-র সুবিধা ছিল জীবনের শুরুতে চোখের জ্যোতি নিভে যাওয়ার কারণে তাঁকে এইসব কাণ্ডকীর্তির ভিতর দিয়ে কভু যেতে হয়নি। ধরায় পাঠানোর সময় আল্লাহ তাঁর কানে মন্ত্রটা বলে দিয়েছিলেন, ‘নিজেকে অন্ধ ভেবে হাহুতাশ করার প্রয়োজন নেই। অন্ধত্ব অতুল অনুভবশক্তি ব্যক্তিকে দান করে এবং ধরায় গমনের পর তুমি সেটা ব্যবহারের চেষ্টা করো। যদি সফল হও তাহলে চক্ষুষ্মান হওয়া সত্ত্বেও লোকে যা দেখতে পায় না তুমি সেটা ঠিক দেখতে পাবে।’
জগতের প্রোগ্রামার অর্থাৎ খোদার নির্দেশ ড. তাহা প্রতি অক্ষরে পালন করেছিলেন সে-ব্যাপারে এখন আর সন্দেহের কারণ নেই। মানব-সংসারে চোখের জ্যোতি না থাকা প্রতিবন্ধকতা গণ্য হলেও স্পর্শের মধ্য দিয়ে অন্ধ লোকের চেতনায় অতুল অনুভবশক্তি জন্ম নিয়ে থাকে এবং সবকিছু দেখার ক্ষমতা তাকে দান করে, যদিও ‘আকল বা ধীশক্তি’-র দোষে সবাই সেটা কাজে লাগাতে পারে না। জগতে এহেন অন্ধ লোকের সংখ্যাই অধিক যারা তীব্র স্পর্শানুভূতি ও অনুভবশক্তির জনক হওয়া সত্ত্বেও ‘আকল’ দোষে অসহায় আর পরনির্ভর জীব রূপে দুঃসহ জীবন কাটায়! একজন বেটোফেন বা তাহা-র সঙ্গে তাদের তফাত ঘটে যায়। স্পর্শানুভূতি হতে জন্ম নেওয়া অনুভব ও ধীশক্তি পরিবেশ-পরিস্থিতির ফেরে সকলে সমানভাবে ব্যবহার করতে পারে না। এর জন্য সাংঘাতিক মনের জোর ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োজন হয় এবং ড. তাহা অন্তরে শক্তিটা ধারণ করায় দৃষ্টিশক্তির বিকলাঙ্গতা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন, অধ্যাপনা ও গবেষণা, আরবি-ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় বুৎপত্তি ছাড়াও মিশর তথা আরব মহাদেশের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী হওয়ার সকল কার্য ভদ্রলোক সম্পন্ন করেছিলেন! গবেষণা ও সমালোচনা সাহিত্য তো রয়েছেই, উপন্যাস আর আত্মজীবনী রচনায় নিজের দাপটের ছাপ রেখেছিলেন তিনি।
আধুনিক মিশরীয় সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় ড. তাহা হোসেইন পশ্চিম গোলার্ধে ফলবান জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। নিজ দেশে ইসলামি ও আরব জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা স্থাপনের পরিবর্তে ইউরোপ-আমেরিকার ধাঁচে গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ্যেই ব্যক্ত করতেন। মিশরে প্রচলিত ইসলাম ও আরব ভ্রাতৃত্বের জিগিরে প্রকম্পিত জাতীয়তাবাদের ধারায় তিনি ছিলেন ঝড়ের নিশান! ইসলামকে রক্তে বহন করলেও ইসলাম-পূর্ব মিশরের অতুলনীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আত্মিক সংযুক্তি ছিন্ন করতে তিনি কেন অপারগ সে-কথা জানিয়ে দিতে অগত্যা কোনও দ্বিধা ছিল না মনে। একজন আরব মুসলমান রূপে পরিচিতি পাওয়ার চাইতে আপাদশির মিশরীয় পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার দিকে তাঁর ঝোঁক ও পক্ষপাত বেশ প্রবল ছিল। নবি মোহাম্মদের সুবাদে প্রাপ্ত ইসলামি ঐতিহ্যকে তিনি রক্তে অনুভব করেন বলে স্বীকার গেলেও ফেরাউন ঐতিহ্য থেকে প্রাপ্ত কুফরি সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বাস্তবতা উপেক্ষার প্রশ্ন উঠলে আপত্তি ঠুকে বসতেন। ডুয়াল স্ট্যান্স বা দ্বৈতাবস্থায় জারি থাকার এই প্রবণতা থেকে সহজে অনুমেয় ড. তাহা কেন সেই সময় মিশর তথা আরববিশ্বের বিদ্বান মহলে ঝড় হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
নেট ঘেঁটে যেটুকু খবর করতে পেরেছি তাতে একরৈখিক মানুষটি ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী ছিলেন বলেই মনে হয়েছে। ইসলামি ছকে বিন্যস্ত আরব জাতীয়তাবাদের বিপরীত স্রোতে দাঁড়িয়ে ইসলাম-পূর্ব মিশর ও অধুনা পশ্চিমপারে বিরাজিত সভ্যতার জ্ঞানপ্রকল্পে শরিক ড. তাহা ছিলেন দূরগামী উট। বিংশ শতকের কুড়ির দশকে তাঁর প্রভাবের সূচনা ঘটে এবং পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে সেই উটরূপে নিজেকে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাঁর ওপর সওয়ার না হয়ে উপায় থাকে না। নাগিব মাহফুজ থেকে শুরু করে আরববিশ্বের পুঁচকে লেখক তাহা-য় প্রভাবিত হওয়ার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন। আরব কবি-লেখকদের কাছে একজন তওফিক আল-হাকিম বা তাহা হোসেইনের আবেদনটি সম্ভবত এখানে নিহিত। আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের প্রফেসর সাদিক এম গওহর যেমন তাঁর গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন : —
Taha Hussein points out that Arab culture is not only Islamic but also has its deep roots in the Mediterranean civilizations of the Greeks and the Phoenicians (Baroot 1990: 254). Through cultural entanglements with western civilization, the Arab world, according to Hussein, would rediscover itself by restoring what the Arabs had given to the West during the golden era of Islamic civilization.—Source: Modernist Arabic Literature and the Clash of Civilizations Discourse by Saddik M. Gouhar; Research_Gate.net.
স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাত (The Clash of Civilizations) নামে খ্যাত টেক্সটের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়ার বাসনায় প্রণীত গবেষণাপত্রে গওহর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, পশ্চিম ও আরব সভ্যতায় বিদ্যমান ঠোকাঠুকির ফলশ্রুতিতে আরব বিশ্বের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার শঙ্কা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মিথ্যে না হলেও পুরোটা সত্য নয়। যেমন সত্য নয় হান্টিংটনের ব্যাখ্যায় প্রভাবিত সিরিয়ার নাগরিক কবি আলী আহমদ সাইদ ওরফে অ্যাদোনিস-র এই নৈরাশ্য : —
পুবের দুনিয়া যেন অবোধ শিশু
সাহায্য মাগে, কান্দে আর ফোঁপায়
পশ্চিমকে নিজের অভ্রান্ত মালিক ঠাউরায়
মানচিত্রটা এখন আগের মতো নাই
আগুনে পৃথিবী লেলিহান
তার ছাইভস্মে, পুব-পশ্চিম বেবাক একাকার
একই কবরখানায়।
- উৎস : An Anthology of Modern Arabic Poetry, Mounah Abdallah Khouri & Hamid Algar; 1975; তরজমা : লেখককৃত; PDF Edition.
উদ্ধৃত কবিতাংশ পশ্চিম বিশ্বের মাতব্বর দ্বারা আরব অঞ্চলের মানুষগুলোর ব্যবহৃত হওয়া ও জায়মান সংঘাতের ইতিহাসকে উদঘাটিত করে, অন্যদিকে দুই সভ্যতার খোলা মনে সংলাপে গমন করতে না পারার ঘাটতিও সেখানে চাপা থাকে না। গওহর তাঁর নাতিদীর্ঘ পেপারে বিষয়টি পরিষ্কার করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। আরবদের জন্য ওরিয়েন্টালরূপে নিজের স্বকীয়তা অনুভবের রাস্তা হলো এডওয়ার্ড সাইদের ঘরানায় ‘আমরা অর্থাৎ পশ্চিম’ এবং ‘অবশিষ্ট বা প্রাচ্য’ এই ছকে নিজেকে ভাগ করে ফেলা, যেন ‘আমরা’ অভিধায় নিন্দিতদের ‘অবশিষ্ট’ উপাধিতে চিহ্নিত ব্যক্তিগণ এ্যানকাউন্টার করতে পারে। শোষিত ও ব্যবহৃত হওয়ার যেসব বিক্ষোভ সাইদকে ‘অবশিষ্ট’-র জন্য পৃথক রাস্তা তৈরির কাজে কামলা খাটায় তার মধ্যে দগদগে সত্য থাকলেও সেই পথে গমনকারী ব্যক্তির মনে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড অবিশ্বাস জন্ম নেওয়ার ফলে তাদের পথকে সে এখন আর নিজের নজদিক ভাবে না। সাইদের রাহা বা পথ যে-কারণে হান্টিংটনে বর্ণিত অমিমাংসিত সংঘাতে একে অন্যকে খতমের রাহা থেকে বেশি দূরের নয়।
অন্য রাস্তাটি নিজের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি ঝোলায় ভরে পশ্চিমের সঙ্গে সংলাপে গমনের রাস্তা খোঁজে। গওহর তাঁর পেপারে বলাবাহুল্য দ্বিতীয় পথে গমনের সাম্প্রতিক প্রবণতার খবর করেছেন। তাঁর পেপার ইসলামের সম্প্রসারণের যুগে প্রায় প্রত্নবস্তুতে পরিণত গ্রেকো-রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টির সঙ্গে মুসলমানদের ঐতিহাসিক সংযোগকে আবার সামনে হাজির করায়। অধুনা আরববিশ্বের কবি-লেখকরা নাকি মিসিং সেই লিংক পুনরুদ্ধারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন! এই আগ্রহ অন্যভাবে তওফিক আল-হাকিম ও ড. তাহা হোসেইনকে তাঁদের কাছে পুনরায় প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। উনারা সেই লোক ছিলেন যাঁরা আরব হিসেবে নিজের স্বকীয়তা অনুভবের জন্য প্রচলিত ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি কেটে সংলাপে গমনের আওয়াজ তুলেছিলেন সেই সময়।
অনেকদিন পর জাদুঘরে নির্বাসিত তাহা ও হাকিমদের জীবিত হয়ে ওঠার মানে হলো আরববিশ্বের কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবীরা দুই সভ্যতার ঠোকাঠুকির ঘটনায় ক্লান্ত ও বিরক্ত। অন্যদিকে সাইদ কিংবা হান্টিংটন একজন আরবের আত্মপরিচয়কে যেসব চিহ্ন ধরে-ধরে পাঠ ও নির্ধারণ করতে থাকেন সেসব নিয়েও তাঁরা ক্লান্ত। তাঁরা এখন লন্ডন ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরের দেয়ালে শোভিত ব্যাঙ্কসির বিখ্যাত দেয়ালচিত্রে নিজের আত্মপরিচয় পাঠ করতে আগ্রহী; — বোমায় ক্ষতবিক্ষত মধ্যপ্রাচ্যের মাটির ওপর দাঁড়িয়ে পালটা বোমা ছোড়ার পরিবর্তে ফুলের তোড়াকে বোমার মতো ইসরায়েল তথা সমগ্র পশ্চিমা সভ্যতার দিকে তাঁরা এখন ছুড়ে দিতে ইচ্ছুক। মিথ্যে নয়, ড. তাহা একদিন এই স্বপ্নটি দেখেছিলেন, মিশর কিংবা আরবের নানান প্রান্ত থেকে ‘ওরিয়েন্টাল’রা বেরিয়ে এসেছে যারা মিশরী, আরব, মুসলমান অথবা প্যাগান পরিচয় সগর্বে বুকে ধারণ করে পশ্চিমের সঙ্গে সংলাপে যাওয়ার হ্যাডম রাখে এবং ফুলের তোড়ায় বাঁধা নতুন জ্ঞান ও কৃষ্টি বোমার মতো ঝাঁ-চকচকে সেই সভ্যতার দিকে অবিরাম ছুড়তে জানে। হয়তো সে-কারণে তাহা হোসেইন তাঁর স্বদেশবাসীকে প্রাচীন আরব এবং ইসলাম সম্প্রসারণের যুগে গ্রেকো-রোমান সভ্যতার সঙ্গে বিদ্বানদের সংলাপে লিপ্ত থাকার ইতিহাস পানে আরেকবার ফিরে তাকানোর ডাক দিতে ইতস্তত বোধ করেননি।
মিশর তথা সমগ্র আরবের সঙ্গে ইসলামের হাজার বছরের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, সমধিক অবিচ্ছেদ্য প্রাচীন আরব ও গ্রেকো-রোমান সভ্যতার সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সংযুক্তি। ইসলামের স্বর্ণযুগে যেসব অতুল বিদ্বান একে-একে ধরায় আবিভূর্ত হয়েছিলেন তাঁরা ইসলামকে কোরান-হাদিস সূত্রে পাঠ যাওয়ার ক্ষণে জাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত গ্রিক ও রোমান জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলা পুনরুদ্ধার এবং নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনের মাধ্যমে মৃতপ্রায় প্রাচীন জ্ঞানকে নবজীবন দান করেছিলেন। তাঁদের এই উদারতা ও অনুসন্ধিৎসা সেকালের ইসলামকে একাধারে স্থানিক ও বৈশ্বিক ঘটনায় পরিণত হতে সাহায্য করেছিল। ইতিহাসের ফেরে সমগ্র পশ্চিম সভ্যতার সঙ্গে আরবের দীর্ঘ বিরোধ-বিচ্ছেদ উৎকট আকার ধারণ করেছে এবং নতুন সেতুবন্ধ যদি সেখানে তৈরি না হয় তাহলে একজন আরবের পক্ষে সে কেন ‘ওরিয়েন্টাল’ এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন হয়। এই পটভূমি থেকে তাহা হোসেইন সম্ভবত পুনরায় দূরগামী উট হয়ে দেখা দিয়েছেন, যাঁর ওপর সওয়ার হয়ে আরববিশ্বের সাম্প্রতিক কবি-লেখকরা নতুন করে পশ্চিমের সঙ্গে সংলাপে যাওয়ার রাহা খুঁজছেন।
প্রকৃতপক্ষে ড. তাহা সেই ঘরানার লোক ছিলেন যাঁকে স্বীকার করার পরিবর্তে অস্বীকার যাওয়া অনেকের কাছে সহজ মনে হয়েছিল সেই সময়। নোবেলের সংক্ষিপ্ত তালিকায় মিলান কুন্ডেরা বা হারুকি মুরাকামির মতো তাঁর নাম একসময় নিয়মিত ঘটনা হয়ে ওঠে। প্রতি বছর নামটা তালিকায় সংযোজিত হতো এবং উপায় নেই দেখে নোবেল কমিটি সে-নাম ছাটাই করতে বাধ্য হতেন। তাহা হোসেইনের সাহিত্যকর্ম নিয়ে পেপার লিখেছেন এমন একজনের লেখা থেকে জানা যায় চৌদ্দ বা পনেরোবার নোবেলের শর্ট লিস্টে তাঁর নাম উঠেছিল এবং প্রতিবার এই লোককে নিয়ে কী করা যায় ভেবে কমিটি দোনোমোনায় ভুগেছেন! কারণটা জটিল কিছু নয়, আরববিশ্বে আলেম-ওলামা থেকে শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে তিনি স্বস্তিদায়ক ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি তো সেই লোক যে কিনা প্যান ইসলামিজ ও আরব ভ্রাতৃত্ব থেকে উদ্ভূত জাতীয়তায় আস্থা রাখতে পারে না, সে বরং উলটো পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সঙ্গে সংলাপে গমন অধিক জরুরি ভাবে এবং মিশরীয় ঐতিহ্যে ইসলাম ও আরব ভ্রাতৃত্বের বাড়াবাড়ি অনুপ্রবেশকে অযাচিত বিচ্যুতি বলে দাগায়!
ড. তাহা-র এহেন মনোভাবের নেপথ্যে কোরানের সঙ্গে তাঁর মানসিক বিরোধ ছিল গণ্য কারণ। নতুন জীবনধারার পত্তন ঘটানোর জন্য কোরানকে তিনি মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি, পক্ষান্তরে ইসলাম-পূর্ব আরব অর্থাৎ ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ’ নামে যে-সময়ের ছবি কোরানে প্রকাশ পায় তাকে একবাক্যে মেনে নিতে তাঁর আপত্তির অন্ত ছিল না। জাহিলি যুগকে কেন্দ্র করে ইসলামবিশ্বাসী মুসলমানের অন্তরে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের যেসব মনোভাব প্রবল আকার ধারণ করেছে অন্তর থেকে তিনি সেটা কখনও মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছে ইসলামি টেক্সট ও সামগ্রিকভাবে আরবি সাহিত্য ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’কে দ্রষ্টব্য ঘটনা করে তুলেছে ভালো কথা কিন্তু এর সত্য-মিথ্যা খোলা মনে সকলের যাচাই করা উচিত। ইসলামের ইতিহাস ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’ রূপে যাকে বিশিষ্ট করে বাস্তবে সেরকম কিছুর অস্তিত্ব ইসলামি বইপত্তর ছাড়া অন্যান্য উৎসে বিরাজিত থাকার প্রমাণ নিজের অনুসন্ধানে তিনি খুঁজে পাননি। অথবা যতখানি সত্যতা সেখানে থাকতে পারে বলে অনুমেয় কোরানের ওপর ভর করে তাকে একরৈখিক ছকে উপস্থাপনের ফলে ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’র নেপথ্যে কী ছিল সেটা আর জানার উপায় থাকে না।
ড. তাহা-র অনুসন্ধানে ইঙ্গিতটি তাই একসময় প্রবল হয়েছিল, — ইসলামি টেক্সটে বন্দি আরব তথা বিশ্ব জুড়ে বিদ্যমান মুসলমান সম্প্রদায়ের মনের মণিকোঠায় জাহিলি যুগের যেসব ছবি সচল দেখা যায় সেগুলা যতটা বাস্তবিক তার অধিক অতিকথা বা মিথ! এই অতিকথার চাপে আরবের হাজার বছরের বহুবর্ণিল সংস্কৃতি কুফরির স্মারক গণ্য হওয়ায় তার সমুদয় চিহ্ন এখন লোপ পেতে বসেছে। ট্রাইবাল জীবনধারার চিরায়ত প্রবণতার সঙ্গে ঐতিহাসিক অভিন্নতা সত্ত্বেও স্থানিকতা থেকে উদ্ভূত যেসব বৈশিষ্ট্য আরব অঞ্চলের গোত্রশাসিত জীবনধারাকে পরস্পর থেকে পৃথক ও বর্ণিল করেছিল, কোরান নির্দিষ্ট বিবরণে তার ভালোমন্দ দিকগুলো সমান গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা পায়নি।
প্রতিমা উপাসনা, গোত্রের মানমর্যাদা রক্ষাকে কেন্দ্র করে খুন-খারাবি, একে অন্যের ওপর আধিপত্য অর্জনের যুদ্ধ, ক্যারাভান লুট, জীবিত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলা, বেপর্দা চলাফেরা, বহুগামীতা, নাচাগানা ও দেদার মদ্যপানের মতো হাজারবর্ষী ট্রাইবাল জীবনাচারের ভালোমন্দের ওপর কোরান নির্দিষ্ট আপত্তি প্রবল হওয়ার কারণে আরব-সংস্কৃতি ক্রমশ একরৈখিক টেক্সটে নিজেকে বন্দি করেছে এবং পরে সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। মনে রাখা প্রয়োজন, ড. তাহা-র সঙ্গে কোরান-প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীদের বিরোধ ঐশী গ্রন্থ ও তার প্রচারক এবং ইসলাম ধর্মের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধেনি; বহুবর্ণিল আরব সংস্কৃতির চিহ্ন সমূহকে কোরান ও ইসলাম যেখানে জাহিলির নমুনা রূপে পাঠ যায় এবং ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন’ যুগের প্রতীকে নির্দিষ্ট ও বাতিল করে সেখানে তাঁর আপত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, যেহেতু এই নির্দিষ্টকরণের মধ্যে তিনি মিশর এবং আরব পেনিনসুলার স্বকীয়তাবোধের সমাধি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাননি।
অন্যান্য ইতিহাসকারের মতো তাহা-ও মনে করেন পৃথিবী জুড়ে বিদ্যমান গোত্রশাসিত জীবনধারার চিরাচরিত নিয়মে যেসব ঘটনা আরব অঞ্চলে সেই সময় ঘটে তা সকল গোত্রের ক্ষেত্রে সমান ছিল না। কোরানের মানদণ্ডে অনুচিত কর্মকাণ্ডের অস্তিত্ব যেমন ছিল, এর বিপরীতে মানবিক সম্প্রীতি, পারিবারিক বন্ধন, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ ও স্বাধীনতার কমতি সেখানে ছিল না। সর্বোপরি যেসব প্রথাচারকে কোরান অনৈতিক ঘোষণা করে, গোত্রশাসিত জীবনরীতির সহজাত বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় সেগুলো আদৌ অনৈতিক বা অস্বাভাবিক হতে পারে না, বরং কোরান আরোপিত নৈতিকতার চাপ সেখানে বেখাপ্পা অভিঘাত রূপে তাদের জীবনে নেমে এসেছিল! নৈতিক এই চাপের কারণে আরব জনপদে বিরাজিত স্থানিকতার উহ্যায়ন কী করে ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ড. তাহা-কে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে। পশ্চিম প্রভাবিত জ্ঞানপ্রকল্পের সাহায্যে আরব অঞ্চলে বিদ্যমান ইসলাম-পূর্ব ও পরবর্তী সাংস্কৃতিক অভিঘাতের তদন্তে উতলা হওয়ার কারণে আরববিশ্বের বুদ্ধিজীবী পরিমণ্ডলে অস্বস্তিকর টেক্সট রূপে তিনি এখনও পঠিত হয়ে থাকেন। তাঁকে উপেক্ষা করা হয় এমন নয় কিন্তু উদার মনে গ্রহণের বেলায় নিজের অস্বস্তি খুব কম ব্যক্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন। হয়তো সে-কারণে দীর্ঘ দিন ফ্রান্সে তাঁকে একপ্রকার নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়েছিল।
কোরান প্রভাবিত ইসলামের একরৈখিক নির্ধারণের চাপে বহুরৈখিকতার বিলুপ্তি ড. তাহা-র মনে বিচ্ছেদের অনুভূতি নিয়ে হাজির হয়েছিল। এটা সেই বিচ্ছেদ যার জের টানতে গিয়ে আরব অঞ্চলের জাতি-গোত্র-সম্প্রদায় নিজের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক কিছুকে এখন ঘৃণ্য বলে ভাবে অথবা তাদেরকে সেরকম ভাবতে প্ররোচিত করা হয়! ভালোমন্দের মিশ্রণে গঠিত সংস্কৃতির স্বকীয়তা ও ঐতিহাসিক প্রাসঙ্গিকতাকে কুফর ছাড়া দ্বিতীয় টেক্সটের সাহায্যে তারা এখন আর পাঠ যেতে পারে না! ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’ যে-কারণে ড. তাহা-র মনোজগতে প্রশ্ন ও সন্দেহের বীজ বপন করেছিল এবং ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতা সম্পর্কে অনুসন্ধানে নামার পর সেই সন্দেহ অন্তত তাঁর নিজের কাছে অমূলক বা ভিত্তিহীন ছিল না।
জাহিলি যুগের যেসব ছবি প্রতিমা উপাসনা ও আল্লাহর একত্ব মেনে নিতে অনিচ্ছুক গোত্রগুলোর আচরণের সুবাদে কোরানের পাতায়-পাতায় ধরা পড়ে তাহা হোসেইনের অনুসন্ধানে সেটা ছিল উদ্দেশ্যমূলক ও পলিটিক্যাল ঘটনা। আল্লাহর একত্বের নিকট মুসলমানের আত্মসমপর্ণের প্রস্তাব মোহাম্মদকে সেকালে ইসলামি কওমিয়াত বা জাতীয়তার রূপকার হতে সাহায্য করেছিল। এই রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে আরব অঞ্চলের বহুবর্ণিল সংস্কৃতিতে বিদ্যমান স্মারক সমূহের আন্তঃসম্পর্ক ও সংঘাত তাঁর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অগত্যা তিনি ‘বাতিল ও নতুন’র দ্বন্দ্বকে সামনে হাজির করতে বাধ্য ছিলেন। মুসলমান মাত্রই মহানবির ‘উম্মত’ — এই টেক্সটের অধীনে আরব তথা সমগ্র বিশ্বের ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে কাতারভুক্ত করার প্রস্তাব সময়ের সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। ‘খোলাফায়ে রাশেদীন’-র এটা হলো মূল কনটেক্সট, যা পরে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের শোর মাচানোর মধ্য দিয়ে ইসলামি জাতীয়তার ভিত্তিতে পরিণত হয় এবং সময়ের পটপরিবর্তনে আরব জাতীয়তাবাদ নিজেকে সেখানে সংযুক্ত হতে দেখে।
এই জাতীয়তা জালালুদ্দিন আফগানিকে প্যান ইসলামিজমে সওয়ার হওয়ার সঙ্গে শরিয়াছকে বিশ্বের মুসলমানকে একীভূত ও সংহত করার স্বপ্নে দিওয়ানা করে তুলেছিল। মিশরে সাইয়েদ কুতুব ও ভারতে মাওলানা মওদুদী থেকে ইরানে আয়াতুল্লা খোমেনি অবধি বিস্তৃত স্বপ্নটি মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং ভারতে জামায়াতে ইসলামীর গোড়াপত্তন ঘটাতে ভূমিকা রাখে। শিয়াশাসিত ইরানে ‘ইসলামি বিপ্লব’ সাধনের ক্ষেত্রেও আফগানি নেপথ্যে প্রভাব রাখেন। ইসলামের স্থানিকতা অতিক্রমে ব্যাকুল বৈশ্বিক ভ্রাতৃত্ব ‘এক আল্লাহ এক কোরান এক জাতি’-র সতেজ বার্তা নিয়ে আবিভূর্ত ও সম্প্রসারিত হলেও ড. তাহা সেখানে স্থানিকতার বিলোপ দেখতে পেয়েছিলেন, এখন যার কাছে কোরান ছাড়া অন্য কোনওভাবে যাওয়ার উপায় থাকল না! যে-কারণে জাহিলিয়া কতটা ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারা থেকে সৃষ্ট আর কতখানি ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত ইতিহাস সেই প্রশ্ন তাঁকে আজীবন তাড়া করে ফিরেছে। মোল্লাদের বাদ-প্রতিবাদ ও আপত্তির মুখে নিজেকে ‘Good Muslim’ দাবি করলেও কোরান নির্ধারিত জাহিলিয়া যুগের বিবরণে ড. তাহা উদ্দেশ্য আরোপণের রাজনীতি সর্বাগ্রে দেখতে পান এবং বিশ্বের মুসলমান সম্প্রদায় এই টেক্সটকে এখন যেভাবে পাঠ যায় এর অনেকখানি তাঁর চেতনায় অতিরঞ্জনের স্মারক রূপেই ধরা পড়েছিল। তাঁর ভাবনার সারসংক্ষেপটি এখানে তুলে ধরা যেতে পারে : —
কোরানের ব্যাখ্যাকে ঘিরে গড়ে-ওঠা অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বিধি সংগত নয়। কোরানের দোহাই দিয়ে যাকে ‘অন্ধকার যুগ’ নামে চিহ্নিত করা হয় ইতিহাসের উৎস বিবেচনায় সেটা গোত্রশাসিত সংস্কৃতির অভিক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের বিশ্বাস-আচার ও জীবনবোধের মিল-বেমিল এবং সংঘাত থাকলেও গোত্ররা প্রত্যেকে সেখানে স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত ছিল। স্বাভাবিক এই স্বাতন্ত্র্যকে ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’ অভিধায় নির্দিষ্ট করার ফলস্বরূপ আরব পেনিনসুলা জুড়ে বিরাজিত গোত্রশাসিত জীবনধারা চিহ্নবিহীন টেক্সটে পরিণত হয়েছে, একমাত্র কোরান ও ইসলামি উৎস ছাড়া যার কাছে এখন আর ফেরত যাওয়ার উপায় নেই; যেন আরব জুড়ে বিচরণরত অঢেল গোত্র ও সম্প্রদায় তারা সকলে একদিন বৃহদাকায় কোরাইশ গোত্রের অংশ ছিল অথবা উক্ত গোত্রের বাইরে দ্বিতীয় কোনও গোত্রের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না যারা কোরাইশ থেকে পৃথক বলে নিজেকে দাবি করতে পারে।
আগেও উল্লেখ করেছি ড. তাহার কাছে এই ঘটনা বিচ্ছেদরেখার অনুভূতি নিয়ে হাজির হয়েছিল, যেখানে খাড়া থাকার পর আরব ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামি জাতীয়তার চেহারাসুরত সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যায় কিন্তু একজন আরব মিশর-সিরিয়া-ইরাক, লেবানন-তিউনিসিয়া-আলজেরিয়া অথবা ইয়েমেনে কী করে খাড়া থাকে তার কিনারা করা ‘মুশকিল কি বাত’ হয়ে ওঠে। ‘বাতিল ও নতুন’-এর ধারণা সামনে আসায় ইসলাম ও ইসলাম-পূর্ব সমাজে যে-বিভাজনরেখা সৃষ্টি হয় সেটা এখন বিশ্ব জুড়ে ইসলামের মৌল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। একজন মুসলমান ‘বাতিল’ বলতে শুধু শিরক ও কুফরের চিহ্ন বহনকারী প্রতিমা উপাসনার সংস্কৃতি বুঝে বিষয়টা এমন নয়, সোজা কথায় যা-কিছু আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস ও নবির উম্মত ভাবতে তাকে বাধা দেয় তার সবকিছু প্রত্যাখ্যান ছাড়া মুসলিম উম্মাহর নির্যাসে নিজেকে দ্রবীভূত করা তার পক্ষে বৈধ হয় না।
নবিদের ইতিহাসে লেখে ইরাকনিবাসী ইব্রাহিম প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কিছুদিন মিশরে অবস্থান করেছিলেন। মিশরে অবস্থান সত্ত্বেও যে-কাজটি তিনি সমাধা করে যেতে পারেননি সুদূর মক্কায় বসে মোহাম্মদ সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। কোরানের সেমিওটিক্স ব্যবহার করে সমগ্র আরব অঞ্চলকে তিনি ইসলামে একীভূত করেন! অন্যদিকে ‘প্রাক-ইসলাম’ নামক টেক্সট খাড়া করে একজন আরবকে তার অতীতে গমনের পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করে দেন! অর্থ অবশ্য এই নয় অতীতে সে গমন করতে পারবে না কিন্তু অতীত ভ্রমণের ক্ষেত্রে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোনও যানবাহনের ব্যবস্থা সেখানে রাখা হয়নি। কেন রাখা হয়নি সে-বিষয়ে খানিক ব্যাখ্যায় যাওয়া প্রয়োজন : —
প্রথমে খেয়াল করা দরকার কোরানকে মানবজাতির জন্য নতুন বার্তা বলে মোহাম্মদ যেমন প্রচার করেন অন্যদিকে ঐশী গ্রন্থে ব্যক্ত সুর কেন নতুন নয় সে-কথা ইয়াদ করাতে ভোলেন না। আহাদ অর্থাৎ ‘এক’ এবং তাওহিদ অর্থাৎ ‘আল্লাহর একত্ব’ (Oneness) বা চির-অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি সম্পর্কে যুগের ফেরে যেসব ভ্রান্ত ধারণা ও বিকৃত বিশ্বাস মানুষের মনে অটল রূপ ধারণ করেছে তাকে ‘বাতিল’ ঘোষণার প্রয়োজনে কোরানের আবির্ভাব এবং এ-কারণে সে নতুনের বার্তাবাহক। পক্ষান্তরে আল্লাহর মৌল গুণাবলী ও অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি নতুন ঘটনা নয়, কাজেই তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কিত বাণীগুলোও চির-পুরাতন। যুগে-যুগে নবি ও আল্লাহনিষ্ঠ মানুষ এই বাণী ধরায় প্রচার করে গেছেন কিন্তু স্রষ্টা প্রদত্ত স্বাধীন ‘আকল’ (যেখানে তিনি পারতপক্ষে হস্তক্ষেপ করেন না।) সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারায় মানব সম্প্রদায় সেই বাণীকে বিকৃত করেছে নয়তো চিরতরে বিস্মৃত হয়েছে। স্বতঃসিদ্ধ বাণীর সহজমর্ম স্মরণ করিয়ে দিতে আল্লাহ কোরান ও বার্তাবাহক নবিকে ধরায় পাঠিয়েছিলেন : —
‘তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত করো। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনও পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’
- উৎস : আর–রূম; ৩০:৩০; আল কোরান; তরজমা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ; পিডিএফ সংস্করণ।
‘আল্লাহর সৃষ্টির কোনও পরিবর্তন নাই।’ — সূরা ‘রূম’-এর এই আয়াতাংশে ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য কোরান ক্লিয়ার করে, — স্রষ্টারূপে আল্লাহর একত্ব যেমন সর্বাবস্থায় মৌলিক, চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয় থাকে, তাঁর একত্ব বা তাওহিদকে স্বীকার যাওয়া ও উপাসনার ধারায় তিনি কোনও পরিবর্তন ঘটাননি। মানবজাতি ছাড়াও সমগ্র জগৎ এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং ফিতরাতের (*আরবি উচ্চারণে ‘ফিতরাহ্’ এবং ইংরেজিতে ‘Fiṭrah’) ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে-কারণে জগতে সকল মানবশিশু আল্লাহর একত্বসূচক তাওহিদ বক্ষে ধারণ করে ধরায় জন্মগ্রহণ করে। শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে পারিপার্শ্বিকের প্রভাব আর নিজের ‘আকল’ বা স্বাধীন বিচারবোধের ভ্রান্ত প্রয়োগ দোষে মৌল পরিচয় থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে যায় অথবা অন্য পরিচয় ধারণপূর্বক নিজেকে সে বিপথগামী করে : —
‘হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে রূপান্তরিত করে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে [জন্মগত] কানকাটা দেখেছো?’
- উৎস : সহিহ বুখারী; অধ্যায় ২০ জানাজা, ১২৭৫; ৫২ তফসির, ৪৪১৩; সহিহ মুসলিম; অধ্যায় ৪৮ তাকদির, ৬৫১৪–৬৫১৯; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ; হাদিস সংকলন গ্রন্থনা : হাদিথবিডিডটকম।

চিত্র–১ : Core Concept of ‘Fitrah’ in Islam
A man born with ‘Natural Disposition’ on his faith to the Creator and thereafter he can take many paths because of the unavoidable circumstances where he lived as a human being. His choice of staying at Natural Disposition depends on how he recognized it by using his self-intellect. If he misunderstood that means an aberration from the purity and right direction due to the bad influence of circumstances. In Islamic Lexicon, it also is Kufr. Image Source: YouTube clips on Fitrah, Sunni Dawah channel.
ইসলামে ফিতরাতের পরিধি ব্যাপক! স্রষ্টার একত্বে ইমান থেকে শুরু করে জন্মগত স্বভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত সহজাত অভ্যাস সেখানে ফিতরাতের আওতায় পড়ে এবং প্রামাণিক হাদিস সংকলনে এ-সংক্রান্ত হাদিসের অভাব নেই। জন্মগত সহজাত বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরায় প্রাণীর আগমন ঘটে এবং বৈশিষ্ট্যের প্রকারভেদ তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক থাকতে সাহায্য করে। অন্যের হস্তক্ষেপ ও প্রভাবে ফিতরাতে পরিবর্তন ঘটলে সে তার মৌল স্বভাব থেকে বিচ্যুত হয় এবং স্রষ্টার মৌল পরিকল্পনায় বিঘ্নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ-কারণে ফিতরাতের ওপর জীবন পরিচালিত করা ইসলামে অশেষ গুরুত্ব বহন করে। এখন ‘বুখারী ও মুসলিম’-এ বর্ণিত হাদিসের শানে নযুল থেকে এহেন মত সংসারে প্রচার লাভ করেছে, মানবশিশু ফিতরাত অর্থাৎ জন্মগত প্রকৃতি অনুসারে মুসলমান রূপে ধরায় আগমন করে এবং পরে ফিতরাত থেকে বিচ্যুতির ফলে বিপথগামী হয় ইত্যাদি।
যদিও সূক্ষ্ম বিচারে একাধিক বিশেষজ্ঞ অভিমত রেখেছেন চির-অপরিবর্তনীয় ও সর্বাবস্থায় ‘এক’ আল্লাহর প্রতি ইমানের নিদর্শন রূপে মানবশিশু ধরায় আগমন করলেও নিজ ‘আকল’ বা স্বাধীন বিচারবোধের ভ্রান্ত প্রয়োগের কারণে পরে যারা বিপথগামী হলো তারা বিধর্মীর ঘরে জন্মগ্রহণ করলে যেমন বিপথগামী গণ্য হবে, এমনকি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও তাদেরকে বিপথগামীই মানতে হয়। আল্লাহর ‘একত্ব’ বা তাওহিদে ইমান রাখার ওপর ফিতরাতের মূল শিকড় প্রোথিত। জন্মগতভাবে মানুষকে আল্লাহ এই ক্ষমতা দান করে ধরায় প্রেরণ করেন এবং একইসঙ্গে বিচারবোধের স্বাধীনতা তাকে তিনি দান করেছেন, যেন মানব সংসারে বিচরণের সময় ভালোমন্দ অভিজ্ঞতার আলোকে নিজের ‘আকল’ খাটিয়ে তাওহিদে সে অটল থাকতে পারে। যে-লোক এই কাজটি করতে পেরেছে তাকে প্রতীকার্থে মুসলমান ভাবা যায়। এখন সে যদি বিধর্মীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে থাকে, তাওহিদে অটল থাকার কারণে ইসলামে বয়েত নিতে সে বাধ্য। আবার যে-ব্যক্তি নিজেকে ফিতরাতে অটল রাখতে পারল না মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও সেই লোক বিপথগামী; নিজের ‘আকল’ ও স্বভাবের প্রকারভেদ অনুসারে সে তখন ভ্রান্ত বিশ্বাসী থেকে অবিশ্বাসী অথবা অজ্ঞেয়বাদী যে কোনও পরিণতি বরণ করতে পারে। ইসলামে ফিতরাত সেই ভিত্তি হয়ে আসে যার ওপর ভর করে কোরান চির-পুরাতন তথাপি চির-নতুনের বার্তাবাহক রূপে নিজেকে হাজির করেছিল একদিন।
স্মরণ রাখতে হয় কোরানের এই দাবি, — মোহাম্মদের পূর্বে ঐশী বাণী নিয়ে যত নবি এসেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে তাওহিদে অটল থাকার বার্তা প্রচার করে গেছেন তাদের সঙ্গে মোহাম্মদ প্রচারিত কোরানের তফাত নেই। তাঁরা সকলে আল্লাহর অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি ও তাঁর উপাসনারীতি সম্পর্কে বাণী প্রচারক ছিলেন। মানবজাতি নিজের স্বাধীন বিচারবোধকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারায় নবিগণ প্রচারিত বাণীর ভুল ব্যাখ্যা যেমন করেছে, তাওহিদ সূত্রে নির্ধারিত উপাসনারীতি ও ঐশী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ কালামের বিকৃতি সাধনের আকাম তারাই করেছিল। এই ভ্রান্তি নিরসনের জন্য আল্লাহ বাধ্য হয়ে বারবার নবি ও ঐশী গ্রন্থ জগতে প্রেরণ করেন এবং কোরান সেখানে সর্বশেষ সংযোজন, যার পরে দ্বিতীয় কোনও ঐশী গ্রন্থের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না।
ফিতরাতের ওপর ভর করে মানব সম্প্রদায়কে সত্য বা সঠিক এবং মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথের পথিক রূপে মার্কিং করার ধরন থেকে অনুমেয় কোরান কেন সেকালের আরবে এমন ঝড় তুলেছিল। ঘটনাটা একদিক থেকে ইসলামের শক্তি ও অনন্যতার পরিচায়ক! গোত্রশাসিত জীবনধারার চিরায়ত রীতি অনুসারে এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের বিবাদ অশান্তির যে-আবহ সৃষ্টি করে আরববিশ্ব সেখানে ব্যতিক্রম ঘটনা ছিল না। আশান্তি মোচনের জন্য ‘বিশ্বের সকল মুসলমান নবি মোহাম্মদের উম্মত’, কোরানের এই নির্দেশনা বিভেদের বাইরে গিয়ে একতায় লীন হওয়ার স্পেস আরবমনে জাগ্রত করতে পেরেছিল। যদিও ইসলামবিশ্বাসী ব্যক্তি মানেই ‘নবির উম্মত’, এরকম অনুভূতি বক্ষে ধারণ করা সত্ত্বেও আরব জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো গোত্রগুলোর দেহে হাজার বছরের স্থানিক সংস্কৃতির ছাপ নীরবে প্রবাহিত থাকায় বিবাদ আজও ঘটে এবং ইঙ্গ-মার্কিন পরাশক্তি ভেদাভেদ জারি রাখতে একে ব্যবহার করে। নবি মোহাম্মদের পর থেকে এখন অবধি সচল আরব জাতীয়তাবাদে মূর্ত ইসলাম যে-কারণে পলিটিক্যাল টেক্সট রূপে ড. তাহা-র চেতনায় ধরা দিয়েছিল। পলিটিক্যাল এই টেক্সট ইসলাম থেকে আরববিশ্বে প্রকৃত সভ্যতার সূত্রপাত ঘটতে দেখে এবং সকল ভেদাভেদের অবসান ঘটাতে ইসলাম-পূর্ব যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যানের ডাক দিয়ে যায়; যদিও ডাক দেওয়ার সময় এর সত্যতা যাচাইয়ের দায় বা তাড়না সে বোধ করে না!
ড. তাহা এখান থেকে ‘ফি আল-শি’র আল-জাহিলি’ বা ‘ইসলাম-পূর্ব কবিতা সম্পর্কে’ (On Pre-Islamic Poetry) বইয়ের জনক হয়ে উঠছিলেন। তাহা-র এই টেক্সট ১৯২৬ সালে আলোর মুখ দেখে এবং আলেম-ওলামাদের ব্যাপক হট্টগোলের মুখে নিষিদ্ধ হয় দ্রুত। অতঃপর ‘ফি আল-আদাব আল-জাহিলি’ বা ‘ইসলাম-পূর্ব সাহিত্য সম্পর্কে’ (On Pre-Islamic Literature) শিরোনামে এর নমনীয় সংস্করণ (Softed Version) তিনি পরের বছর বাজারে ছাড়েন। যুক্তি ছিল, নিজেকে তিনি ইসলাম ও মুসলমানের বাইরে ভাবেন না তবে সত্যানুসন্ধানে মতভেদ ঘটতেই পারে। আলেমদের ক্ষুব্ধ হওয়া ও তাহা-কে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দেওয়ার মূলে এই আপত্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল যেখানে তিনি কোরান-হাদিস-সিরা-ফিকাহ এবং ভাষাতত্ত্ব-ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামি সাহিত্যে বিরাজিত রেফ্রেন্স দাখিল করে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ’ সম্পর্কে জানার প্রাথমিক উৎস উপায় যেমন কোরান, অনুরূপভাবে ইসলাম-পূর্ব কবিতা বলতে যে-বস্তুকে বোঝানো হয় তার উৎস ইসলামিক নথিপত্র ছাড়া অন্যত্র অনুসন্ধান পণ্ডশ্রমের নামান্তর! জাহিলি যুগের কবিতায় বর্ণিত জীবনধারাকে নৈতিকতা বিবর্জিত জীবনসংস্কৃতির দ্যোতক চিহ্নিত করার প্রবণতা ইসলামবিশ্বাসী ছাড়া অন্য কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং তাহা সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য ছিলেন : —
ইসলাম-পূর্ব যুগের কবিতা নামে এখন বাজারে যা চলে তার বৃহৎ অংশ সে-যুগে আদৌ রচিত হয়নি! জাহিলি যুগের কবিতার মধ্যে এমন সব কবিতাও পাওয়া যায় যা ইসলাম সম্প্রসারণের ক্ষণে লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হয়েছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে বিরচিত এইসব কবিতা প্রকারান্তরে ‘জাহিলিয়াত’ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বয়ান মাত্র। তাহা মনে করেন বিশেষ যে-পটপ্রবাহে ইসলাম-পূর্ব মক্কার গোত্রশাসিত জীবনধারাকে ‘অন্ধকার যুগ’ নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল ইসলামের সম্প্রসারণ ঘটার সময় সেই পটপ্রবাহ বিবেচনার দায় কেউ সেভাবে অনুভব করেননি। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পরিবর্তে জাহিলিয়াকে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়। জনতার মনে যেন স্থায়ী দাগ কাটতে পারে এহেন অভিপ্রায়ে অন্ধকার যুগের জীবনপদ্ধতি নিয়ে কবিতা লেখার জোয়ার তৈরি করা হয় এবং উদ্দেশ্যমূলক এইসব কবিতা ইমরুল কায়েস লাবিদ কিংবা নাবিগার নামে বাজারে ব্যাপক প্রচারণা পেতে শুরু করে।
এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ড. তাহা কোরানের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদের কাজটি সেই সময় সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর মতে কোরানের সেমিওটিক্স আরবি ভাষার ধ্রুপদি অঙ্গের পাশাপাশি সৌদি রাষ্ট্রের প্রতিবেশী ইয়েমেনে প্রচলিত স্থানিক ভাষা-রূপের সঙ্গে সাযুজ্য রাখে, যদিও সেকালে আরববিশ্বে প্রচলিত আরবি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপভেদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্ষীণ ছিল। সম্পর্ক প্রবল হয়ে ওঠে মোহাম্মদ ওফাত লাভের পরে। ইরাক থেকে মিশর অবধি বিস্তীর্ণ আরবিভাষী বলয় ক্রমে কোরান-হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্রে নিজের কায়েমি স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করায় মুয়াল্লাকা অর্থাৎ কাবাঘরের দেয়ালে লটকানো কবিতার চল নতুন করে প্রসার লাভ করে এবং কবিতাগুলোর উদ্দেশ্য হয় ‘অন্ধকার যুগ’র জীবনধারায় বিদ্যমান কুফর, শিরক ও অশ্লীলতা সম্পর্কে মানুষকে কবিতার মাধ্যমে সচেতন করা। তো সেই কাজে কিন্দা গোত্রের অবিসংবাদিত প্রেমিক শরাবি যুবরাজ ইমরুল কায়েস থেকে স্বয়ং নবি মোহাম্মদ কর্তৃক প্রশংসিত লাবিদ সকলে কমবেশি ব্যবহৃত হতে থাকেন।
সময়ের স্রোতে এইসব কবি মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, এখন উদ্দেশ্য চরিতার্থে উটের হাওদায় তাঁদেরকে উঠানো হতে থাকে। ইমরুল কায়েসের রচনা নয় কিন্তু তাঁর নামে চালু কবিতা পাঠের পর একজন মুসলমান যেন বুঝতে পারে কুফরে আবিল সেই যুগে মদহুঁশ ইমরুল কেন বেদুইন বালিকা উনাইজার নিতম্ব ঘূর্ণণে দিশাহারা বোধ করার মুহূর্তে আরও হাজার উনাইজার জন্য লম্পট হতে দ্বিধা করেনি। নবি মোহাম্মদ জাহিলি যুগের দু-চারজন কবির কাব্যশক্তির শংসা গাইলেও মোটের ওপর কেন তাদেরকে বাতিল গণ্য করেছিলেন মানুষ যেন সেটা বুঝতে পারে সে-জন্য ইসলামের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের যুগে কায়েস, লাবিদ, নাবিগার নামে কবিতা লেখার দেদার প্রচলন ঘটানো হয়। তাহা তাই অভিমত রেখেছিলেন : —
কায়েস বা আরও অনেক জাহিলি যুগের কবিদের নামে যেসব কবিতা বাজারে চালু আছে তা কেন অরিজিনাল নয় সেটা বোঝার জন্য খানিক খাটনি ও ধীশক্তি যথেষ্ট। তাঁদের কবিতায় ব্যবহৃত ভাষাভঙ্গি, শব্দবন্ধ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির মধ্যে যেসব ভারসাম্যহীনতা চোখে পড়ে তা বিবেচনায় নিলে বুঝতে বাকি থাকে না কোনটা অরিজিনাল আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত বা ‘অন্ধকার যুগ’ সম্পর্কে প্রোপাগান্ডার অংশ হিসেবে বিরচিত।
ড. তাহা-র এই কিতাব এহেন বক্তব্যের কারণে আজও অস্বস্তির জনক হয়ে বিরাজিত এবং নেট ঘাঁটলে তার প্রমাণ সহজে পাওয়া যায়। আমি ওপরে যা লিখেছি সেটা তাহা-র বই সম্পর্কে পক্ষে-বিপক্ষে পেপার লিখেছেন এমনসব রচয়িতার ব্যাখ্যা-ব্যাখান সূত্রে যতখানি বোধগম্য মনে হয়েছে তার সঞ্চয়ন বলা যেতে পারে। এর বেশি বলা মুশকিল, কারণ ড. তাহা-র মূল টেক্সট ইংরেজি অনুবাদে নেটে সহজে পাওয়ার উপায় নেই। পিডিএফ, ই-বুক কিংবা ডিজিটাল ফরমেটে তাঁর সৃষ্টিসমগ্র আজও সহজলভ্য নয়। কাহলিল জিবরান, নাগিব মাহফুজ, মাহমুদ দারবিশ থেকে শুরু করে আবদুল লতিফ লাবি বা অ্যাদোনিস যত সহজে নেটে পাওয়া যায় তাহা-র বইপত্তর পাওয়া ততটাই কঠিন। ফলে অন্য লোকজনের ব্যাখ্যার ওপর ভর করা ছাড়া উপায়ও নেই। আরববিশ্বে এ-পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে প্রচুর পেপার লেখা হলেও সিংহভাগ ড. তাহা-র যুক্তি খণ্ডন বা তাঁর বক্তব্যের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিরচিত এবং পাঠের পর নির্বীষ মনে হয়েছে!
বক্তব্য খণ্ডনের লক্ষ্যে সক্রিয় এইসব লেখকদের তুলনায় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সমাজ-ইতিহাসবিদ এ্যারন আয়ালনের পেপারকে খানিক সুসংহত বলা চলে। ড. তাহা রচিত দুটি বইয়ের তুলনামূলক আলোচনা সেখানে তিনি টেনেছেন। নিজের অনুসন্ধানে এ্যারন প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, মোল্লাদের ঠাণ্ডা করার জন্য ‘ফি আল-শি’র আল-জাহিলি’র নমনীয় সংস্করণ যা ড. তাহা ‘ফি আল-আদাব আল-জাহিলি’ নামে বাজারে ছেড়েছিলেন সেটা প্রথম বইয়ের থেকে মোটেও মৃদু বা নমনীয় কিছু ছিল না! প্রথম বইয়ে যেসব কথা রাখঢাক করে বলবার চেষ্টা ছিল দ্বিতীয় বইয়ে বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা যাচাই আর নিজের কথা ক্লিয়ার করার প্রয়োজনে তিনি বরং এক কদম আগে বেড়েছেন। ‘ফি আল-আদাব আল-জাহিলি’ রচনার পর ড. তাহা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, — ঐতিহাসিক বিবেচনায় কোরান ঐশী গ্রন্থ (Devine Text) নয় বরং মোহাম্মদের মনোবাসনা পূরণে ব্যবহৃত ডিপ্লোম্যাটিক টেক্সট : —
In Ḥusayn’s second book, he reversed himself, denying that jāhilī poetry existed before the emergence of Islam. He went still farther, challenging the historicity of the Qur’an and even implying that it was not a divine book.
- Source: Revisiting Taha Husayn’s Fi al-Shi’r al-Jahili and its sequel by Yaron Ayalon; academia.edu.
যা-ই হোক, এ্যারনের দাবির সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ে ড. তাহা-র মূল বই পাঠ জরুরি। কোনও এক মুহূর্তে তাঁর বই যদি নেটে পাই এবং পাঠের পর যা বলেছি সেসব ভুল প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে ভুল স্বীকার ও ভাবনার সংশোধনে দ্বিধা থাকবে না এই নিশ্চয়তা আগেভাগে জানিয়ে রাখছি।
ড. তাহা হোসেইনকে দুটি কারণে ব্যতিক্রম মনে হয়েছে, — প্রথম কারণ, কোরানে ‘আইয়ামে জাহিলিয়াত’ বা ‘প্রাক-ইসলামিক’ অভিধায় চিহ্নিত টেক্সট তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি কিন্তু চিহ্নায়নের তরিকা পরে কেন উদ্দেশ্যমূলক হয়ে উঠেছিল তা জাতির সামনে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। দ্বিতীয় যে-কারণে তিনি অভিনব সেটা হলো ইসলামি ও আরব জাতীয়তার সঙ্গে স্থানীয় জীবনধারার সন্ধি-বিচ্ছেদের ইতিহাস বুঝতে তাঁর বক্তব্য কাজে লাগে। এদিক থেকে তিনি নতুন ধারার জনকও বটে। জনান্তিকে জানিয়ে রাখি, ইসলাম-পূর্ব আরবি কবিতা বিশেষভাবে মুয়াল্লাকা বা দেয়ালে লটকানো কবিতা সম্পর্কে খোঁজখবর করতে যেয়ে ড. তাহা আগ্রহের কারণ হয়েছিলেন। জাহিলিয়া যুগে রচিত কবিদের কবিতা নিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষায় কমবেশি চর্চা নতুন ঘটনা নয়। বঙ্গানুবাদে র্যানল্ড নিকলসনের ‘আরবি সাহিত্যের ইতিহাস’ বইটি একসময় পাঠ করেছিলাম। প্রাচীন যুগের আরবি কবিদের নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা ছিল সেখানে। নিকলসন সেখানে কোরান ও অন্যান্য ইসলামিক উৎসের সাহায্যে ‘অন্ধকার যুগ’ ও পরবর্তী আরবি সাহিত্যের খোঁজখবর করেছেন। তাঁর গ্রন্থটি ইতিহাস হলেও নতুন কোনও দৃষ্টিভঙ্গির জনক মনে হয়নি। মোহাম্মদের জীবনে কিন্দা গোত্রের যুবরাজ ইমরুল কায়েসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রূপে আবিভূর্ত হওয়া কিংবা আল-নাবিগা, লাবিদ বা আল আশাহ বাংলা ভাষায় পঠিত বলে জানি। ইসলামি টেক্সটে মূলধারার পাশাপাশি বিকল্পধারায় বিদ্যমান উদার ও মধ্যপন্থী সংস্কারবাদী এবং প্রাক্তন মুসলমান (ex-Muslim) পরিচয়ে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তিবর্গের খবর এতদিন অবধি জানা ছিল। তাহা-র মাধ্যমে তৃতীয় আরেকটি ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটল, লাভের দিক বলতে এটাই।
ড. তাহা সম্পর্কে এর বেশি জানার সুযোগ যেহেতু ঘটেনি তাঁর সাহিত্যকৃতির তুল্যমূল্য নিয়ে মন্তব্য সমীচীন বোধ করি না। যদি কোনওদিন তাঁর বইপত্তর সুলভে পাওয়া যায় তখন হয়তো স্থানীয় সংস্কৃতি আর কোরান-সৃষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে বিরাজিত সাংঘর্ষিক প্রবণতা নীরবে একজন আরবকে কীভাবে গড়েভাঙে সে-অনন্যতার অনেককিছু খোলাসা হবে। তাহা হোসেইন বিষয়ে আপাত যতি টেনে ইসলামের মৌল ভিত্তি এবং এ-সম্পর্কিত পক্ষে-বিপক্ষে সচল পঠন-পাঠনের অনুসন্ধান ও ক্ষেত্রবিশেষে ভ্রম সংশোধনের প্রবাহে গমন করতে চাই, যা এই বক্ষ্যমাণ রচনার মূল উদ্দেশ্যও বটে।
ইসলামবীক্ষণ : একটি পুনর্বিবেচনা ২
… …
- হাসিনাপতন : প্রতিক্রিয়া পাঠোত্তর সংযোজনী বিবরণ || আহমদ মিনহাজ - September 4, 2024
- তাণ্ডব ও বিপ্লব || আহমদ মিনহাজ - August 10, 2024
- তাৎক্ষণিকা : ১৮ জুলাই ২০২৪ - August 8, 2024


COMMENTS