এ হয়তো আমাদের সম্মিলিত আত্মহনন যে, অজস্র কথার ঢেউয়ে দরকারি কথারা ক্রমশ নিরাকারে তলিয়ে যাচ্ছে। সোজা করে অথবা প্যাঁচিয়ে যেভাবে বলুন-না-কেন সেই কথাগুলো শোনা ও শোনানোর মাধ্যমরা বিগত মাধ্যমগুলোর তুলনায় কম কার্যকরী। হতে পারে সবাই এত বেশি বলছি বলে হয়তো কারও কথাই সমাজে দরে বিকোচ্ছে না। আমরা হয়তো ‘ভাবার’ চেয়ে বলছি বেশি। লম্বা কথাকে খাটো করে বলার চর্চা যুগজটিলতার রকমফেরে কঠিন হয়ে উঠেছে। কতরকমের বইপত্র! কত রকমারি উপায়ে মানুষ নিজের বাখানি গাইছে! যত কথা তত উৎপাতের মতো বিমূর্ততার বিশ্বে হাবুডুবু খাচ্ছে মানুষ। কথামালার এই বিমূর্তায়ন বা Abstraction-ই আজকের ভাষাবিশ্ব; যেখানে যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক সকল দরের কথারাই মানুষের মন-মেজাজ ভেদে যৌক্তিক রূপে নন্দিত হয় এবং দ্বান্দ্বিক বা Dialectical হয়ে ওঠে। যদিও যৌক্তিকতা বা Rationality শব্দটি সকল কালের ভাষাবিশ্বের সাপেক্ষে এক প্রহেলিকা। অগত্যা মির্চা এলিয়াদ তাঁর The sacred and the profane বহির উপসংহারে পৌঁছে যখন মন্তব্য ঠোকেন, A purely rational man is an abstraction; he is never found in real life., তখন সেই মন্তব্যকে এক-কথায় খারিজ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। মানুষের ভাষাচর্চার এইসব বিবিধ প্রহেলিকার মধ্যে বসে সাহিত্য করাটা আমার কাছে তাই এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহনের মতো কঠিন মনে হয়।
এটা সেই সময় যখন আপনি চাইলেও স্রেফ মানুষের জগতে কেন্দ্রীভূত থেকে একটি লাইন লিখতে পারবেন না। মানুষকে অতিক্রমকারী জগৎ আপনাকে নানাভাবে শাসন করবে। যা-কিছু পেছনে ফেলে এসেছেন, যা-কিছু সহ্য করে অদ্য সহিসালামতে বিরাজ করার আয়েশ বোধ করছেন, এবং যা-কিছু সামনে ঘটতে চলেছে…তার সবখানি একত্রে গড় করতে না-পারলে সোজা কিংবা বাঁকা, স্পষ্ট কী-বা সহজ, অথবা প্যাঁচমারানিয়া কোনও কথাই টিকবে না ভবে; লোকের কানের পাশ ঘেঁষে তারা হুশ করে ছিটকে বেরিয়ে যাবে।
কথার এইসব গুলাগুলি ও গোলযোগের মধ্যে দামি কথার সুলুক পেতে হলে গল্প-কবিতা-আখ্যান এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভাষা-কাঠামোয় বসে যাঁরা কথা কইছেন তাদের হয়তো নিজের বলা কথাগুলোকে সেট-থিয়োরির মতো ভেঙেচুরে রকমফের ঘটিয়ে সাজানো প্রয়োজন। যেমন ধরুন, জনৈক কথাকার কাহিনি ফেঁদে অথবা কাহিনিকে নাকচ করে যেভাবে লিখুন-না-কেন, যে-সময়ে বসে তিনি লিখছেন তার সঙ্গে ফেলে-আসা এবং আগত ও দূরবর্তী সময়ের তীরকে একত্রে জুড়ে নিতে ব্যর্থ হলে তার পক্ষে ভাষার বিমূর্তায়নে যাওয়া সম্ভব নহে। কাঠোমাবাদী সাহিত্যের ছকে লিখে যাওয়াকে আমি খাটো করে দেখছি না, তবে যুগযুগান্তর ধরে চর্চিত এই কাঠামোকে নতুন করে গড়েপিটে নেওয়ার তাড়না তীব্র হওয়া দরকার — যেটা এই বঙ্গে এখনও সেভাবে জোরকদমে চলার শক্তি অর্জন করেছে বলে প্রত্যয় হয় না।
…
আমার কাছে দেবেশ রায় এবং তাঁর মতো অথবা তাঁর থেকে ভিন্ন ঘরানার কতিপয় বঙ্গীয় রচয়িতার গুরুত্বটি এখানে। তাঁরা কাহিনি-বয়ানের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নতুন কাঠামোর সন্ধান করছেন এবং নিজের লেখায় সেটি ব্যবহার করেছেন। দেবেশ যেমন প্লট ছকে কাহিনি ফেঁদেছেন ঠিক, কিন্তু সেই কাহিনিকে বঙ্গদেশের পক্ষে নতুন বর্ণনাভঙ্গির সাহায্যে ভেঙেও দিয়েছেন। তাঁর গল্প ও আখ্যানে সংবাদসুলভ প্রতিবেদনের আঙ্গিকে যে-দীর্ঘ ধারাবর্ণনা চলতে থাকে সেটার চাপ প্রকারান্তরে গল্পকথনের (অর্থাৎ এরপরে কী কী ঘটবে?) উপমহাদেশীয় অভ্যাসে বিপর্যয় ঘটায়। তাঁর এই ধারাবর্ণনার আদি উৎস রুশ দেশ থেকে আহরিত হলেও রুশিরা ধারাবর্ণনায় গল্পের বিষয়-চরিত্র এবং সংলাপের মধ্যে একটি আনুপাতিক সামঞ্জস্য রাখেন, যেন একস্বরের মধ্যে বহুস্বর অর্থাৎ বাখতিন-কথিত পলিফনি বা বহুস্বরের আবেশ ক্ষুন্ন না হয়। দেবেশের রচনায় সেটা বহাল থাকে না। তাঁর আখ্যানপাঠ তাই গল্পের পরম্পরা মেনে চরিত্র ও কাহিনি পাঠে অভ্যস্ত প্র্যাচ্যদেশি পাঠকের কাছে ক্লান্তিকর ঠেকে। যেহেতু এখানে কাহিনির ছকে চরিত্র-নির্মাণ আসলে মুখ্য নয়, চরিত্র তার পরিপার্শ্বের সঙ্গে গলেমিশে কোনও ভূখণ্ড এবং সময়প্রবাহের স্মারক হয়ে উঠতে পারল কি না সেটাই সেখানে মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে।
‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-এ বাঘারু এভাবে একটি জনপদের প্রতীকী বয়ান রূপে Class-Contrast-এর মধ্যে তার নিজের দাঁড়ানোর মাটি খুঁজে ফেরে। ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ আখ্যান হিসেবে একদিক থেকে সার্থক (আমার ক্ষুদ্র পাঠবিচেনায় অবশ্যই), সেটি এ-কারণে যে, বাঘারু এখানে একা ও সর্বগ্রাসী চরিত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। সে এমন এক চরিত্র যাকে তার জনপদ ও সেই জনপদের অতিপ্রাকৃত জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বাঘারু আদিম। সে যতটা প্রলেতারিয়েত, তারচেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রাগৈহিতাসিক। অন্ত্যজ মানবগোষ্ঠীর অংশ সে, যুগে-যুগে যাদের জন্ম হয়েছে Class-Contrast-এর চাকা সচল রাখার খাতিরে। তার বিদ্রোহে শ্রেণিচেতনা অতটা প্রবল নয়, যতটা রয়েছে আদিম অন্ধ ক্রোধ; যে তার কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারছে তাকে বহুভাবে তার নিজস্ব ঠিকানা ও প্রকৃতিজাত স্বভাব থেকে বিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র চলছে। যে-ষড়যন্ত্রে সমাজ-সভ্যতা-রাষ্ট্র ও সময় সকলই তার প্রতিপক্ষ বটে। সে সাম্যবাদের প্রাণশীতলকারী বৈপ্লবিক মুখপত্র/মুখপাত্র নয়, যদিও ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’-র মঞ্চায়নে এই দিকটি নির্দেশক অমোঘ করে তুলতে চেয়েছেন। কেন? সে তিস্তাপারের মঞ্চায়করাই ভালো বলতে পারবেন।
আমার ক্ষুদ্র পাঠবিবেচনায় বাঘারু সেই আদিমতার স্মারক যে তার জনপদে বিরাজিত থাকার হিস্যা চাইছে, যেভাবে চাইলে পরে তাকে সেই জনপদের অচ্ছেদ্য অংশ রূপে ভাবা যায়। শিরা-ফোলানো বিদ্রোহের দামামা তিস্তাপারের এই আখ্যানে অন্তত আমার নজরে পড়েনি। এবং এটা আখ্যানটিকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। অন্যদিক থেকে ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’ একপেশে। সেটি এ-কারণে, বৃহৎ এই আখ্যানে বাঘারু ছাড়া অন্য কেহই যেন আখ্যানের পরিসরে যুৎসই জায়গা করে নিতে পারেনি। রুশদেশি লেখকরা এ-কাজে পারঙ্গম। তুচ্ছ চরিত্রও সেখানে মূল্য ধরে ও পাঠকের মনের গহীন কোণে কেমন করে যেন টিকে যায়! দেবেশের আখ্যানে বাঘারু ছাড়া বাকি চরিত্ররা কী করে যেন স্মৃতির অতলে হারায়। মনে স্থায়ী দাগ রেখে যেতে পারে না। এমনকি Class-contrast-এর স্মারক রূপে যেসব ঘটনা, চরিত্র ও উপাদানরা সেখানে ভিড় জমিয়েছে তারা বাঘারু-চাপে ক্রমশ নিখোঁজ হতে থাকে। ফলে এই আখ্যানটিকে কেন্দ্র করে Dialectical Conversation কিংবা সে-রকম সংলাপে যাওয়াটা ভীষণ মুশকিল ঠেকে।
ফুটনোটে বলে রাখি, বঙ্গদেশে প্রলেতারিয়েতপন্থীরা কেমন করে যেন এই আখ্যানের মধ্যে Dialectical Conversation-এর মতো বিষয় ও চরিত্র এন্তার খুঁজে পান! কবুল করছি, এ আমার সীমাবদ্ধতাও হতে পারে, বাঘারুকে আমি সেই সংশ্লেষে পড়ে উঠতে পারিনি। দেবেশের এই ম্যাগনাম-ওপাস পাঠের প্রথম ধাক্কায় ধারাবর্ণনার কারিকুরি সম্পর্কে একটি ধারণা হয়েছিল। স্মৃতি থেকে বলছি, তিস্তাপারের জনপদে বলিউডরাণী শ্রীদেবীর আগমন উপলক্ষে একটি জম্পেশ ধারাবর্ণনা দেবেশ রায় দিয়েছিলেন। আখ্যানের ওই অংশটি অন্তত আমার কাছে এখনও হীরকসম উজ্জ্বল মনে হয়; যেহেতু জনপদের সঙ্গে বিনোদনদুনিয়ার রাণীর এই Contrast-টি জবর ছিল।
দেবেশকে অন্যরকম লেগেছে তাঁর ‘মানুষ খুন করে কেন’ কিংবা ‘একমাইল শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে’-র মতো আখ্যানে। ‘দাঙ্গা’, ‘খরা’ বা ‘মফস্বলী বৃত্তান্ত’-র মতো রচনাগুলো তাঁর নিজস্ব ধারাবর্ণনার ছকে আবর্তিত এবং সেখানে বেশিক্ষণ যাপন করা কঠিন। হয়তো এ-আমারই ব্যর্থতা, — দারিদ্র্যের রকমফের ঘিরে রচিত হাহাকার ও উপহাস এবং তাকে ঘিরে অমোঘ–হয়ে–ওঠা Class-contrast ইত্যাদির সাহিত্যিক পাঠ বেশিক্ষণ সহ্য করা মুশকিল। এটা অন্যভাবে হয়তো দেবেশের সাফল্য হতে পারে, আমার মতো দুর্বল স্নায়ুর পাঠককে তাঁর বয়ান থেকে তিনি ছিটকে যেতে বাধ্য করছেন। মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্ট নিয়ে দারিদ্র্যের জটিল অভিঘাত পাঠ করে চলার আয়েশকে জোর ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এইভাবেও তাঁর এই রচনাগুলোকে বিবেচনা করা যায়। তবে কবুল করছি, এই ধাঁচের Text সম্যক পড়ে ওঠা বেশ ক্লান্তিকর। যেহেতু, এর মধ্যে ধারাভাষ্যের (যেন নিরপেক্ষ কোনও দর্শক দূর থেকে চোখে বাইনোকুলার সেঁটে জনপদের দৃশ্য দেখছেন) নবায়ন থাকলেও সেই ঘূর্ণিস্রোত নেই যা আপনাকে পাঠে ফেরত যেতে বাধ্য করতে পারে। আমার অতি নগণ্য এবং অনায়াসে বাতিলযোগ্য গল্প-আখ্যান লেখার স্পর্ধা বা অপচেষ্টায় দেবেশ রায়ের বয়ানরীতি অনুপ্রেরণা-সঞ্চারক ঘটনা হয়েছিল কি না, তার উত্তরে এটুকু যোগ করা যায় :— দেবেশ তাঁর নিজস্ব মহিমায় মাস্টারক্লাস হলেও আমার পাতের জিনিস নন।
তাঁকে প্রণাম এজন্য যে, আখ্যান-রচনার নতুনত্ব নিয়ে তিনি বিস্তর ভেবেছেন। তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধে চোখ রাখলে সে-সম্পর্কে উৎসাহজাগানিয়া ভাবনার সুলুক মিলে। আমাদের নিজস্ব বয়ানরীতির খোঁজ কেমন করে আমরা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য-আঙ্গিকে বিরচিত ভাষাবিশ্ব থেকে পেতে পারি সে-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নিবিড় পাঠ ও অনুসরণ দাবি করে। অথবা ধরুন, বঙ্কিমী-ঘরানার বাইরে বাঙালির নিজস্ব লৌকিক ভাষারীতির প্রয়োগে (যার নমুনা কালীপ্রসন্ন সিংহ ও প্যারিচাঁদ মিত্র এমনিক স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন তাঁর নাটকে করে দেখিয়েছেন) কেন অধিক আগানো গেল না, কেন সেটি এখনও অনাবিষ্কৃত ভূগোল হয়ে পড়ে থাকে ইত্যাদি নিয়ে তাঁর বিচক্ষণ ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করার জো নেই।
দেবেশ রায় প্রবন্ধ-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁর সেই টেক্সটগুলোর অবিরত পুনর্পঠন জরুরি মনে করি। এর অর্থ অবশ্য এই নয়, গল্প-আখ্যানে তিনি গৌণ। তাঁর মাপের লেখকের কোনও কৃতিই গৌণ নয়। নিজস্ব এক ভাষাপ্রকৌশলের জোরে অনেকের কাছেই তিনি অমোঘ থাকবেন দূর আগামীতেও। তবে এটাকে অনুসরণ করা বা এর বিনির্মাণ বিপজ্জনক মনে করি। এই ধারাবর্ণনার মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক যে-মনোটনি রয়েছে সেটাকে অনুসরণ করে বেশিদূর আগানো কঠিন। ওটা দেবেশের জন্য উপযুক্ত হলেও অনেকের জন্য আত্মহননের শামিল হতেও পারে। যে-কারণে হয়তো (আমার পর্যবেক্ষণ সঠিক নাও হতে পারে) তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখককুলকে দেবেশের রচনাপদ্ধতি ও ভাষাপ্রকৌশল সেভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি।
…
দেবেশ রায় সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি বলার স্পর্ধা আমি রাখি বলে মনে করি না। সাহিত্য থেকে এমনিতেও বিলগ্ন আছি অনেক বছর ধরে। যেটুকু সংযোগ রয়েছে সেখানে আমার নিজের আখ্যানভাবনার কোনও সম্পর্ক নেই।
- ইমেইলে লেখকের সঙ্গে আলাপের অংশবিশেষ এই তাৎক্ষণিকা। — গানপার
… …
- হাসিনাপতন : প্রতিক্রিয়া পাঠোত্তর সংযোজনী বিবরণ || আহমদ মিনহাজ - September 4, 2024
- তাণ্ডব ও বিপ্লব || আহমদ মিনহাজ - August 10, 2024
- তাৎক্ষণিকা : ১৮ জুলাই ২০২৪ - August 8, 2024

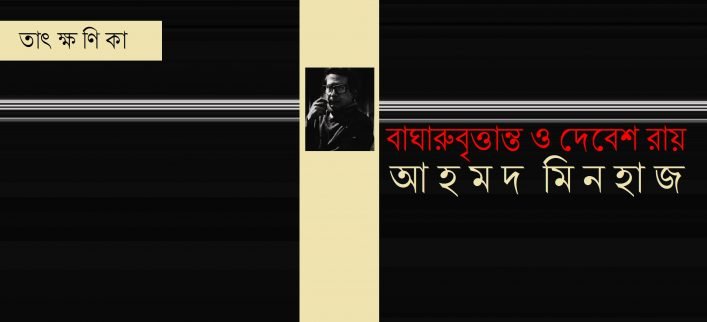
COMMENTS